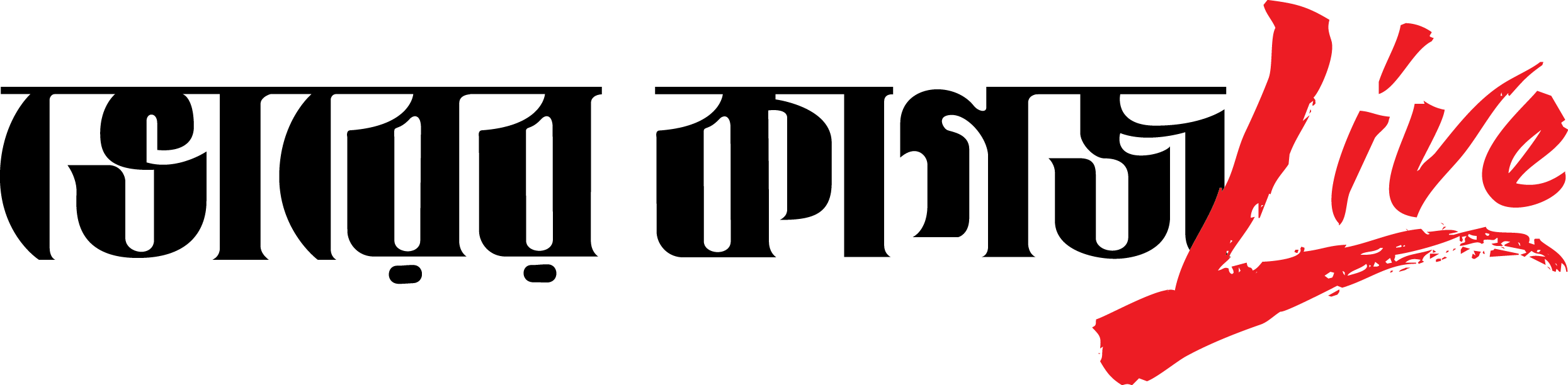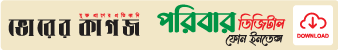যে পদ্ধতিতে হতে পারে পুলিশ বাহিনীর সংস্কার
আজিজুর রহমান জিদনী
প্রকাশ: ০৩ অক্টোবর ২০২৪, ১২:০০ এএম
প্রিন্ট সংস্করণ

বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন ঘিরে পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে পুলিশ বাহিনীর কর্মকাণ্ড নিয়ে আলোচনা-সমালোচনা হচ্ছে দেশজুড়ে। ছাত্র-জনতার গণআন্দোলনের সময়েও বিগত শেখ হাসিনার সরকারের আজ্ঞাবহ হিসেবে শিক্ষার্থীসহ সাধারণ নাগরিকদের নির্বিচারে গুলি করে হত্যার অভিযোগ ওঠে আইনশৃঙ্খলা রক্ষায় মুখ্য দ্বায়িত্ব পালন করা এ বাহিনীর ওপর।
এরই ধারাবাহিকতায় জনরোষে পড়ে থানা ভাঙচুর ও অগ্নিসংযোগসহ পুলিশ পিটিয়ে হত্যার ঘটনা ঘটে। এমন পরিস্থিতিতে ট্রমায় থাকা পুলিশ বাহিনীকে সংস্কারের কথা জানানো হয় অন্তর্বর্তী সরকারের পক্ষ থেকে। গত ১১ সেপ্টেম্বর সন্ধ্যায় জাতির উদ্দেশে দেয়া ভাষণে অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূস পুলিশ প্রশাসনে সংস্কার কমিশনের প্রধান হিসেবে দায়িত্ব দেন সফর রাজ হোসেনকে। আনুষ্ঠানিকভাবে ১ অক্টোবর কাজ শুরুর কথা রয়েছে তার। ৩ মাসের মধ্যে তাকে কাজ শেষ করতে হবে।
এরই ধারাবাহিকতায় কোন পদ্ধতিতে ও কীভাবে পুলিশ বাহিনীর সংস্কার হওয়া প্রয়োজন তা নিয়ে শুরু হয় নানা আলোচনা। এ বিষয়ে সংশ্লিষ্টরা বলছেন, সংস্কার প্রস্তাব অনেকবার এলেও কাগজেই সীমাবদ্ধ থেকেছে; কখনো আলোর মুখ দেখেনি তা। নিজেদের স্বার্থে ব্যবহার করতে গিয়ে বিভিন্ন সময়ের শাসকগোষ্ঠী পুলিশে সংস্কারের দিকে মনোনিবেশ করেনি।
ফলে পুলিশের কাক্সিক্ষত সেবা পাওয়ার বিষয়টি দুষ্করই থেকে যায় সাধারণ জনগণের কাছে। সম্প্রতি বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের সময়েও পুলিশ বাহিনীর ভূমিকা ব্যাপকভাবে সমালোচিত হওয়ায় এখন এই বাহিনী সংস্কারের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। এক্ষেত্রে গণতান্ত্রিক বাংলাদেশের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে পুলিশ কাঠামোর ব্যাপক সংস্কারই পারে ভাবমূর্তি উজ্জ্বল করতে। প্রথমেই পুলিশ আইনে পরিবর্তন আনতে হবে- যা করা গেলে সমস্যার ৮০ শতাংশ নিজে থেকেই সমাধান হবে। এখানে ২০০৭ সালে প্রস্তাবিত পুলিশ অধ্যাদেশ-২০০৭ অনুসরণ করা যেতে পারে।
পুলিশ বাহিনীর সংস্কার বিষয়ে সাবেক আইজিপি মোহাম্মদ নুরুল হুদা ভোরের কাগজকে বলেন, সংস্কার হলে কতগুলো মোটা দাগের কাজ থাকে। সেক্ষেত্রে ১৮৬১ সালের পুলিশ আইন ব্যাপক সংস্কার ও পরিবর্তন প্রয়োজন আছে বলে অনেকেই মনে করেন। কারণ এই আইনগত কাঠামোতেই পুলিশ বাহিনী পরিচালিত হয়। এদিকে, পুলিশ বাহিনীর হাতে যেহেতু ক্ষমতা আছে আর ক্ষমতা থাকলেই তার অপব্যবহার সাধারণত হয়েই থাকে। সেক্ষেত্রে ক্ষমতার অপব্যবহার রোধের জন্য গ্রহণযোগ্য স্বাধীন তদন্ত সংস্থা করা যায় কিনা- যা পৃথিবীর কিছু-কিছু দেশে বিদ্যমান রয়েছে।
এছাড়া নিয়োগ নিয়ে অনেক অভিযোগ রয়েছে যে তা ঠিকমতো হয় না। কীভাবে নিয়োগ পদ্ধতি গ্রহণযোগ্য করা যায় তা দেখার বিষয় রয়েছে। অন্যদিকে, এ বাহিনীর পেশাগত দক্ষতা কীভাবে আরো বাড়িয়ে বিজ্ঞানমনস্ক করা যায় তাও দেখতে হবে। যে কাজগুলো পুলিশের কাজে ব্যাঘাত সৃষ্টি করে তা দেখারও বিষয় আছে।
পুলিশ সংস্কার বিচ্ছিন্নভাবে দেখার সুযোগ নেই উল্লেখ করে পুলিশের সাবেক এই কর্মকর্তা বলেন, অধিকাংশ বিষয় বা প্রতিষ্ঠানের সঙ্গেই পুলিশের সম্পর্ক রয়েছে। কাজে তাদের ম্যান্ডেট কী হবে তা পুলিশ আইনেও থাকবে এবং পুলিশ অন্য যাদের কাজে নিয়োজিত হবে সেখানকার আইনেও তার উল্লেখ থাকবে। যেমন পুলিশের গোয়েন্দা সংস্থার লোক যে রাজনৈতিক লোকদের পেছনে থাকে। সেটা কতখানি হবে। তারা কি সরকার না রাষ্ট্রের স্বার্থ দেখবে- তা দুই জায়গাতেই উল্লেখ থাকবে।
এক প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, সংস্কারকাজ কত সময় নেবে তা নির্ভর করে কী ধরনের লোক এই কাজের প্রধান হিসেবে রয়েছেন। তার চিন্তা কী। কত লোকবল কাজ করবে এখানে। এছাড়া রিফর্ম নিয়ে পড়াশোনা করাসহ অন্যান্য অভিজ্ঞ লোকদের সঙ্গে আলোচনা করতে হবে। এখানে বাংলাদেশে যেমন ১৯৮৮ সালে বিচারপতি আমিনুর রহমান ও তার আগে পাকিস্তান আমলে শেষের দিকে ১৯৬৯ সালে পুলিশ বাহিনীতে সংস্কার কাজ হয়েছিল। যতটুকু মনে পড়ে এক বছরের বেশি সময় লেগেছিল তাদের। আসলে রিফর্ম তো চলমান প্রক্রিয়া। একেবারে মোটা দাগের পরিবর্তন ছাড়া অন্যান্য বিষয়ে সংস্কার চলমান থাকবে।
আইন ও সালিশ কেন্দ্রের (আসক) নির্বাহী পরিচালক বিশিষ্ট মানবাধিকারকর্মী মো. নূর খান এ প্রতিবেদককে বলেন, পুলিশে সংস্কারের ক্ষেত্রে প্রথমত তাদের রাজনৈতিক ব্যবহার বন্ধে সর্বোচ্চ উদ্যোগ নিতে হবে। এছাড়া তাদের নিয়োগ, পদায়ন-বদলির স্বচ্ছ প্রক্রিয়া ও মানবিক পুলিশ হওয়ার প্রশিক্ষণ নিশ্চিত করতে হবে। এছাড়া কেউ অপরাধে জড়ালে তার যথাযথ শাস্তির বিষয়টি যাতে দ্রুত নিশ্চিত হয় তার ব্যবস্থা করতে হবে।
বিগত ২০০৭-৮ সালের তত্ত্বাবধায়ক সরকারের আমলে পুলিশ রিফর্ম-প্রজেক্টের (পিআরপি) অধীনে ২০০৭ সালে প্রস্তাবিত পুলিশ অধ্যাদেশ-২০০৭ প্রণয়ন করা হয়। তখন অধ্যাদেশটি অনুমোদন করার আগে জনমত যাচাইয়ের সিদ্ধান্ত হয়। অধ্যাদেশ অনুমোদনের পক্ষে ৭০ হাজার লোক মত দেন। মতামতসহ অধ্যাদেশটি আবার তৎকালীন প্রধান উপদেষ্টার কাছে পাঠানো হয়। তিনি
অভিমতসহ অধ্যাদেশটি পর্যালোচনার জন্য স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে পাঠিয়ে দেন। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের তৎকালীন অতিরিক্ত সচিবের নেতৃত্বে গঠন করা হয় পর্যালোচনা কমিটি। ওই কমিটি অধ্যাদেশের ২৩টি ধারাসহ কয়েকটি উপধারার ব্যাপারে আপত্তি জানায়। সেগুলো সংশোধন করে ২০১৩ সালে ফের একটি প্রস্তাবিত অধ্যাদেশ করা হয়- যা এখনো প্রস্তাবিত আকারে রয়েছে; যা অনুসরণ করলে বাকি ২০ শতাংশের পরিবর্তন আনা সম্ভব। এই আইনে পুলিশপ্রধানসহ ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের নিয়োগের জন্য ১১ সদস্য বিশিষ্ট পুলিশ কমিশন রাখা, অপরাধের অভিযোগ উঠলে যথাযথ বিচার করে শাস্তির জন্য পুলিশ ট্রাইব্যুনাল রাখা, সব ধরনের তদবির ও সুপারিশকে না বলার শক্ত কৌশল গড়ে তোলা, কর্মক্ষেত্রে রাজনীতি চর্চার অভিযোগে শাস্তিমূলক ব্যবস্থার প্রচলন, অপরাধ দমন নয় তার প্রতিকারে বেশি মনোযোগী হওয়া এবং নিয়মিত প্রশিক্ষণ আয়োজনের বিষয়ে গুরুত্ব দেয়া হয়েছে।
মাওলানা ভাসানী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্রিমিনোলজি অ্যান্ড পুলিশ সাইন্স বিভাগের অধ্যাপক ওমর ফারুক বলেন, বাংলাদেশ গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র হওয়ায় এখানে পুলিশ ব্যবস্থা হবে সরকারের চেয়ে বেশি জনগনের ও রাষ্ট্রের। সেই আলোকেই পুলিশ বাহিনী সংস্কার করতে হবে। আমাদের এখানে প্রো-একটিভ ও রি-একটিভ পুলিশিং হলেও গণতান্ত্রিক পুলিশিং নেই- যা অনেক উন্নত গণতান্ত্রিক দেশেই আমরা লক্ষ্য করে থাকি। এ ধরনের পুলিশিং ব্যবস্থায় জনগণের মানবাধিকার ও সম্মানের দিকে সবচেয়ে বেশী গুরুত্ব দেয়া হয়। এমনটা করা গেলে পুলিশ হয়তো এত বেপরোয়া হতে পারত না। এছাড়া বাংলাদেশ পুলিশ অধ্যাদেশ ২০০৭ সংস্কার প্রস্তাবের কিছু অংশ অনুসরণ ও ব্রিটিশ আমলের অনেক আইনের পরিবর্তন দরকার।
পুলিশের অতিরিক্ত ডিআইজি মো. সোহেল রানা ভোরের কাগজকে বলেন, নিয়োগ, পদায়ন ও পদোন্নতি সঠিক হলে সমস্যার অনেকটাই সমাধান হবে। এক্ষেত্রে, ২০০৭ সালের পুলিশ অধ্যাদেশটি বিবেচ্য হতে পারে। এর বাইরে, পদোন্নতির ক্ষেত্রে বিদ্যমান নিয়মের মতো নিয়োগকালীন জ্যেষ্ঠতাকে মূল বিবেচ্য না ধরে, একজন কর্মকর্তার পূর্বাপর সব শিক্ষাগত যোগ্যতা, সার্বিক সততা ও দীর্ঘ সময়ে তার অবদান, কাজ এবং সেবার মানসহ সব ধরনের যোগ্যতাকে প্রাধান্য দেয়া উচিত। পুলিশ প্রশাসন সংস্কার কমিশনের প্রধান হিসেবে দায়িত্ব নেয়া সফর রাজ হোসেনের সঙ্গে মোবাইলফোনে যোগাযোগ করা হলে তিনি কীভাবে সংস্কার কাজ করা হবে সে বিষয়ে কথা না বললেও ভোরের কাগজকে জানান, আগামী ১ অক্টোবর থেকে কাজ শুরু হবে। তখন সংস্কার বিষয়ে গণমাধ্যমের সঙ্গে কথা বলবেন তিনি।