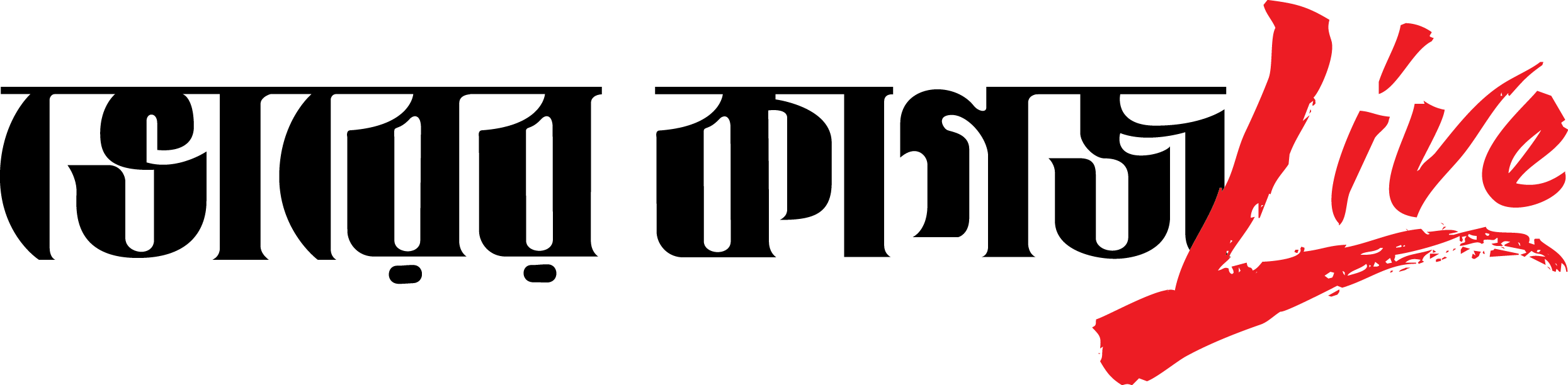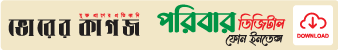ব্যবস্থাপনা গলদে অচল সড়ক
ইমরান রহমান
প্রকাশ: ২৪ নভেম্বর ২০২৪, ১২:০০ এএম
প্রিন্ট সংস্করণ

চতুর্মুখী ৮টি লেন মিলে বিএফডিসি সংলগ্ন রেইনবো ক্রসিং। এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ের একটি র্যাম্পও মিশেছে এই ক্রসিংয়ে। প্রতিটি লেনের জন্য সিগন্যাল বাতি থাকলেও আলো জ্বলে না তাতে। নেই কোনো রোড সাইন। মগবাজার থেকে সাতরাস্তাগামী লেনের সিগন্যাল বাতি উল্টো লাগানো। আশপাশে নেই কোনো বাস স্টপিস। হাতের ইশারায় চলা সিগন্যাল ব্যবস্থায় যাওয়ার অনুমতি মিললেও যাত্রীর অপেক্ষায় নড়তে চায় না বাস।
তড়িঘড়ি করে বাসে উঠতে সড়কের উপরই যাত্রীদের জটলা। ফুটওভার ব্রিজ ও জেব্রা ক্রসিংয়ের অস্তিত্ব না থাকায় হাতিরঝিলের দিক থেকে আসা কারওয়ান বাজারগামী হাজার হাজার পথচারী রাস্তা পার হচ্ছেন জীবনের ঝুঁকি নিয়েই। ফুটপাতজুড়ে ভ্যানগাড়ি ও টং দোকানের সারি। যেটুকু খালি থাকে সেটুকুর পরিবেশও অস্বাস্থ্যকর। ফলে, পথচারীদের যাতায়াত চলছে মূল সড়কের মাঝখানে থাকা ফ্লাইওভারের পিলারের পাশ দিয়ে।
গাড়ির চাপ সামলাতে সেখানে দায়িত্বরত সার্জেন্ট ও ট্রাফিক কনস্টেবলরা ছুটছেন এক লেন থেকে আরেক লেনে। আইন অমান্যকারী গাড়ি ও তাদের মধ্যে চলছে ‘চোর-পুলিশ খেলা’। পুলিশ সদস্যদের অনেকে ক্লান্ত হয়ে সড়কের এক পাশে বসে পড়ছেন, ৫ মিনিট না যেতেই আবার দৌড়াদৌড়ি শুরু করছেন। তীব্র গরমে ট্রাফিক বক্সে বসে যে একটু বিশ্রাম নেবেন, সে সুযোগও নেই। কারণ ফুটপাতের উপর নামকাওয়াস্তে বানানো বক্সে ফ্যান দূরে থাক, নেই বিদ্যুৎ সংযোগই। ফলে, ব্যস্ত সময়ে সিগন্যাল ব্যবস্থা সামলিয়ে অল্প কিছু গাড়িকে মামলা দিতে পারছেন সার্জেন্ট। এই হলো রাজধানীর ব্যস্ততম একটি ক্রসিংয়ের ট্রাফিক ব্যবস্থার চিত্র।
রাজধানীর গুলিস্তান মাজার, মিরপুর-১০ নম্বর গোলচত্বর, যাত্রাবাড়ী চৌরাস্তা, বাড্ডা লিংক রোড, মহাখালী আমতলীর অবস্থা আরো ভয়াবহ। শুধু এই কয়টি ক্রসিং নয়- এই চিত্র পুরো ঢাকা শহরের। গুলশান-২ নম্বর গোলচত্বর ছাড়া কোথাও জ্বলে না ট্রাফিক সিগন্যাল বাতি। ট্রাফিক ব্যবস্থাপনার এই বেহালদশার মধ্যে বেশ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ স্পটে ইঞ্জিনিয়ারিং ত্রুটি বাড়িয়েছে আরো বিপত্তি। সবকিছু মিলিয়ে সড়কের এই রুগ্নদশা যানজটের পাশাপাশি বাড়াচ্ছে সড়ক দুর্ঘটনা। বাড়ছে মৃত্যুর মিছিলও।
সংশ্লিষ্টরা বলছেন, সড়কে ট্রাফিক নিয়ন্ত্রণের দায়িত্ব পুলিশের হলেও সড়কের উন্নয়ন, সিগন্যাল ব্যবস্থা স্থাপন ও যে কোনো ধরনের সংস্কার কাজ করে থাকে সিটি করপোরেশন। কিন্তু এসব ক্ষেত্রে কখনো ট্রাফিক পুলিশের পরামর্শ নেয়া হয় না। ফলে, সড়ক ব্যবস্থাপনার ত্রুটিও দূর হয় না। যার প্রভাবে যানজটও কমছে না।
এ বিষয়ে ডিএমপির অতিরিক্ত কমিশনার (ট্রাফিক) খোন্দকার নজমুল হাসান ভোরের কাগজকে বলেন, রাজধানীর দুই সিটি করপোরেশনের সঙ্গে আমাদের কথা হয়েছে। এখন থেকে ট্রাফিক পুলিশের সঙ্গে আলোচনা করেই তারা সড়ক ব্যবস্থাপনার কাজগুলো করবে। এছাড়াও কাকলী বাস-বে, হাতিরঝিল চক্রাকার বাস ও ঢাকা চাকার মতো সুশৃঙ্খলভাবে চলতে থাকা উদ্যোগগুলোকে ট্রাফিক সমস্যা সমাধানে গুরুত্ব দেয়া হবে বলে জানিয়েছেন সংশ্লিষ্টরা।
সম্প্রতি সরজমিন যাত্রাবাড়ী ক্রসিংয়ে গিয়ে দেখা যায়, দক্ষিণবঙ্গ ও চট্টগ্রাম মহাসড়ককে সংযোগ করা এই ক্রসিং দূরপাল্লা ও সিটি সার্ভিস বাসে ঠাসা থাকে সব সময়। এরপরও এই ক্রসিংয়ে ট্রাফিক ব্যবস্থাপনা বলতে কিছুই নেই। যানবাহনের অথৈই সাগরে যেন ঠোঁটে বাঁশি ও হাতে লাঠি নিয়ে কোনোরকমে ভেসে থাকার আপ্রাণ চেষ্টা করে যাচ্ছেন তারা। নির্ধারিত বাস স্টপেজ, জেব্রা ক্রসিং ও ফুটওভার ব্রিজের ব্যবহার এখানে ‘সোনার হরিণ’। মূল সড়কের ৩ ভাগের ২ ভাগ থাকে বিভিন্ন পরিবহনের বাসের দখলে। চৌরাস্তার মাঝখানে বিশাল জায়গা নিয়ে যে গোলচত্বর করা হয়েছে, সেটির মধ্যে গড়ে উঠেছে নার্সারি। ফ্লাইওভার ব্রিজের পিলার ঘেঁষে প্রধান চত্বরের পাশেই করা হয়েছে পাবলিক টয়লেট। যাত্রাবাড়ী থেকে ধোলাইপাড় অংশে ফ্লাইওভারের নিচে যে জায়গাজুড়ে বর্জ্য স্থানান্তর কেন্দ্র, লেগুনা স্ট্যান্ড ও বিভিন্ন দোকানপাট করা হয়েছে; ওই জায়গাটা সড়কের আওতায় আনলে অনায়াসেই দূরপাল্লার বাসের জন্য একটি লেন বের করা যেত। যানজট সৃষ্টি হওয়ার সম্ভাবনাও থাকত না। নার্সারি গড়ে ওঠা চত্বর কাজে লাগিয়েও মূল সড়ককে চাপমুক্ত করার উদ্যোগ নেয়া যেত অনায়াসে।
কাকরাইল ক্রসিংয়েরও বেহাল দশা। ট্রাফিক বাতি থাকলেও আলো জ্বলে না বছরের পর বছর। বাস স্টপেজ বলতে কিছু নেই। শান্তিনগরের দিকে যেতে ‘বাস থামাবার জায়গা’ লেখা সংবলিত একটি নির্দেশিকা থাকলেও পাশেই দুই হাত দূরত্বে আরেকটি নির্দেশিকায় লেখা ‘পার্কিং নিষেধ’। এতে যে কেউ দ্বিধায় পড়বেন- তার কী করা উচিত। ফার্মগেটের বঙ্গবন্ধু চত্বরের সৌন্দর্য মুগ্ধ করার পাশাপাশি অবাকও করবে। কারণ অপরিকল্পিতভাবে গড়ে তোলা এই ‘সৌন্দর্য’ সড়কে যান চলাচলের বড় বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে। যান চলাচলের জন্য ক্রসিংয়ের এক পাশ বাঁশ দিয়ে বন্ধ করে দেয়া হয়েছে। এতে করে এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ের একটি র্যাম্পের গাড়িসহ অন্য যানবাহনকে সংসদ ভবনের সামনে দিয়ে ইউটার্ন নিতে হচ্ছে।
কারওয়ান বাজার ও মিরপুর-১০ নম্বর গোলচত্বরে বাস স্টপেজ না থাকায় ক্রসিংয়ের উপর দাঁড়িয়ে যাত্রী তোলে বাস। এতে বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে যানজট তীব্র আকার ধারণ করে। সাতরাস্তায় ফুটপাতের ওপর একটি বাস স্টপেজ থাকলেও ৫০ মিটার দূরত্বে থাকা সিএনজি পাম্পের গাড়ির সারিতে সেটি কোনো কাজেই আসছে না। বাড্ডা লিংক রোড এলাকাজুড়েই ফুটওভার ব্রিজ ও জেব্রাক্রসিং সংকটে জীবনের ঝুঁকি নিয়ে রাস্তা পার হন পথচারীরা। শুধু এই সমস্যাগুলোই নয়- ম্যানহলের ঢাকনা উঠে গর্ত তৈরি হওয়া, নিম্নমানের বিটুমিন ব্যবহারে সড়কে নদীর ঢেউয়ের মতো উচুঁ-নিচু অবস্থা তৈরি হওয়ার মতোও সমস্যা রয়েছে নগরের প্রায় সব সড়কেই।
হাতে গোনা বাস-বে, তাও দখলে : রাজধানীতে যাত্রীবাহী বাস দাঁড়ানোর জন্য তেমন কোনো বাস-বে নেই। হাতে গোনা যে কয়েকটা আছে, সেগুলোও বিভিন্নভাবে দখলে চলে গেছে। কোনোটি নির্দিষ্ট কোনো একটি পরিবহন তাদের স্ট্যান্ড হিসেবে ব্যবহার করছে। আবার কোনোটিতে হয়েছে সিএনজি অটোরিকশার পার্কিং স্ট্যান্ড। যেমন রাজধানীর গুলিস্তানের বাস-বে। মাজার থেকে জিপিও চত্বরগামী সড়কে যাত্রীবাহী বাস থামানোর জন্য করা হয়েছিল এটি। কিন্তু ওই বে-জুড়েই ১৫টির মতো টং দোকান বসানো হয়েছে। একপাশে করা হয়েছে সিএনজি অটোরিকশা ও ভ্যান রাখার পার্কিং।
বাস-বের উত্তর পাশের টং দোকানি সোহাগ হোসেন ভোরের কাগজকে বলেন, এখানে একটি বাসও প্রবেশ করে না। এটি করার আগে বাস যেভাবে মূলসড়কে দাঁড়িয়ে যাত্রী তুলতো, এখনো সেভাবেই তোলে। রাত হলে কয়েকটি বাসকে পার্কিং করা দেখতে পান তারা। বে-র সামনে মূলসড়কে যাত্রী তোলার জন্য দাঁড়িয়ে থাকা সদরঘাট-আব্দুল্লাহপুর রুটের ভিক্টর ক্লাসিক পরিবহনের বাসের (ঢাকা মেট্রো-হ ১৩-০২৭৩) চালক খালিদ হাসান ভোরের কাগজকে বলেন, এখানে (বাস-বে) আমাদের ঢুকতেই দেয় না লাইনম্যানরা। এজন্য আমরা আগের নিয়মে মূল সড়কে দাঁড়িয়ে যাত্রী তুলি। সবাইকে ঢুকতে দিলে আমি এখানে দাঁড়াতাম না। আর মূল সড়ক যাত্রীদের বাসে ওঠার জন্য নিরাপদও নয়।
গুলিস্তান থেকে মৎস্য ভবন হয়ে শাহবাগ-কারওয়ান বাজার পেরিয়ে ফার্মগেট গেলে চোখে পড়বে আরেকটি বাস-বে। আনন্দ সিনেমা হলসংলগ্ন এই বে-তে বেশ কয়েকটি বাস দাঁড়ানোর জায়গা আছে। কিন্তু এখানেও তেমন কোনো বাস প্রবেশ করে না। এটির একটি লেন ট্রাস্ট পরিবহনের বাসগুলোর জন্য ব্যবহৃত হয়। আরেকটি লেনে বিআরটিসির বাস ও কালেভদ্রে অন্য পরিবহনের কয়েকটি বাস প্রবেশ করে। এমনটি কেন হচ্ছে- কারো কাছে সেই প্রশ্নের উত্তর পাওয়া দুষ্কর। মহাখালী টার্মিনালের চিরচেনা যানজট কমাতে বাস-বে করে অবস্থার উন্নতি ঘটিয়েছিল ডিএমপির গুলশান ট্রাফিক বিভাগ। কিন্তু সেটিও বেশিদিন স্থায়ী হয়নি। বর্তমানে পরিস্থিতি আগের অবস্থায় ফিরে গেছে। সড়কের পাশেই দুই সারিতে পার্ক করা হচ্ছে দূরপাল্লার বাস।
কাজে লাগে না ‘অপরিকল্পিত’ ফুটওভার ব্রিজ : দারুস সালামের জাতীয় গণমাধ্যম ইনস্টিটিউটের পাশে স্বল্প দূরত্বে দুটি দৃষ্টিনন্দন ফুটওভার ব্রিজ করা হয়েছে। বিভিন্ন গাছ দিয়ে সৌন্দর্যবর্ধন করা এই দুটি ফুটওভার ব্রিজে ওঠেন না তেমন কেউ। কিন্তু মানুষের কাজে আসা শ্যামলীর ফুটওভার ব্রিজটি তেমন দৃষ্টিনন্দন নয়। উপরে ছাউনিও দেয়া হয়নি। ফলে, সাধারণ মানুষ কষ্ট করে এটিতে উঠতে চায় না। রাজধানীর সরকারি বাংলা কলেজের প্রধান ফটকের সঙ্গেই করা ফুটওভার ব্রিজেও কোনো ছাউনি নেই। রোদের তীব্রতা একটু বাড়লেই এই ফুটওভার ব্রিজ এড়িয়ে রাস্তা পার হন শিক্ষার্থীসহ অভিভাবকরা। আবার পর্যাপ্ত সুব্যবস্থা থাকার পরও সচেতনতার অভাব ও দীর্ঘদিনের অভ্যাসে মূল সড়ক দিয়েই রাস্তা পার হচ্ছে বেশির ভাগ মানুষ।
মিরপুর-১০ নম্বর গোলচত্বরের চতুর্দিকেই ফুটওভার ব্রিজ দিয়ে পারাপারের ব্যবস্থা থাকা সত্ত্বেও বেশির ভাগ মানুষই ব্যবহার করেন সড়ক। সেখানে কর্মরত ট্রাফিক সার্জেন্ট মো. আতিকুর রহমান ভোরের কাগজকে বলেন, ফুটওভার ব্রিজ ব্যবহার না করার প্রধান কারণ অসচেতনতা ও তাদের এটি ব্যবহারে বাধ্য না করা। এজন্য ৭০ শতাংশ মানুষ সড়ক দিয়ে পার হচ্ছে। এতে করে সড়কে গাড়ির গতি কমে ভয়াবহ যানজট সৃষ্টি হচ্ছে।
সিটি করপোরেশনের সঙ্গে ডিএমপির সমন্বয়হীনতা : ঢাকায় ট্রাফিক ব্যবস্থাপনার বেহালদশার মূল কারণ হিসেবে ইঞ্জিনিয়ারিং ত্রæটিকে অনেক আগে থেকে দায়ী করে আসছেন বিশেষজ্ঞরা। বিশেষ করে অচল সিগন্যাল বাতি, ওভারব্রিজ কিংবা আন্ডারপাস ও জেব্রা ক্রসিংয়ের পর্যাপ্ত ব্যবস্থা না থাকা, যত্র-তত্র গাড়ি পার্কিং, পথচারীদের ব্যবহারের জন্য ফুটপাত নিশ্চিত করতে না পারা, নির্দিষ্ট স্থান ছাড়াই যেখানে-সেখানে যাত্রী ওঠানো-নামানো, লেন ব্যবস্থা না থাকায় ওভার টেকিং করা ও যানবাহনের বেপরোয়া গতিকে অন্যতম সমস্যা হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। কিন্তু এই ত্রুটিগুলো ঠিক করতে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান হিসেবে সিটি করপোরেশনকে তেমন একটা কাজ করতে দেখা যায় না। অথচ ঢাকার দুই সিটি করপোরেশনেরই রয়েছে আলাদা ট্রাফিক ইঞ্জিনিয়ারিং সার্কেল। তারা ট্রাফিক ব্যবস্থা ঠিক রাখতে মাঠপর্যায়ে দায়িত্ব পালন করা ডিএমপির ট্রাফিক বিভাগের সঙ্গে আলোচনা করে কোনো প্রকল্প নেন না। সংশ্লিষ্টরা বলছেন, ট্রাফিক নিয়ে মাঠপর্যায়ে কাজ করে ট্রাফিক পুলিশ। সুতরাং, সড়কের সমস্যাগুলো তারাই সবচেয়ে ভালো বলতে পারবেন। তাদের সম্পৃক্ততা ছাড়া প্রকল্প নেয়া হলে সেটি কার্যকর হওয়ার সম্ভাবনা খুবই কম।
বিজ্ঞানসম্মত ভূমি ব্যবস্থাপনা জরুরি : যোগাযোগ বিশেষজ্ঞ ও বুয়েটের অ্যাকসিডেন্ট রিসার্চ ইনস্টিটিউটের সাবেক পরিচালক অধ্যাপক ড. মো. হাদিউজ্জামান ভোরের কাগজকে বলেন, সিগন্যাল বাতিই ট্রাফিকের সব সমস্যার সমাধান নয়। যারা ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব পালন করছেন, তাদের সবার আগে সড়কের সক্ষমতার সঙ্গে যানবাহনের সংখ্যার সামঞ্জস্য আনতে হবে। ধারণক্ষমতার ৩-৪ গুণ বেশি যানবাহন থাকলে কখনোই শৃঙ্খলা আসবে না। কারণ ঢাকা শহরে রাস্তা বাড়ানোর সুযোগ নেই। পাশাপাশি বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে ভূমি ব্যবস্থাপনা করা প্রয়োজন। গত দুই যুগে ৫ বার ট্রাফিকের বিভিন্ন প্রকল্প নেয়া হলেও ভূমি ব্যবস্থাপনার অভাবে তা কাজে আসেনি। মনে রাখতে হবে, সড়কের হৃৎপিণ্ড যাকে বলা হয়- সেই জংশন পয়েন্টগুলো দুর্বল হয়ে গেছে। এগুলোর আশপাশে বহুতল ভবন হয়েছে। যা বাস-বে ও আলাদা লেন তৈরির ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করছে।
তিনি আরো বলেন, ছোট যানগুলোর জন্য আলাদা লেন বানিয়ে মূল সড়কের যান চলাচল নিরবচ্ছিন্ন করার উদ্যোগ নিতে হবে। ট্রাফিক ইঞ্জিনিয়ারদের সংখ্যা বাড়াতে হবে। বলা হয়ে থাকে- প্রতি ২০ হাজার লোকের বিপরীতে একজন ট্রাফিক ইঞ্জিনিয়ার প্রয়োজন হয়। সে হিসেবে ঢাকায় ৬০০ জন ইঞ্জিনিয়ার প্রয়োজন। কিন্তু বাস্তবতা বড়ই কষ্টদায়ক। পরিশেষে তিনি বলেন, ঢাকার ট্রাফিক ব্যবস্থা ঠিক করতে গণপরিবহন বাড়ানো এবং ব্যক্তিগত গাড়ির সংখ্যা কমাতে নীতিনির্ধারণী পর্যায়ে সুপরিকল্পিত উদ্যোগ নিতে হবে।
দুই দশক আগের নীতিমালায় ট্রাফিকের জনবল : ডিএমপির ট্রাফিক সূত্র বলছে, একটি শহরে মোট আয়তনের ২০-২৫ শতাংশ সড়ক থাকার কথা। কিন্তু ঢাকায় রয়েছে ৭-৮ শতাংশ। সেইসঙ্গে রিকশা-ঠেলাগাড়ি থেকে শুরু করে কাভার্ড ভ্যানের মতো ২২ ধরনের যানবাহন এই শহরে চলছে। কিন্তু ট্রাফিক ব্যবস্থাপনা সেভাবে উন্নত হয়নি। প্রায় সব সিগন্যাল বাতিই বিকল। ফলে, ট্রাফিক সদস্যরা হাত উঁচিয়ে ট্রাফিক ব্যবস্থা সচল রাখার কাজটি করে যাচ্ছেন। যা বর্তমান সময়ে সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়িয়েছে।
সূত্র আরো জানায়, দিন দিন ঢাকার সীমানা ও সড়কের সংখ্যা বাড়লেও দুই দশক আগের নীতিমালায় ধার্য জনবল দিয়ে কার্যক্রম পরিচালনা করা হচ্ছে। ওই নীতিমালা অনুযায়ী, বর্তমানে ট্রাফিক বিভাগে ৪২১১ জনবল থাকলেও সড়কে দায়িত্ব পালন করতে পারছেন ৩৮০০ জন।
এ বিষয়ে ডিএমপির অতিরিক্ত কমিশনার (ট্রাফিক) খোন্দকার নজমুল হাসান ভোরের কাগজকে বলেন, আপাতত জনবল বৃদ্ধির পরিকল্পনা আমাদের নেই। কারণ ট্রাফিক ব্যবস্থা ঠিক করতে সচেতনতাই মূল ভূমিকা রাখতে পারে। আমরা সেদিকেই বেশি জোর দিচ্ছি। পাশাপাশি দেশীয় প্রযুক্তিতে ট্রাফিক সিগন্যাল ব্যবস্থা চালু, বাস-বে বাড়ানো ও যেগুলো আছে সেগুলো দখলমুক্ত রাখা, চালকদের নিয়মের আওতায় আনার মতো কাজগুলো শুরু করেছি। অতিরিক্ত কমিশনার আরো বলেন, বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের সময় রাজধানীর ১৬২টি ট্রাফিক বক্স পুড়িয়ে দেয়া হয়েছে। সিটি করপোরেশন নতুন করে সুপরিকল্পিত ট্রাফিক বক্স করে দেয়ার আশ্বাস দিয়েছে। আমরা মনে করি, চালক ও জনসাধারণ সচেতন হলে ট্রাফিক ব্যবস্থার অনেকটাই উন্নতি হবে।
ঢাকাতেই আছে ‘মুদ্রার উল্টো পিঠ’ : রাজধানীর বাস সার্ভিস ব্যবস্থায় মুদ্রার উল্টোপিঠের মতোই ‘হাতিরঝিল চক্রাকার বাস’ ও ‘ঢাকা চাকা’। কোনো যাত্রী বাস স্টপেজ ছাড়া বাসে ওঠেন না। বাস কর্তৃপক্ষও সুনির্দিষ্ট বাস স্টপেজ ছাড়া যাত্রী ওঠানামা করান না। অন্য সিটি সার্ভিস বাসে যত্রতত্র ওঠলে-নামলেও এই দুই বাস কর্তৃপক্ষের পরিকল্পিত ব্যবস্থাপনায় যাত্রীরা নির্দিষ্ট বাস কাউন্টার থেকে টিকেট কেটে অন্য বাস স্টপেই নামছেন।
হাতিরঝিল চক্রাকার বাসের ব্যবস্থাপনার দায়িত্বে থাকা মাসুদ করিম ভোরের কাগজকে বলেন, এইচ আর ট্রান্সপোর্ট এজেন্সির আওতায় ১৬টি বাস দিয়ে আমরা সেবা দিচ্ছি। আমাদের চালকদের ১২-১৫ হাজার টাকা মাসিক বেতন দেয়া হয়। পাশাপাশি প্রতিদিন খাবার বাবদ ২৫০ টাকা দেয়া হয়। আর হেল্পারদের প্রতিদিন ১৫০ টাকা বেতন ও খাবার বাবদ ৪০ টাকা দেয়া হয়। যদি কোনো বাসে কাউন্টার ব্যতিত টিকিট ছাড়া যাত্রী ওঠে- তাহলে চালক ও হেল্পারের খাবার টাকা দেয়া হয় না। ১০-২০ টাকা লাভের আশায় খাবার টাকা হারানোর ভয়ে তারা এই কাজ করেও না। কিন্তু বাইরে বিভিন্ন পরিবহনের বাসগুলো চুক্তিতে যাত্রী পরিবহন করে। তাদের মধ্যে যাত্রী ওঠানোর অসুস্থ প্রতিযোগিতার এটিই প্রধান কারণ। ঢাকা চাকা পরিবহনে নিয়মিত যাতায়াত করা গুলশান-২ নম্বরের ইউনিমার্টের কর্মী রূপা খানম ভোরের কাগজকে বলেন, কখনোই এই পরিবহন কাউন্টার ছাড়া যাত্রী তোলে না।
এই দুই বাস সার্ভিস ছাড়াও ‘কাকলী বাস স্টপ’ আরেকটি আদর্শ উদাহরণ হতে পারে। সড়কের উপর অঙ্কিত ‘বাস স্টপ সাইন’ বাসগুলোকে এনে দাঁড় করিয়ে দিচ্ছে যাত্রী ছাউনিতে। মূল সড়কের পাশে বাস দাঁড়ানোর পর্যাপ্ত জায়গা রাখা হয়েছে। এতে মূল সড়কে চলাচলকারী যানবাহনকে কোনোরকম বিপত্তিতে পড়তে হয় না। যাত্রীরাও বাস স্টপেজ থেকে নিরাপদে বাসে উঠতে পারছেন। একই বাস অন্য স্পটে যাত্রী উঠাতে মরিয়া থাকলেও এখানে সুশৃঙ্খলভাবেই যাত্রী তুলে আবার ছেড়ে যাচ্ছে। বাসে উঠতে যাত্রীদেরও হুড়োহুড়ি করার কোনো প্রয়োজন হয় না। ভিন্নতা রয়েছে বাস স্টপটির পাশের ফুটওভার ব্রিজটিতেও। রাস্তা পারাপারে এই ফুটওভার ব্রিজ ছাড়া কোনো বিকল্প না থাকায় সবাই বাধ্য হয়ে এটি ব্যবহার করছেন। ফলে, সড়কে পথচারী পারাপারের প্রভাব পড়ছে না। যানবাহনগুলো গতি বজায় রেখে চলাচল করতে পারছে।
ডিএমপি সূত্র জানায়, ঢাকা রোড সেফটি প্রজেক্টের (ডিআরএসপি) আওতায় এই বাস স্টপেজের জায়গা সম্প্রসারণ করা হয়। যেহেতু আইন প্রয়োগ না হলে কেউ নিয়ম মানতে চায় না, এজন্য সেখানে সার্বক্ষণিক একজন সার্জেন্ট রাখার ব্যবস্থা করা হয়। এরকম কিছুদিন চলার পর বাস চালকরা বুঝতে পারেন, এই বাস স্টপেজে নিয়ম না মানলে মামলা দেয়া হয়। তাই তারা নিয়ম মেনে বাস স্টপেজে দাঁড়াতে শুরু করেন। যাত্রীরাও বুঝে গেছেন, এখানে তাড়াহুড়ো করে বাসে উঠা লাগে না- বাস এমনিতেই থামে। এতে করে তারা নিজ থেকেই সড়কে জটলা না করে বাস স্টপেজে অপেক্ষা করেন। রাজধানীর সব বাস স্টপেজ এটির আদলে করা হলে- যত্রতত্র যাত্রী ওঠানামায় শৃঙ্খলা ফিরবে, এমনটাই মত সংশ্লিষ্টদের। ট্রাফিক ব্যবস্থাপনার সবচেয়ে ভালো উদাহরণ হতে পারে ক্যান্টনমেন্ট এলাকাও। ঢাকার ট্রাফিক ব্যবস্থা ঠিক করতে এ ধরনের পরিকল্পিত ও সুশৃঙ্খল উদ্যোগই বেশি প্রয়োজন বলে মনে করেন সংশ্লিষ্টরা।