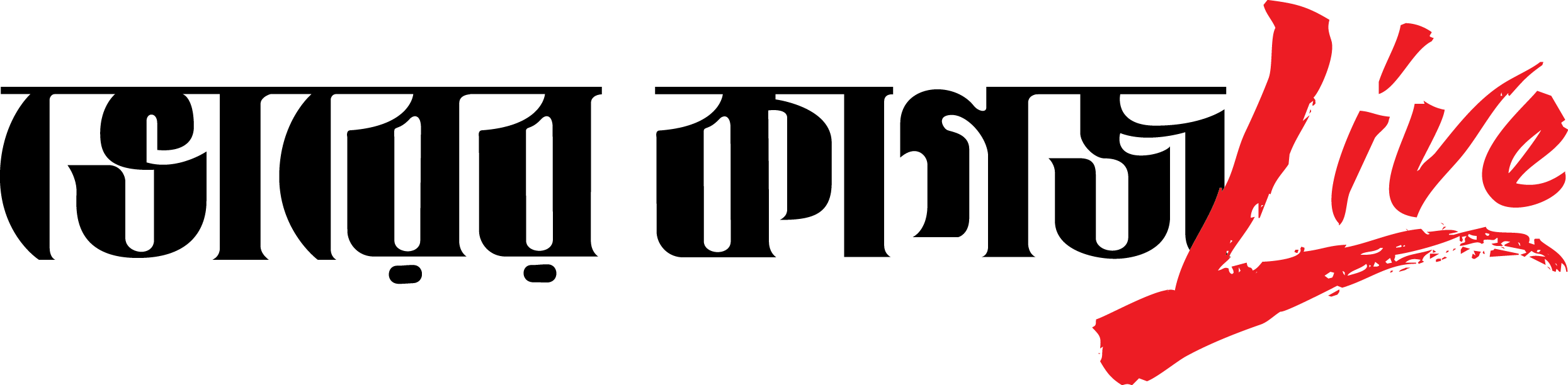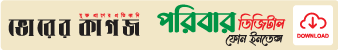সমাজতান্ত্রিক অক্টোবর বিপ্লবের শতবর্ষে আত্মজিজ্ঞাসা
মুক্তচিন্তা কলাম লেখক
প্রকাশ: ০৭ নভেম্বর ২০১৭, ০৭:৩৫ পিএম
চেতনায় প্রত্যাশাঅক্টোবর বিপ্লব শ্রমিক বিপ্লব বা শ্রমিক শ্রেণির পার্টির নেতৃত্বে বিপ্লব। আমাদের দেশেও শোষণ-শাসন থেকে মুক্তির জন্য অক্টোবর বিপ্লবের মতো বিপ্লব করতে হবে, এটাই ছিল প্রতিজ্ঞা। শ্রমিক বিপ্লব করতে হলে চাই শ্রমিক শ্রেণির দল। শ্রমিক শ্রেণি এক ও অবিভাজ্য এবং তাদের মধ্যে স্বার্থের কোনো দ্বন্দ্ব নেই। তাই তাদের নেতৃত্বে এমন বিপ্লব অপরিহার্য ও অনিবার্য।
কলামটা লেখা শুরু করেছি ৭ নভেম্বর ২০১৭ খুব ভোরে। আজ রুশ সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব বিজয়ের একশত বছর পূর্ণ হলো। পুরনো রুশ ক্যালেন্ডার অনুযায়ী ২৫ অক্টোবর তারিখে বিজয়ী হয়েছিল বলে এই অক্টোবর বিপ্লব নামে সুপরিচিত। আন্তর্জাতিক ক্যালেন্ডার অনুযায়ী পরে ওই তারিখটি হয় ৭ নভেম্বর। ছাত্রাবস্থায় ষাটের দশকের প্রথমদিকে যখন গভীর আবেগ নিয়ে বাম ছাত্র ইউনিয়নে যোগ দেই, তখন এই বিপ্লব সম্পর্কে বিপুলভাবে আগ্রহান্বিত হয়ে উঠি। স্টেডিয়ামের স্ট্যান্ডার্ড পাবলিসার্স নামে বইয়ের দোকানের কল্যাণে এক সময় আমেরিকান বিখ্যাত সাংবাদিক (বিপ্লবের সময় রাশিয়াতে ছিলেন) জন রিডের ‘দুনিয়া কাঁপানো দশদিন’ বইটি পড়ে ফেলেছি। এখনো মনে পড়ছে, ১৯৬৭ সালে চরম দমন-পীড়নের মধ্যে অক্টোবর বিপ্লবের ৫০ বছর পালন উপলক্ষে ৮ দিনব্যাপী অনুষ্ঠান সফল করার জন্য কর্মী হিসেবে (তখন ছাত্র ইউনিয়ন কেন্দ্রীয় কমিটির সহসাধারণ সম্পাদক) কাজ করার স্মৃতি। উৎসবের শেষদিন সন্ধ্যায় আউটার স্টেডিয়ামে ‘আমরা চলি অবিরাম’ ও কবিগান অনুষ্ঠিত হয়েছিল। এই গীতি আলেখ্যর রচয়িতা ও সঙ্গীত পরিচালনায় ছিলেন দুই দিকপাল শহীদ শহীদুল্লাহ কায়সার ও আলতাফ মাহমুদ। মানবজাতি সংগ্রাম করতে করতে গিয়ে পৌঁছাবে শোষণ-বৈষম্য নিপীড়নহীন স্বাধীনতা ও সাম্যের সমাজে, এটাই ছিল গীতি আলেখ্যের বিষয়। মন কি যে আলোড়িত হয়েছিল তখন! ভাবতে অবাকই লাগে। কলামের শুরুতেই দুই শ্রদ্ধেয় শহীদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করছি।
প্রসঙ্গত বলতেই হয় যে, রুশ দেশে অক্টোবর বিপ্লব-জাত সোভিয়েত ইউনিয়ন ছাত্রাবস্থায় তখন কতটা প্রভাবিত করেছিল, তা ভাষায় প্রকাশ করা যাবে না। কমিউনিস্ট পার্টির সার্বক্ষণিক হয়েছিলাম ওই বিপ্লব এবং দেশের প্রভাবে পড়েই। এখনো আমি যা, আমার চরিত্র বৈশিষ্ট্য যেরকম, তা অক্টোবর বিপ্লব এবং পরে ’৬৯-এর গণঅভ্যুত্থান, যাকে মনে করতাম আমাদের দেশের সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের ‘ড্রেস রিহার্সেল’, সুনির্দিষ্ট করে দিয়েছিল। আমরা মনে করতাম, বিংশ শতাব্দীর ‘সেরা ঘটনা’ অক্টোবর বিপ্লব এবং এই অপ্রতিরোধ্য বিপ্লব মানবজাতির স্বপ্ন বাস্তবায়নের সূচনালগ্ন। কিন্তু সোভিয়েত ইউনিয়ন ও বিশ্ব সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা যখন নব্বইয়ের দশকের শুরুতেই তাসের ঘরের মতো ভেঙে পড়ে, তখন মনে হয় এমনভাবে ভাঙন বিংশ শতকের সবচেয়ে ‘বড় স্বপ্নভঙ্গ’। কেন স্বপ্নভঙ্গ হলো? এটা কি অনিবার্য ছিল? কেন ভাবলাম না স্বপ্নভঙ্গ হতেও পারে? তাসের ঘরের মতো যেসব ভেঙে গেল, তার কোনো কি সংকেত আগেই পাওয়া গিয়েছিল? এসব প্রশ্ন নিয়ে যখন ভাবি, তখন আত্মজিজ্ঞাসার মুখোমুখি হই। ধারণা করি এই আত্মজিজ্ঞাসার মুখোমুখি হন আমার মতো তখনকার বাম ও কমিউনিস্ট আন্দোলনের অনেকেই। এই কলামটাতে কোনো তত্ত্বকথা নেই। কেবল আত্মজিজ্ঞাসা সংশ্লিষ্ট অভিজ্ঞতাসঞ্জাত কতক বিষয় পাঠকদের দরবারে তুলে ধরা হলো। এক. অক্টোবর বিপ্লব শ্রমিক বিপ্লব বা শ্রমিক শ্রেণির পার্টির নেতৃত্বে বিপ্লব। আমাদের দেশেও শোষণ-শাসন থেকে মুক্তির জন্য অক্টোবর বিপ্লবের মতো বিপ্লব করতে হবে, এটাই ছিল প্রতিজ্ঞা। শ্রমিক বিপ্লব করতে হলে চাই শ্রমিক শ্রেণির দল। শ্রমিক শ্রেণি এক ও অবিভাজ্য এবং তাদের মধ্যে স্বার্থের কোনো দ্বন্দ্ব নেই। তাই তাদের নেতৃত্বে এমন বিপ্লব অপরিহার্য ও অনিবার্য। কিন্তু আমরা যখন সমাজতন্ত্রের মন্ত্রে দীক্ষা নেই, তখনই ক্ষমতা হাতে নিয়ে সোভিয়েত ইউনিয়নে পার্টি ও রাষ্ট্রের নেতা স্ট্যালিন নিজ দলের মানুষকে হত্যা করেছিলেন কথাটা যেমন শুনি তেমনি ‘ডিসস্ট্যানাইজেশন’ বা তাতে রাষ্ট্র ও সমাজ জীবন উৎখাত করার কথাও শুনি। ইতোমধ্যে শ্রমিক শ্রেণির পার্টির নেতৃত্বে পরিচালিত দুই দেশ রাশিয়া বনাম চীন দ্ব›দ্ব শুরু হয়। আমাদের এখানেও রুশ-চীন আদর্শগত মতভেদ পার্টি তীব্র হয়ে উঠলে কমিউনিস্ট পার্টি ভেঙে যায়।
পরে স্বাধীনতার পর ১৯৭৩ সালে যখন বার্লিন যুব উৎসবে যাই, তখন দ্বিপক্ষীয় আলোচনার জন্য যখন পোল্যান্ড ও হাঙ্গেরির প্রতিনিধিদলের সঙ্গে আলোচনা করতে যাই, তখন আমি কমিউনিস্ট পার্টি প্রতিনিধি ছিলাম বলেই হয়তো আমাকে ডেকে নিয়ে ওদের কেউ কেউ এমন কথা বলে, রুশ পার্টির দাদাগিরি মেনে নেয়া যায় না। ঠিকানা দিতে চায় তারা। যোগাযোগ রাখতে বলে। তাদের এভয়েড করাটাই ছিল আমার জন্য স্বাভাবিক। পরে ঢাকা এসে আমি এটা পার্টিকে রিপোর্ট করি। এখন এই আত্মজিজ্ঞাসার মুখোমুখি হই এই প্রশ্নে যে, শ্রমিক শ্রেণি এক ও অবিভাজ্য শ্রেণি, তাদের স্বার্থের মধ্যে কোনো দ্ব›দ্ব ও সংঘাত নেই, এমন স্বতঃসিদ্ধটা এত সহজ ও সরলভাবে সেই দিনগুলোতে মনে করা কি সঙ্গত হয়েছে? দুই. একইভাবে ‘স্বশ্রেণিত্যাগী’ (ডিক্লাশড) শব্দটাও সহজ সরলভাবেই মেনে নিয়ে নিজে তা হতে চেষ্টা করেছিলাম। কারণ ডিক্লাশড না হয় তো কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য হওয়া যায় না। যখন ছাত্র ছিলাম বা চাকরি ব্যবসা ইত্যাদি পেশায় না গিয়ে পার্টি অফিসের স্টোররুমের মতো একটা ঘরে থাকতাম, তখন তা নিয়ে মনে কোনো দ্বিধাদ্ব›দ্ব ছিল না। তবে পার্টির মধ্যে তখন এই প্রশ্নে তর্ক-বিতর্ক চরমে উঠেছিল। বিশেষ কারণের পেছনে ছিল, পার্টি অফিসকে তখন চ‚ড়ান্ত আধুনিকভাবে গুছানোর পরিকল্পনা চলছিল। এতে এতটা বিভ্রান্তি সারাদেশে ছড়িয়ে পড়েছিল যে, ২১ পুরানা পল্টনের সেই হলুদ অফিসের যে ঘরে কমরেড মণি সিংহ বসতেন, সেই ঘরে এয়ারকন্ডিশন রয়েছে। জানালায় এয়ারকন্ডিশনের পেছনের পরিত্যক্ত একটা খোল ছিল। ওটা খুললে বন্ধ করতে অর্থ লাগবে, এই বিবেচনায় প্রথমে রেখে দেয়া হয়েছিল। তাতে প্রশ্ন দাঁড়ায়, পার্টি অফিসে এয়ারকন্ডিশন কেন? পার্টি কি বুর্জোয়া হয়ে গেছে? মফস্বল থেকে টেলিফোন বা চিঠি আসতে থাকে। এসব প্রশ্নে জর্জরিত হওয়া ভিন্ন উপায় ছিল না। পরে ওটা যেমন খোলা হয় তেমনি অফিসের জাঁকজমকও কাটছাঁট করা হয়।
অপরের সমালোচনায় কেন, সংসার করতে গিয়ে নিজেরাই এই প্রশ্নে দগ্ধ হয়েছি। থাকা-খাওয়া-চালচলন, পুরনো সবচেয়ে ছোট একটা ফ্রিজ কেনা, ছেলেকে সেন্ট জোসেফ স্কুলে ভর্তি করানো প্রভৃতি যে কোনো কিছু করার সময়েই নিজে অসামঞ্জস্যতায় ভুগেছি, দগ্ধ হয়েছি। পরে এক সময় যখন ক্ষেতমজুর আন্দোলন দেশব্যাপী শক্ত অবস্থান নিয়ে গড়ে ওঠে, তখন একবার কলকাতা যাওয়ার সময় ফরহাদ ভাই বললেন, ওখানে গিয়ে বিহারের ক্ষেতমজুর আন্দোলন (সেখানে আশির দশকে শক্তিশালী ক্ষেতমজুর আন্দোলন ছিল) সম্পর্কে জেনে আসবেন। খোঁজ নিতে গিয়ে জানলাম, সমস্যা হচ্ছে আন্দোলন-সংগঠনের কাজের ভেতর দিয়ে ক্ষেতমজুর যারা নেতা হন, তাদের অনেকেই ক্রমে পেটি বুর্জোয়া বনে যান এবং সুবিধাবাদী ও সুযোগসন্ধানী হয়ে ক্ষেতমজুরদের থেকে বিচ্ছিন্ন হন। এটা যেন উল্টো স্বশ্রেণিত্যাগ! এখনো যখন শ্রমিক কৃষক মেহনতি জনতার মুক্তির বিষয়টা ভাবি, তখন আত্মজিজ্ঞাসার মুখোমুখি হই এই ভেবে যে, আদৌ মধ্যবিত্ত বা উচ্চবিত্ত পরিবার থেকে আসা কোনো ব্যক্তি স্বশ্রেণিত্যাগী হতে পারেন কি? স্বশ্রেণিত্যাগ সমাজে কোন মুখী, ওপরমুখী না নিচমুখী? আত্মজিজ্ঞাসার প্রশ্নটা পাঠকদের কাছেই রাখলাম।
তিন. পার্টির সদস্যপদ পাওয়ার আগে ষাটের দশকের শুরুতে গোপনে পার্টি ক্লাস নিতেন পদার্থ বিজ্ঞানের ছাত্র কাজী ভাই। তিনি ক্লাসে বেশ কয়েকবার কবিগুরুর ‘রাশিয়ার চিঠি’-এর উদ্ধৃতি দিয়েছিলেন। কবিগুরু লিখেছেন, ‘রাশিয়ায় না এলে এ জন্মের তীর্থদর্শন অসমাপ্ত থাকত।’ আমাদের দেশকেও করতে হবে তীর্থক্ষেত্র, এই আবেগে সাথীরা মিলে ওই বইটি পড়েছিলাম। উল্লিখিত ওই বাক্যটির সঙ্গে আরো একটি বাক্য তখন স্মরণে রেখেছিলাম, ‘বিশ্ব ইতিহাসের সবচেয়ে বড় কর্মযজ্ঞের অনুষ্ঠান’ না দেখলে তা ‘আমার জন্য অমার্জনীয় হতো’। বলতে দ্বিধা নেই আর ওই বইয়ের আর কোনো বাক্যই মনে দাগ কাটতে পারেনি। তখন ওই বইতে লেখা ‘ গলদ আছে’, ‘ছাচে ঢালা মনুষ্যত্ব কখনো টিকে না’, ‘মন যাবে মরে আড়ষ্ট হয়ে কিংবা কলের পুতুল হয়ে দাঁড়াবে’, ‘জবরদস্তি’, ‘মত স্বাতন্ত্র্যের অধিকার মানতে চায় না’, ‘প্রতারণা বা নিষ্ঠুরতা’ প্রভৃতি কথাগুলো চোখে দেখেনি বা মনে দাগ কাটেনি। কি আশ্চর্য! কবিগুরু যে চিঠিতে লিখেছেন ‘তীর্থদর্শন’ বাক্যটি, সেই তৃতীয় চিঠিতে তিনি একটি বাউল সঙ্গীত দিয়ে চিঠির সমাপ্তি করেছেন। সঙ্গীতটা হলো, ‘নিঠুর গরজী,/তুই কি মানস মুকুল ভাজবি আগুনে?/ তুই কি ফুল ফুটাবি/ বাস ছুটাবি সবুর বিহনে।/দেখ-না আমার পরম গুরু সাঁই/ সে যুগযুগান্তে ফুটায় মুকুল,/তাড়াহুড়া নাই।’ এখন প্রায়ই এই বাউল গানটা সুরবিহীন সুরে মনে মনে গাই। আর আত্মজিজ্ঞাসার মুখোমুখি হই এই ভেবে যে, যুবক বয়সে এতটা অন্ধ হওয়া কি ঠিক হয়েছে?
চার. স্বাধীনতার পর পার্টির প্রকাশনা সংস্থা ‘প্রাচ্য প্রকাশনী’ বুলগেরিয়ার কমিউনিস্ট নেতা জর্জি ডিমিত্রভের ‘যুক্তফ্রন্ট’ বিষয়ে বইটি প্রকাশ করার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করে। একতা সম্পাদক মতিউর রহমান (বর্তমানে প্রথম আলো সম্পাদক) আমাকে বই ছাপানোর উপযোগী করে এবং ভ‚মিকা লিখে দিতে বলেন। ইংরেজির সঙ্গে বাংলা অনুবাদ মিলিয়ে দেখার সময় আমার নজরে আসে, একটি ইংরেজি কপিতে আছে সোভিয়েত নেতা স্ট্যালিনের অকুণ্ঠ প্রশংসা বাণী, যা বাংলা বা অন্য ইংরেজি কপিতে নেই। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর বুলগেরিয়াসহ পূর্ব ইউরোপ ফ্যাসিবাদ মুক্ত এবং কমিউনিস্ট পার্টির একনায়কত্বের আওতায় আসায় জর্জি ডিমিত্রভের এমন প্রশংসা করাটাই ছিল স্বাভাবিক। দেশে প্রত্যক্ষ-পরোক্ষ সামরিক আইনের মধ্যে তখন মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস বিবৃতি ও কর্তন চলছিল। পার্টির বিরুদ্ধে সংগ্রাম করছিল। এই প্রেক্ষাপটে ইতিহাসের বড় এক অংশবাদ তথা এমন কর্তন মেনে বই প্রকাশ করা ঠিক হবে কিনা প্রশ্নটি মনে এসেছিল। পরে ঠিক হলো স্ট্যালিনের প্রশংসা বাদ দিয়েই বইটি ছাপানো হবে। এখনো তাই আত্মজিজ্ঞাসার মুখোমুখি হই এই ভেবে যে, ঐতিহাসিক ঘটনার মধ্যে ছুরি চালানো কিংবা বিকৃত করা কি রাজনীতি ও ক্ষমতার অনুষঙ্গ? এটা করা কি নৈতিক? রাজনীতি ও নৈতিকতার আন্তঃসম্পর্ক কি? ভেবে ভেবে কখনো মনে হয়, এন্ড জাস্টিফাই দি মিনস। আবার কখনো এটা ভুল মনে হয়। ধারণা করি, এই আত্মজিজ্ঞাসার উত্তর আর এই জন্মে খুঁজে পাব না।
পাঁচ. কমিউনিস্ট পার্টি অফিস তখন ভীষণ ব্যস্ত। তখন একটি ফটোস্টাট মেশিন কেনার প্রয়োজন পড়ল। না কেনার সিদ্ধান্ত গৃহীত হলো এবং মস্কোতে জানানো হলো যাতে সেখানকার পার্টি আমাদের একটি মেশিন উপহার দেয়। এল মেশিন। কিন্তু ক্যাটালগ নেই। কোনো মেকানিক্স তা ফিট করতে পারে না। ভাবলাম সমাজতন্ত্রের মেশিনের সঙ্গে ধনতন্ত্রের মেশিনের পার্থক্য তো থাকবেই। চলল খোঁজ, কে এটা চালু করতে পারে। ওয়ারীর ইসরাফিলকে পাওয়া গেল। সে চালু করে দিল ঠিকই। কিন্তু বলল, এটা ব্যবহার করা যাবে না। কারণ এই টেকনোলজি অচল। পরে শুনলাম সমাজতান্ত্রিক দেশের গোপন দলিলপত্র সব ধনবাদী সাম্রাজ্যবাদী দেশ পেয়ে যাবে, সেজন্য এর উন্নত সংস্করণ সেখানে করা হয়নি। আরো একটি বিষয় ছিল, সোভিয়েত ইউনিয়ন ভ্রমণে গিয়ে ঘড়ি কেনে আনা ছিল সস্তা বলে প্রথমে খুবই জনপ্রিয়। কমবেশি সময়ে নষ্ট হওয়াটাই ছিল বিধিলিপি। কেবল বাংলাদেশ-সোভিয়েত মৈত্রী সমিতির কালিদার (প্রয়াত) ঘড়িটা বেশ কিছুদিন টিকে ছিল। আমরা তাকে খেপাতাম এই বলে যে, মৈত্রী সমিতি করায় ভালো ঘড়িয়া উনার ভাগ্যে পড়েছে।
তাত্ত্বিক নেতা অনিলদা এক সময় আমাদের প্রবোধ দিয়ে বললেন, শীতের দেশের ঘড়ি গরমের দেশে এসে নষ্ট হয়ে যায়। যে দেশ এটম বোমা বানাতে পারে, যে দেশ মহাশূন্য অভিযানে আমেরিকাকে পাল্লা দেয়, সেই দেশ কি বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিতে পিছিয়ে থাকতে পারে! প্রসঙ্গত বলি, বার্লিন ওয়াল ভাঙার আগে অজয়দা ও আমি পূর্ব জার্মানি ও সোভিয়েত ইউনিয়নের তাত্ত্বিকদের সঙ্গে আলোচনার জন্য মস্কো ও বার্লিন যাই। মস্কো থেকে বার্লিন যাওয়ার পথে এক ব্র্রিটিশ মহিলা আমার পাশে বসেছেন। তার স্বামী আর্মি অফিসার হিসেবে মস্কো ও বার্লিনে কিছুদিন থেকেছেন। প্রয়াত স্বামীর স্মৃতি স্মরণ করতে তিনি মস্কো ও বার্লিন দেখতে এসেছেন। আমি তাকে বললাম, কি দেখলে আর কি বুঝলে মস্কো থেকে। দশাসই সেই মহিলাটি হেসে বললেন, এখানে সব আমার মতো বড় ও মোটা। নড়তে পারে না। সুক্ষতা নেই। সমষ্টি আছে, ব্যক্তি অনুপস্থিত। পছন্দ নির্ভর করে সমষ্টির ওপর, ব্যক্তি সেখানে অনুপস্থিত। পছন্দ না হওয়ায় কিছু কিনতেও পারি নি। আমি বললাম, এই জন্যই তো গ্লাসনস্ত ও প্রেস্ত্রোইকা। তিনি প্রশ্ন করলেন, এতদিন যা কেবল বড় হয়েছে, তা কি এক ধাক্কায় কমে যাওয়া সম্ভব? আমিও কি আর এই বয়সে শরীরের মেদ কমাতে পারব? এখন ভাবি, তিনি কি সোভিয়েত ইউনিয়ন ও সমাজতান্ত্রিক বিশ্ব ভাঙার সংকেত আমাকে দিয়েছিলেন? এই আত্মজিজ্ঞাসার উত্তর কখনো দিতে পারব না।
ছয়. ডেমরার বাওয়ানি চটকলের শ্রমিক ও মুক্তিযোদ্ধা আজিমউদ্দিন চাচাকে তখন আমরা কমবেশি সবাই চিনতাম। শ্রমিকদের দেশ দেখতে রাশিয়া যাবেন। কি যে খুশি! স্বপ্নের দেশ দেখবেন। ফিরে এলেন তিনি। পরে একদিন মন খারাপ করে ছোট অফিস ঘরটাতে আমার টেবিলের সামনের একমাত্র চেয়ারটাতে বসলেন। মন খারাপ। বাবুলালকে চা আনতে বলে কেন মন খারাপ প্রশ্ন করলাম। বললেন রাশিয়ার শ্রমিকরা ‘কুইড়া’ হয়ে গেছে। এমনটা হলে কি সাম্যবাদ হবে? ঘটনা জানতে চাইলে তিনি বললেন, তারা যখন সকালে একটি কারখানা দেখতে যান, তখন দেখতে পান শীতের সময় বরফের কারণে জমে থাকা ময়লা পরিষ্কার করার জন্য ৬/৭ জনের একদল মানুষ জড়ো করা হয়েছে। তখন চাচার মনে প্রশ্ন জাগল আমাদের দেশের চারজন লোকের যেখানে একদিনের কাজ, সেখানে এত লোক কেন? ফেরার সময় দেখলেন, অর্ধেকেরও কম ময়লা পরিষ্কার করা হয়েছে। দোভাষীর কাছে প্রশ্ন করে তিনি জানলেন, আরো দুদিন লাগবে ওটা পরিষ্কার করতে।
শ্রমিকরা ‘কুইড়া’ হয়ে গেছেন, তাই তিনি শঙ্কিত। ওই দিন আমি বইয়ের মুখস্ত করা বিদ্যা থেকে যে উত্তর তাকে দিয়েছিলাম, তা ভাবলে এখন লজ্জায় মনে হয়, ধরণী দ্বিধা হও। যতটুকু মনে পড়ে বার্লিন ওয়াল ভাঙার আগে উল্লিখিত ওই তাত্ত্বিক আলোচনায় এক বৃদ্ধ বলেছিলেন, পশ্চিম জার্মানি থেকে পূর্ব জার্মানির শ্রমের উৎপাদনশীলতা অর্ধেক। তবে সমাজতান্ত্রিক দেশগুলোর মধ্যে পূর্ব জার্মানি আছে এগিয়ে। এটা এখন পরিবর্তন করতে হবে। তখনই আমার মনে পড়েছিল, অজিমউদ্দিন চাচার কথা। তিনি বুঝলেন ‘কুইড়া’ বিষয়টা। কিন্তু আমি! আজ আত্মজিজ্ঞাসার মুখোমুখি হই এই ভেবে যে, আমি তখন জার্মান মহাকবি গ্যাটের কবিতাটা জানা সত্ত্বে ও কিছু বুঝতে পারিনি কেন? তিনি লিখেছিলেন, ‘তত্ত্ব বড় নিরস বন্ধু,/প্রাণতরু সহজ সরল।’ আজ থেকে ১৫০ বছর আগে মহামতি কার্ল মার্কস যখন সমাজ বিকাশের ক্ষেত্রে নতুন চিন্তার উদ্ভব ঘটিয়েছিলেন তখন তিনি ‘একটি চরম সত্য ধারণকারী, অনঢ়, স্বয়ংসম্পূর্ণ, শাস্ত্রবদ্ধ, মতান্ধ ও গোঁড়ামিপূর্ণ মতবাদ’ হিসেবে তার উদ্ভাবিত তত্ত¡কে না দেখতে বলেছিলেন। প্রকৃত বিচার পরিস্থিতি পাল্টে গেলে তত্ত¡ ‘নিরস’ হয়ে যায়। তাই মার্কস লিখেছিলেন, ‘যা কিছু বিদ্যমান তার বিরুদ্ধে নির্মম সমালোচনা চালিয়ে যাওয়া, নির্মম অর্থে যে পরিণাম উদ্ভ‚ত হবে তাতে ভীত না হওয়া’ প্রয়োজন। অজিমউদ্দিন চাচা আসলে কি পার্টি শৃঙ্খলার ভয়ে ভীত হয়ে একান্তে ‘কুইড়া’ শব্দটা আমাকে বলেছিলেন? আমি তখন সেই কথার পাত্তা দেইনি। আত্মজিজ্ঞাসাটা কত বিশাল ওজনের বোঝা, তা কি কল্পনা করো চলে!
সাত. উল্লিখিত তাত্তি¡ক আলোচনার পর বার্লিনে শেষদিন আমার বয়েসী সমাজবিজ্ঞানে ডক্টরেট পার্টির স্টাফ জার্মান মহিলা দোভাষী আমাকে বলল, তুমি কি ক্লান্ত? গাড়িতে না উঠে চলো গল্প করতে করতে হোটেলে হেঁটে যাই। ওর সঙ্গে বেশ বন্ধুত্ব হয়েছিল। আমি কথা ফাঁস করব না ভেবে সে কিছু বলতে চাইছে। আমি রাজি হয়ে গেলাম। কথার শুরুতেই মনে হলো সে ভীষণ ক্ষুব্ধ বিরাজমান ব্যবস্থার প্রতি। এক সময় রেগে বলল, গাড়ি কিনতে চায়। দরখাস্ত করেছে। কবে পাবে কে জানে! কেউ কেউ পায় বেশ বয়স হলে। ওই বয়সে গাড়ি দিয়ে কি হবে? পশ্চিম জার্মানি যাও। সঙ্গে সঙ্গে গাড়ি ও চাবি পেয়ে যাবে। আমি অবাক! সে বলল, পরিবর্তন হবেই। এটা রোধ করার সাধ্য কারো নেই। পরে সন্ধ্যায় যখন বার্লিন টাওয়ারে উঠেছি, তখন মোমবাতি মিছিল হচ্ছে। আমি আমাদের দেশের মশালের কথা বলে তাকে প্রশ্ন করলাম, মোমবাতি কেন? সে বলল, ওটা গির্জার প্রতীক। একনায়কত্বের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ। প্রসঙ্গত আমরা বার্লিন থাকতেই নেতা হোনেকার অপসারিত এবং ক্রেইনস ক্ষমতাসীন হন। দলের এক সিদ্ধান্তে দেশের ক্ষমতা বদল। দেশে এসে যখন ঠাকুরগাঁওয়ে পার্টির জেলা কমিটির বর্ধিত সভা করছি, তখন শুনতে পেলাম বার্লিন ওয়াল ক্ষুব্ধ জনতা ভেঙে দিয়েছে। তবুও আমি ছিলাম কট্টরপন্থী। কেননা মস্কোর তাত্তি¡করা বলেছিল, গ্রাসনন্ত ও প্রেস্ত্রোইকা সমাজ ও রাষ্ট্র জীবনে প্রয়োগের ফলে সমাজতন্ত্রের পালে হাওয়া লেগেছে। অক্টোবর বিপ্লবজাত সোভিয়েত সমাজতন্ত্র অপরিবর্তনীয়। কিন্তু কিছুদিন পরই জানলাম, ক্রিমিয়া থেকে ছুটি শেষ করে এসে সোভিয়েত নেতা গর্ভচেভ বলেছেন, সোভিয়েত বিপ্লব পরাজিত হয়েছে।
এই শেষ বয়সে এসে প্রকৃতপক্ষে পার্টি জীবনের গৌরবের দিনগুলোর কথা যেমন মনে পড়ে, তেমনি উল্লিখিত এবং এখানে অনুল্লিখিত ঘটনা ও অভিজ্ঞতা বিবেচনায় এনে সদাসর্বদা আত্মজিজ্ঞাসার মুখোমুখি হই। অনেক সময়ই নির্মম সমালোচনায় নিজে নিজেই প্রশ্নে প্রশ্নে ক্রশবিদ্ধ হই। মনে রক্ত ঝড়ে। বাংলার দুঃখী মানুষের মুখে হাসি ফোটানোর জন্য চার মূলনীতির এক নীতি সমাজতন্ত্রের কথা মনে পড়ে। ক্ষুধা দারিদ্র্য শোষণ বঞ্চনা নির্যাতন নিপীড়ন বেকারত্ব থেকে মুক্তির আকাক্সক্ষা ও প্রত্যাশা তখন সমাজতন্ত্র শব্দের ভেতর দিয়ে অভিব্যক্ত হয়েছিল। অভিজ্ঞতার আলোকে কমিউনিস্ট পার্টি যখন ছেড়ে আসি, তখন ‘মার্কসবাদ: একটি জীবন্ত মতাদর্শ/একটি আলোচনার সমালোচনা’ পুস্তিকায় লিখেছিলাম, ‘সত্যের মুখোমুখি নির্মমভাবে দাঁড়ানোর অর্থ তাকে সম্পূর্ণ পরিত্যাগ বা বিসর্জন দেয়া নয়। মানবজাতির যে কোনো মহৎ কর্মকাণ্ড-মতামত-প্রচেষ্টা ছেঁড়া জামার মতো পরিত্যাগ বা বিসর্জন দেয়া যায় না। মার্কস-এঙ্গেলস-লেনিন শোষণমুক্ত সমাজের স্বপ্ন দেখেছিলেন। তারা সেই চিন্তার বাস্তব রূপ দিতে চেয়েছিলেন। কোনো নির্দিষ্ট দেশের সমাজ ল্যাবরেটরি নয় যে, একই সময়ে ভিন্ন ভিন্ন চিন্তা-মতামত পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা চলে। মানবসভ্যতার অগ্রগতির সংগ্রামে মার্কসবাদ-লেনিনবাদ তত্ত¡ ও প্রয়োগ এবং তা থেকে প্রাপ্ত অভিজ্ঞতা ইতিহাসের স্বপ্নভঙ্গ হলেও বিশাল আলোকবর্তিকা হয়ে থাকবে। ওই তত্ত¡ ও প্রয়োগের বিরাট অভিজ্ঞতা আছে আবার এর বাইরেও জগৎ আছে; জীবন, সত্য ও চিন্তা আছে।’ এই কথাগুলো অক্টোবর বিপ্লবের শততম বার্ষিকী পূর্তির দিনে আবারো স্মরণ করলাম।
কবিগুরু মৃত্যুর আট মাস আগে ‘রোগশয্যায়’ কাব্যগ্রন্থের ‘ওরা কাজ করে’ কবিতায় লিখেছেন, ‘ওরা কাজ করে/নিরন্তর দেশে দেশান্তরে/..অনিঃশেষ প্রাণ? অনিঃশেষ মরণের স্রোতে ভাসমান/ পদে পদে সংকটে সংকটে/নামহীন সমুদ্রের নিরুদ্দেশ তটে। পৌঁছিবারে অবিশ্রাম বাহিতেছে খেয়া/কোন সে অলক্ষ দেয়া/মর্মে বসি দিতেছে আদেশ,/নাই তার শেষ।’ কবিগুরু সাগর তীরের শেষ শেষ নাই বলে মন্তব্য করেছিলেন। আত্মজিজ্ঞাসার মুখোমুখি হয়ে যখন ভাবি, শোষণমুক্তির তীরের দেখা আদৌ পাবে কিনা মানবজাতি ঊষালগ্ন থেকে চিন্তিত চর্চিত ও প্রয়োগকৃত সাম্যের সমাজ তীরের? জানি না! উত্তর আমার কাছে নেই।
শেখর দত্ত : রাজনীতিক, কলাম লেখক।