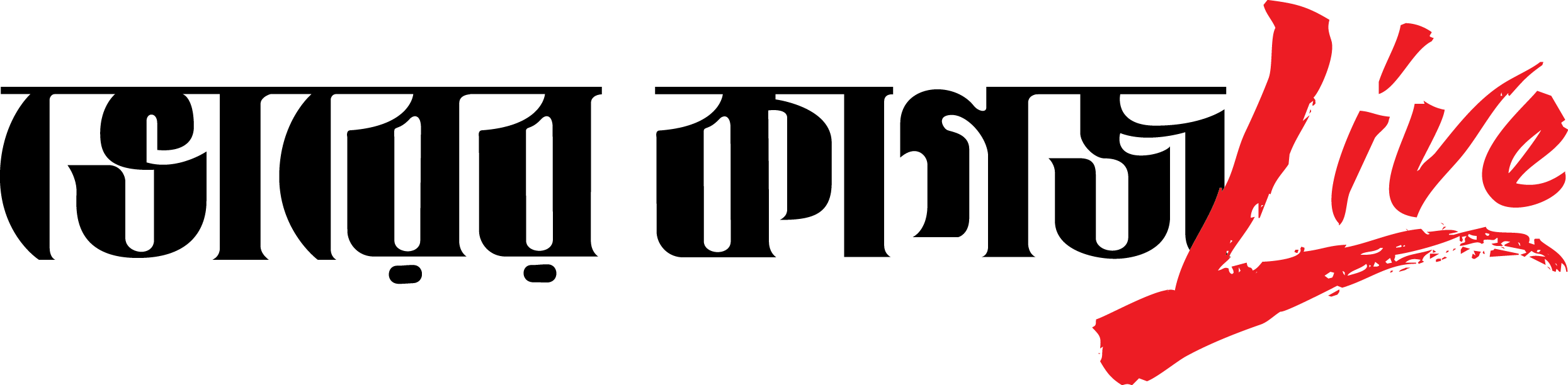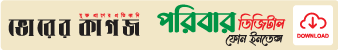কালের সাক্ষী ‘ব্রাহ্মসমাজ’ গণ্ডি ছোট ঐতিহ্য অটুট
প্রকাশ: ১৯ জানুয়ারি ২০২৫, ১২:০০ এএম
প্রিন্ট সংস্করণ

সেবিকা দেবনাথ : সময়ের পরিক্রমায় অনেক কিছুই তার জৌলুস হারায়। তাই বলে ওই জিনিসের গুরুত্ব কমে যায় তা কিন্তু নয়। বিশেষ করে ইতিহাস ঐতিহ্যকে ধারণ করা স্থাপনাগুলোর গুরুত্ব কখনোই কমে না। মাথা উঁচু করে কালের সাক্ষী হয়ে থাকে। তেমনই এক স্থাপনা ঢাকার ব্রাহ্ম সমাজ। যার অবস্থান পুরান ঢাকার ব্যস্ত এলাকা পাটুয়াটুলিতে। যানবাহন ও মানুষের চলাচল এতটাই বেশি- সেখানে দু’দণ্ড দাঁড়ানোর কোনো সুযোগই নেই। সুমনা ক্লিনিকের দিকে এগিয়ে যেতেই ডান দিকে একটি গেট চোখে পড়বে। গেটের মাথায় নীল রঙের ফলকে রুপালি রঙে বড় করে লেখা, ‘বাংলাদেশ ব্রাহ্ম সমাজ’। এর নিচে ব্র্যাকেটে লেখা নিরাকার একেশ্বরবাদী ধর্মীয় সম্প্রদায়। প্রতিষ্ঠার সাল ১৮৬৯। আরেকটু এগিয়ে গেলে দূর থেকে দেখা মিলে লাল রঙের একটি ভবন। গাছের সবুজ পাতার ফাঁক গলিয়ে উঁকি দিলেই ভবনের চূড়ায় নকশাদার ফলকে সাদা রঙে ‘ব্রাহ্ম সমাজ’ লেখাটি বেশ স্পষ্ট বোঝা যায়। ব্রিটিশ স্থাপত্যশৈলীতে নির্মিত ভবনটি প্রকৃতপক্ষে রাজা রামমোহন রায়ের প্রবর্তিত ব্রাহ্ম সমাজের সদস্যদের উপাসনার জন্য নির্মিত হয়েছিল। রথী-মাহারথী অনেকের পদধূলি পড়েছে এখানে।
ইতিহাস থেকে জানা যায়, ভারতবর্ষে রাজা রামমোহন রায় প্রবর্তিত একটি ধর্ম হচ্ছে ব্রাহ্ম। ঢাকায় ব্রাহ্ম সমাজ প্রতিষ্ঠিত হয় এই ধর্ম প্রবর্তনের প্রায় দুই যুগ পর। হিন্দু ধর্মের গোঁড়ামি ও অজ্ঞতা দূর করার জন্য রাজা রামমোহন রায় ১৮১৫ সালে ‘আত্মীয় সভা’ প্রতিষ্ঠা করেন। এ আত্মীয় সভাই ১৮২৮ সালে ব্রাহ্ম সমাজে রূপ লাভ করে। এই সমাজের সঙ্গে দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, কেশবচন্দ্র সেনসহ অনেক বিখ্যাত ব্যক্তির নাম জড়িয়ে আছে।
অধ্যাপক ড. মুনতাসীর মামুন তার ঢাকা সমগ্র বইয়ের দ্বিতীয় খণ্ডে লিখেছেন, এই মন্দির প্রতিষ্ঠায় কলেজিয়েট স্কুলের শিক্ষক দীননাথ সেন প্রধান ভূমিকা রেখেছিলেন। সেই সময় ভবনটি নির্মাণে প্রায় ১০ হাজার টাকা খরচ হয়। তখন বাংলাদেশ ব্রাহ্ম সমাজ পরিচিত ছিল ‘ঢাকা ব্রাহ্ম সমাজ’ নামে। ইতিহাসের তথ্য বলছে,
১৮৬৬ সালে দীননাথ সেন ঢাকায় ব্রাহ্মদের নিজস্ব উপাসনালয় নির্মাণের প্রস্তাব করেন। সে বছরের ২৫ আগস্ট এ বিষয়ে ৯ সদস্যের কমিটি গঠিত হয়। তখন আরমানিটোলার ব্রাহ্মসমাজ গৃহে তারা প্রার্থনার জন্য সমবেত হতেন। বাড়িটি ছিল একজন ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটের। যদিও এ নিয়ে মতান্তর আছে। ভিন্ন মতানুসারে কলতাবাজারের জমিদারেরা (বসাক পরিবার) সেই জমি ও বাড়ির মালিক ছিলেন। ১৮৬৭ সালের এপ্রিলে অভয়কুমার দত্ত মন্দিরের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন। পরের বছরের ১০ সেপ্টেম্বর জমি নিবন্ধিত হয়। মন্দিরের নকশা করেন উমাকান্ত ঘোষ। রাসমাণিক্য সেন নির্মাণকাজ পরিচালনা করেন। প্রায় ১০ হাজার টাকা ব্যয়ে ১৮৬৯ সালের ২২ আগস্ট নির্মাণকাজ শেষ হয়। ধর্ম নির্বিশেষে গণ্যমান্য ব্যক্তিদের উপস্থিতিতে সে বছরের ৫ ডিসেম্বর মন্দির উদ্বোধন করা হয়। প্রতিষ্ঠাকালীন সম্পাদকের দায়িত্বে নিয়োজিত হন দীননাথ সেন। সে সময় প্রতি রবিবার প্রায় তিন’শ সদস্য এখানে প্রার্থনার জন্য সমবেত হতেন।
তবে এখন ব্রাহ্ম সমাজের সেই রমরমা অবস্থা নেই। এর সদস্য দিনে দিনে কমছেই। নেহায়েত পালা-পার্বণে কিছুটা লোকসমাগম হয়। প্রতি রবিবার সাপ্তাহিক যে প্রার্থনা অনুষ্ঠিত হয় সেখানেও হাতে গোনা দু-চার জনকে পাওয়া যায়। নতুন করে আর কেউ এই সমাজের সদস্য হচ্ছেন না। প্রচারণার কাজও এখন বন্ধ। টাঙ্গাইল, নারায়ণগঞ্জ, রংপুর, সিলেট, ময়মনসিংহসহ দেশের বিভিন্ন এলাকায় ৯০টির মতো ব্রাহ্ম সমাজ ছিল। কালের বিবর্তনে সে সংখ্যা এখন এসে দাঁড়িয়েছে ৭ থেকে ৮টিতে। বর্তমানে আমাদের দেশে একশ জনেরও কম ব্রাহ্ম আছেন। জন্মসূত্রে ব্রাহ্ম ১৫ জনের মতো হবেন। গন্ডি ছোট হয়ে এলেও নিজেদের ঐতিহ্য এখনো বজায় রেখেছেন এই সমাজের সদস্যরা।
ঢাকায় ব্রাহ্ম সমাজের সাধারণ সম্পাদক রনবীর পাল ভোরের কাগজকে বলেন, বিংশ শতকের মাঝামাঝি থেকে এই সমাজের অনুসারী কমতে থাকে। ব্রাহ্মদের মধ্যে দুটি ভাগ আছে। জন্মসূত্রে ব্রাহ্ম ও অনানুষ্ঠানিক ব্রাহ্ম। যারা এই মত সমর্থন করেন, কিন্তু আনুষ্ঠানিকভাবে গ্রহণ করেননি তারা অনানুষ্ঠানিক ব্রাহ্ম। তবে তারাও সমাজের সদস্য হতে পারেন। আমাদের ৭ সদস্যের কার্যনির্বাহী কমিটি আছে। ট্রাস্টি বোর্ডও আছে ৭ সদস্যের। মন্দিরের রক্ষণাবেক্ষণ সংক্রান্ত যাবতীয় কার্য তারা করে থাকেন।
ব্রাহ্ম সমাজের কার্যক্রম সম্পর্কে জানতে চাইলে রনবীর পাল বলেন, ব্রাহ্ম সমাজের উদ্যোগে এক সময় সামাজিক সংস্কারমূলক প্রচুর কাজ হয়েছে। তবে এখন কাজ হচ্ছে স্বল্পপরিসরে। শীতকালে বস্ত্র বিতরণ, অসুস্থদের জন্য চিকিৎসার ব্যবস্থা- প্রভৃতি কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়। এছাড়াও বছরে ছয় থেকে সাতটি উৎসব আয়োজিত হয়ে থাকে মন্দিরটিতে। বিশেষ করে জানুয়ারি, মে, জুন ও সেপ্টেম্বর মাসে। পয়লা বৈশাখ রাজা রামমোহন রায়ের জন্ম ও মৃত্যুবার্ষিকীও পালন করেন ব্রাহ্মরা। ব্রাহ্ম সমাজের মন্দিরে রয়েছে জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সব মানুষের প্রবেশাধিকার। এই মন্দিরে পদধূলি পড়েছে অনেক রথী-মহারথীদের। ১৯২৬ সালে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এখানে এসেছিলেন। প্রার্থনাও করেছিলেন। দীননাথ সেনের নাতবৌ সুচিত্রা সেনও স্বামী দিবানাথ সেনের সঙ্গে এখানে একবার এসেছিলেন।
ব্রাহ্ম সমাজের মূল গেট দিয়ে ঢুকে গেলে হাতের বামে লোহার বেষ্টনী দিয়ে ঘেরাও করা বাগান। সেখানে বাহারি ধরনের গাছ। হাতের ডানে পুরনো জীর্ণ ভবন। সেটি এই প্রতিষ্ঠানের অফিস হিসেবে ব্যবহৃত হয়। এগিয়ে যেতে থাকলে দোতলা একটি ভবন, যার নিচতলা একটি আধাপাকা ঘর যেখানে বিবাহ নিবন্ধন করা হয়। এই ভবনটিতে এক সময় ছিল রাজা রামমোহনের লাইব্রেরি। ভবনটি ঝুঁকিপূর্ণ হওয়ায় বর্তমানে লাইব্রেরিটি মূল ভবনে সরিয়ে নেয়া হয়েছে। মূল ভবনের পেছন দিক দিয়ে লাইব্রেরিতে যেতে হয়। দরজায় পড়ে থাকা ধুলার আস্তর দেখে স্পষ্টই বোঝা যায়- এখানে লোকজনের যাতায়াত নেই বললেই চলে। ১৮৭১ সালে প্রতিষ্ঠিত এ লাইব্রেরিতে অনেক দুষ্প্রাপ্য বই ও পুঁথির এক বিশাল সংগ্রহ ছিল। কিন্তু ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধের সময় পাকিস্তানি সৈন্যরা লাইব্রেরিটি ধ্বংস করে দেয়। সেই সময়ই এর মূল সংগ্রহ নষ্ট হয়ে গেছে।
মূল ভবনের পূর্ব-পশ্চিমে আয়তাকার, চার ফুট উঁচু মঞ্চের ওপর নির্মিত; পাঁচটি সিঁড়ি বেয়ে প্রবেশ করতে হয় মন্দিরে। মন্দিরের চারপাশে প্রশস্ত বারান্দা। তার ঠিক মাঝখানে বিশাল এক হলঘর। চারপাশের বারান্দা থেকে হলঘরে প্রবেশের জন্য আছে নির্দিষ্ট দূরত্বে ১৬টি পথ। এই হলঘরে পূজা হয় না। হলঘরের উত্তর অংশের ঠিক মাঝখানে উঁচু বেদিতে বসে সম্পাদক ব্রাহ্ম মতবাদের কথা বলেন। বেদির সামনে বসে শিল্পীরা ব্রাহ্মমতের বিভিন্ন গান গেয়ে থাকেন। চারপাশের বেঞ্চে বসে শ্রোতারা তা শুনতে পারেন। মন্দিরের আচার্যের দায়িত্বে যিনি আছেন তিনি প্রার্থনাসভা পরিচালনা করেন। তার অনুপস্থিতিতে রনবীর পালও এই কাজ করেন বলে জানান। বেদিতে বসেই ঈশ্বরের আরাধনা চলে। বৈদিক মন্ত্র পাঠের পাশাপাশি চলে রবীন্দ্র নাথঠাকুর, দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর, কাঙালিচরণ সেনের লেখা গান। সেই তালিকায় আছে- ‘অরূপ তোমার বাণী’; ‘তোমারি নামে নয়ন মেলিনু পুণ্যপ্রভাতে আজি’; ‘আমার হিয়ার মাঝে লুকিয়ে ছিলে’; ‘সকাতরে ওই কাঁদিছে’; ‘আনন্দলোকে মঙ্গলালোকে’; ‘শ্রান্ত কেন ওহে পান্থ’ এমন অসংখ্য গান। সেই সংগীতের মাঝে ডুবে গিয়ে ভক্ত ও দর্শনার্থীরা জীবনের সব অশান্তি, কোলাহল ভুলে খুঁজে পান পরমানন্দ।