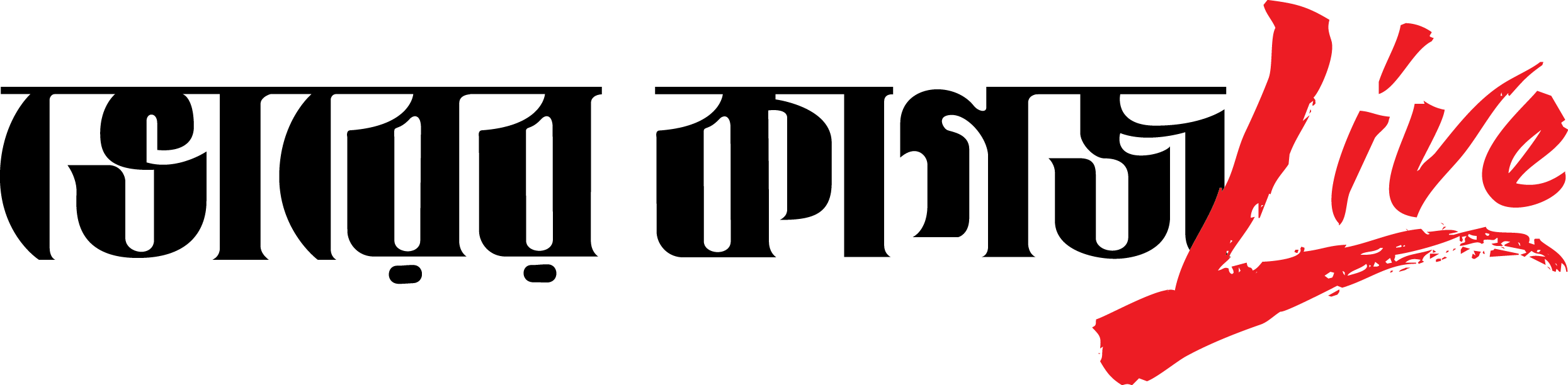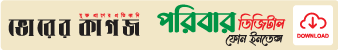মুক্তিযুদ্ধে ১০ বিদেশি সাংবাদিকের অবদান
প্রকাশ: ১৬ ডিসেম্বর ২০২৪, ১২:০০ এএম
প্রিন্ট সংস্করণ
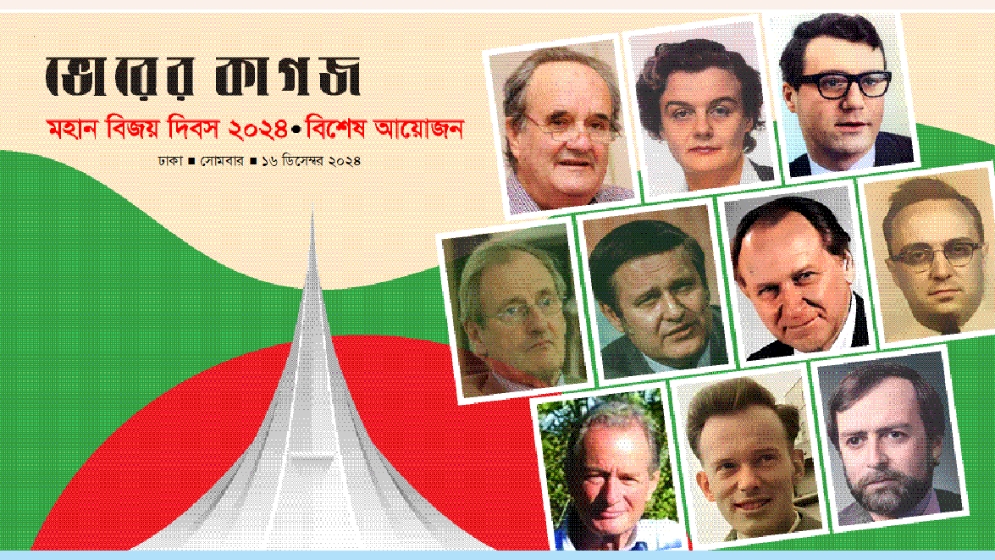
মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে সকালে-সন্ধ্যায় বিবিসির মার্ক টালি কী বলছেন, তা শোনার জন্য উৎকণ্ঠিত হয়ে থাকত সাড়ে সাত কোটি মানুষ। যারা বাংলাদেশের পাশে দাঁড়িয়েছেন, উৎকণ্ঠা তাদের; যারা স্বাধীনতার বিরোধিতা করেছেন, উৎকণ্ঠা তাদেরও কম নয়- আসলে পূর্ব পাকিস্তানে কী ঘটছে, সত্যিকারের খবরটি দিতে পারবেন মার্ক টালি। শুধু কি মার্ক টালি? জীবনের ঝুঁকি নিয়ে নেমেছেন সিডনি শনবার্গ, মিশেল লরেন্ট, অ্যান্থনি ম্যসকারেনহাস, ড্যান কোগিন, সাইমন ড্রিং, নিকোলাস টোমালিন, ক্লেয়ার হোলিংওয়ার্থ, মার্টিন ওলাকট, জন পিলজার, ডেভিড লোশাক, পিটার হ্যাজেলহার্স্ট, অ্যান্থনি লুইস ও আরো অনেকে। এ দেশে মার্চের শুরু থেকেই বিদেশি সংবাদমাধ্যমের প্রতিনিধিদের আগমন ঘটছিল। ২৫ মার্চ রাতে পাকিস্তানি সামরিক বাহিনী যখন হত্যাযজ্ঞে মেতে উঠল, তার সাক্ষী হয়ে রইলেন কজন বিদেশি সাংবাদিক। ৩৫ জন বিদেশি গণমাধ্যম প্রতিনিধিকে ৪৮ ঘণ্টারও বেশি সময়ের জন্য আটকে রাখা হয় ঢাকার হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টালে। ২৭ মার্চ বলপ্রয়োগ করে পূর্ব পাকিস্তান থেকে তাদের বহিষ্কার করা হয়। বহিষ্কারের প্রক্রিয়ায় করাচির উদ্দেশে বিদেশি সাংবাদিকদের উড়োজাহাজে তোলার আগে সাংবাদিকদের তল্লাশি করা হয়। তাদের নোটবই, ছবির ফিল্ম ও ফাইল বাজেয়াপ্ত করা হয়। বহিষ্কৃত সাংবাদিকরা যুক্তরাষ্ট্র, অস্ট্রেলিয়া, যুক্তরাজ্য, কানাডা, ফ্রান্স, জাপান ও রাশিয়ার সংবাদপত্রসহ অন্যান্য গণমাধ্যমে কর্মরত ছিলেন। বৈশ্বিক রাজনীতিতে রাষ্ট্র ও সরকার যে অবস্থানই গ্রহণ করুক না কেন মুক্ত সাংবাদিকতা জনগণকে সঠিক খবরটিই দিয়েছে। পাকিস্তানের মিত্র হিসেবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও চীন সরকার পূর্ব পাকিস্তানে নারকীয় সামরিক হস্তক্ষেপকেও পাকিস্তানের অভ্যন্তরীণ বিষয় হিসেবে এড়িয়ে যেতে চেয়েছে। কিন্তু সব মার্কিন পত্রিকা পাকিস্তানের বর্বরোচিত কর্মকাণ্ডের নিন্দা করেছে, পাকিস্তানকে অস্ত্র সরবরাহ থেকে বিরত রাখার জন্য যুক্তরাষ্ট্র সরকারের ওপর ক্রমাগত চাপ প্রয়োগ করেছে। মহান মুক্তিযুদ্ধে ১০ বিদেশি সাংবাদিকের অবদান নিয়ে
বিশেষ আয়োজনের গবেষাণামূলক প্রতিবেদনটি লিখেছেন কথাসাহিত্যিক ও কলাম লেখক আন্দালিব রাশদী সম্পাদনায় সালেক নাছির উদ্দিন
মার্ক টালি বিবিসি
১৯৭১ সালে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের দিনগুলোতে আমাদের পাশে পৃথিবীর বিভিন্ন অংশের বহু বিদেশি সত্যিকার বন্ধুর মতো দাঁড়িয়ে গেছেন। আমাদের দুঃখ-বেদনার ভাগ নিয়েছেন, বাংলাদেশের মানুষের মতো তারাও স্বাধীন বাংলাদেশের স্বপ্ন দেখেছেন। একাত্তরের এমন একজন বন্ধুর নাম মার্ক টালি।
মাতৃভাষা অবশ্যই মায়ের ভাষা, মাতৃস্তন্য অবশ্যই মায়ের দুধ, মাতৃস্নেহ অবশ্যই মায়ের স্নেহ। মাতৃভূমি কি মায়ের জন্মভূমি নয়? অবশ্যই। এই সত্যটি যদি আমরা স্বীকার করে নিই তাহলে মার্ক টালির মাতৃভূমি অবশ্যই বাংলাদেশ।
মার্ক টালির মা বাংলাদেশেই জন্মগ্রহণ করেন। ১৮৫৭-র সিপাহি বিদ্রোহের আগেই ভারতবর্ষে আসেন মার্ক টালির নানার দাদা।
তিনি আফিম ব্যবসায়ের সঙ্গে জড়িত ছিলেন। উত্তর প্রদেশের পূর্বাঞ্চলে আফিম এজেন্ট ছিলেন। সিপাহি বিদ্রোহের ভয়াল যখন ইংরেজ মাত্রই সিপাহি এবং ভারতীয় বিপ্লবীদের টার্গেট এমন ভয়ংকর সময়ে তিনি নৌকায় চড়ে নিরাপদ বিবেচনা করে কলকাতা চলে আসেন। নানার বাবা ছিলেন ব্যবসায়ী। আর মার্ক টালির নানার ছিল পাটের কারবার। সুতরাং সে কালের সোনালি আঁশ অঞ্চলই তাকে বেছে নিতে হয়েছে। সেজন্য পূর্ব বাংলাই ছিল উত্তম। এখানেই তার মায়ের জন্ম।
মার্ক টালির বাবার সঙ্গে তার মায়ের প্রথম দেখা কলকাতাতেই, তার বাবাও ব্যবসায়ী ছিলেন। ১৯৩৫ সালে টালিগঞ্জে মার্ক টালির জন্ম। ছয় সন্তানের একজন হিসেবে তিনি বেড়ে উঠেন, কলকাতায় হলেও তার শৈশব ছিল ‘ভেরি ব্রিটিশ চাইল্ডহুড’। একেবারে ছোটবেলা থেকেই তিনি যে ইন্ডিয়ান নন বরং ব্রিটিশ এই শিক্ষাই পরিবার থেকে পেয়েছেন এবং এ কথা তাকে বারবার স্মরণ করিয়ে দেয়া হয়েছে।
সপ্তাহের সাত দিন পুরো ২৪ ঘণ্টাই ব্রিটিশ ন্যানির নিয়ন্ত্রণ ও তত্ত্বাবধানে থাকতে হতো। ভারতীয় ড্রাইভারের কাছ থেকে শোনা শব্দ উচ্চারণ করার কারণে ন্যানি তার মাথায় চাটিও মেরেছে। যে সব ইংরেজ শিশুদের বাবা-মার খাস ব্রিটিশ ন্যানির ভরণ-পোষণের সামর্থ্য ছিল না, তাদের সন্তানের জন্য ভারতীয় কিংবা অ্যাংলো ইন্ডিয়ান ন্যানি রাখতে হতো।
কিন্তু মার্ক টালির এই বিলেতি ন্যানির শাসন এতটাই কড়া ছিল যে তাকে এবং তার পরিবোরের শিশুদের এ ধরনের ন্যানি-লালিত শিশুদের সঙ্গে মিশতে দিতেন না।
ভারতীয় জাত-পাত ও বৈষম্যের সঙ্গে আর একটি ভিন্ন রূপ এর সঙ্গে যোগ হয়েছিল কলকাতায়। ইন্ডিয়ান সিভিল সার্ভিসের (আইসিএস) সদস্যদের মনে করা হতো ব্রাহ্মণ, ভারতীয় সেনা সদস্যদের মনে করা হতো রাজপুত (যোদ্ধা শ্রেণি) আর আমার ব্যবসায়ী বাবা তাদের কাছে ছিলেন বৈশ্য। নাক উঁচু আইসিএস আর সামরিক বাহিনীর কাছে তিনি ছিলেন কেবল একজন বোচাওয়ালা ব্যাপারি।
‘আমার বন্ধুরা প্রায় সবাই ভারতীয়। আমার কন্যার জামাতা এবং পুত্রবধূ উভয়েই ভারতীয়। আমি ভারতীয় একটি ভাষা জানি। আমি আরো ভালো জানতে পারতাম যদি ভারতীয়রা আমার সঙ্গে সাক্ষাতের সময় হিন্দিতে কথা বলতেন।’ পাছে তিনি না বোঝেন এজন্য তারা ইংরেজি বলেন, এতে চর্চা হয়ে উঠে না। গোড়াতেই ইউরোপিয়ান ন্যানির কঠোর প্রহরা ছিল যেন তিনি হিন্দি শব্দ মুখে তুলে না নেন। একমাত্র ইংরেজিই ছিল তার কাছে গ্রহণযোগ্য ভাষা।
ভারতে আসা ব্রিটিশদের তখনকার বিধান ছিল ছেলেমেয়ে স্কুলে পড়ার বয়সে পৌঁছলে তাদের ইংল্যান্ড পাঠিয়ে দিতে হবে। কিন্তু তখন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ চলছে, লন্ডনে বোমা পড়ছে। প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষাগ্রহণের জন্য মার্ক টালিকে দার্জিলিং পাঠানো হলো। ‘সেগুলো ছিল আমার জন্য বিস্ময়কর আনন্দের দিন। জায়গাটা আমার খুব পছন্দ হয়ে যায়, প্রকৃতির খুব কাছাকাছি। সার্বক্ষণিক চোখে চোখে কেউ রাখত না। হেডমাস্টার ছিলেন খুব উদার। স্বাধীনভাবে বাজারে ঘুরে বেড়াতাম।’
এ সময় তার বাবার ম্যানচেষ্টারে চাকরি হয়ে যাওয়াতে তাকে শৈশবের বাকি অংশটুকু কাটাতে হয় ব্রিটেনেই, বোডিং স্কুলে। ভারত তখন রয়ে যায় দৃষ্টিসীমার বাইরে। তাছাড়া ভারতের পাট তো চুকিয়েই চলে এসেছেন। সেই ভারত তার আর কখনো ফেরার কোনো কারণ ছিল না।
১০ বছর বয়সে ব্রিটেনে ফিরে যান, মার্লবরো কলেজ, ক্যামব্রিজের ট্রিনিটি কলেজে পড়াশোনা করেন। তিনি আন্তরিকভাবেই সিদ্ধান্ত নিলেন ধর্মযাজক হবেন। সে উদ্দেশ্য মাথায় নিয়ে ক্যামব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে ধর্মতত্ত্ব ও ইতিহাস নিয়ে পড়াশোনা শুরু করলেন। কিন্তু আর্কবিশপ সন্দিহান হলেন এই যুবক কৌমার্য ধারণ করে যাজক হতে পারবে না।
তিনি তাকে প্রত্যাখ্যান করলেন। মার্ক টালি একটু আহত হলেও ভাবলেন তার কারণে চার্চের ভাবমূর্তি তো নষ্ট হতে দেয়া যায় না। পরবর্তীকালে তিনি স্বীকার করেছেন আর্কবিশপের সিদ্ধান্তই সঠিক ছিল।
তিনি চার বছর একটি বেসরকারি সংস্থায় কাজ করে বিবিসিতে যোগ দিলেন- কিন্তু মোটেও সংবাদিক হিসেবে নয় প্রশাসন শাখাতে পার্সোনেল ম্যানেজার হিসেবে। তিনি সাংবাদিক হবেন, এ চিন্তা কখনো তার মনে আসেনি।
পরের বছর ১৯৬৫ সালে তিনি আকস্মিকভাবে বিবিসি দিল্লি ব্যুরোতে কনিষ্ঠ প্রশাসনিক সহকারীর পদে বদলি হলেন। তিনি তার স্মৃতিময় জন্মস্থানে ফিরে এলেন যদিও জন্মস্থান সম্পর্কে এক বৈরী মন আগেই তৈরি করে দেয়া হয়েছিল। কিন্তু তা স্থায়ী হয়নি।
মার্ক টালি মনে করলেন ভারতে ফিরে আসাটাই নিয়তি ‘আমার ভারতে ফেরার কথা ছিল, তা ঘটে গেছে। পরের বছর সদর দফতর থেকে পদোন্নতি দিয়ে তাকে বিবিসির নিউজ করেসপন্ডেন্ট করা হলো। দিল্লিতে তার অফিস; কিন্তু তাকে কাভার করতে হবে গোটা দক্ষিণ এশিয়া- ভারত, পাকিস্তান, শ্রীলঙ্কা নেপাল। তখন বাংলাদেশ তো পাকিস্তানেরই অংশ। ঢাকা থেকে পাঠানো একটি প্রতিবেদন, দিল্লি ও লন্ডনে ধারণকৃত ও সম্প্রচারিক ভাষ্য এবং পর্যালোচনার অনুবাদ উপস্থাপন করা হলো :

বিবিসি লন্ডন
ঢাকা থেকে মার্ক টালি
১ জুলাই ১৯৭১
ঢাকা ও ঢাকার আশপাশে বিভিন্ন এলাকায় ব্যবসায়ী, সাংবাদিক এবং সাধারণ মানুষের সঙ্গে আলোচনার পর এটা আমার কাছে আরো স্পষ্ট হয়ে উঠেছে যে, প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খানের সর্বশেষ রাজনৈতিক কর্মসূচি পূর্ব পাকিস্তানের জন্য আরো হতাশাব্যঞ্জক। যেসব মন্তব্য আমি মানুষের কাছে শুনেছি, তার সারকথা হচ্ছে- প্রেসিডেন্টের ভাষণে পূর্ব পাকিস্তানের জন্য কিছুই নেই। অনেকেই মনে করেন পশ্চিম পাকিস্তানের জনগণ এবং সশস্ত্র বাহিনীকে উৎসাহ জোগানোর জন্যই প্রেসিডেন্টের ভাষণটি তৈরি করা হয়েছে। যারা সত্যিই সমস্যার একটি সমাধান খুঁজছিলেন- প্রেসিডেন্টের ভাষণে আওয়ামী লীগ নেতৃত্বের প্রতি নিন্দাসূচক বক্তব্য তাদের হতাশ করেছে।
সশস্ত্র বাহিনীর জন্য তার ভূয়সী প্রশংসাকেও ভীষণ সন্দেহের চোখে দেখা হচ্ছে। প্রেসিডেন্টের ভাষণে ইসলাম ধর্মের ওপর জোরালো বক্তব্য সময়োচিত হয়নি। যেসব হিন্দু এখনো এখানে আছে তা তাদের ভয় বাড়িয়ে দেবে এবং তা নিশ্চয়ই শরণার্থীদের দেশে ফিরে আসতে উৎসাহ দেবে না। প্রকৃত সত্য হচ্ছে, যুক্তিসঙ্গত কারণেই বাঙালিরা সেনাবাহিনীকে বিশ্বাস করে না।
ঢাকা থেকে ৫০ মাইল উত্তর-পশ্চিমে আটটি গ্রাম ধ্বংস করে পাকিস্তানি সেনাবাহিনী সন্দেহাতীতভাবে আবার প্রমাণ করেছে প্রতিহিংসায় শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ তারা বন্ধ করেনি।
সেনা-নির্যাতনের যে গুজব ঢাকা ও চারপাশে ছড়িয়ে পড়েছে তাতে সেনাবাহিনী নির্মমভাবে মানুষকে ক্যান্টনমেন্টে ধরে আনছে, তারা আর ফেরত যাচ্ছে না, ধর্ষণ সমানে চলছে, বলপূর্বক অর্থ আদায় ও মূল্যবান দ্রব্যসামগ্রী ছিনিয়ে নেয়া অব্যাহত রেখেছে- এসব সেনা-আচরণ সবসময় হাতেনাতে প্রমাণ করা না গেলেও সারাবিশ্বই তাদের এসব অপকর্ম সম্পর্কে অবহিত। এ ধরনের পরিস্থিতিতে সেনাবাহিনীর পক্ষে জনগণের আস্থা ফিরে পাওয়া অসম্ভব। তাছাড়া আস্থা ফিরে পেতে তাদের কোনো পদক্ষেপ গ্রহণ করতেও দেখা যাচ্ছে না। রাস্তায় ভীতসন্ত্রস্ত সশস্ত্র পাঞ্জাবি পুলিশের টহল, মাঝে মধ্যে সেনাবাহিনীকে দেখা যায় মেশিনগান উঁচিয়ে টহল দিচ্ছে। টেলিগ্রাফ অফিসে ঢোকার সময় লোকজনকে তল্লাশি করা হচ্ছে, রাস্তাঘাটেও তল্লাশি চলছে।
আমি যাদের সঙ্গে কথা বলেছি, তারা সন্ত্রস্ত হয়ে পড়েছে পাছে সেনাবাহিনীর চোখে পড়ে যায়। বাজারে তুলনামূলকভাবে অল্পকিছু চাঞ্চল্য রয়েছে, বাজারে লোকের সংখ্যা আগের চেয়েও অনেক কম আর রাত্রিকালীন রাস্তাঘাট জনশূন্যই থাকছে। অফিসে হাজিরা কিছুটা বেড়েছে, তবে দেখা যাবে হিন্দু কর্মচারীদের কেউই অফিসে ফেরেনি। আসলে সেনাবাহিনী যে ক্ষতিসাধন করেছে তা পূরণের কোনো পদক্ষেপই নেয়া হয়নি। উর্দুভাষী ও বাঙালিদের মধ্যে সাম্প্রদায়িক বিরোধ অত্যন্ত তীব্র। এ অবস্থায় মূলত পশ্চিম পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর সঙ্গে কোনো না কোনোভাবে সম্পর্কিত একটি সরকার যে জনগণের আস্থা ফিরে পাবে তা একেবারেই অসম্ভব।
একাত্তরের বিবিসি লন্ডন
একাত্তরের সবচেয়ে বিশ্বাসযোগ্য ও নির্ভরযোগ্য গণমাধ্যম ছিল বিবিসি- ব্রিটিশ ব্রডকাস্টিং করপোরেশন। এদেশের মানুষের সঙ্গে বিবিসি বাংলা বিভাগের একটি আবেগময় সম্পৃক্ততা থাকার কথাই। একাত্তরের ‘বিবিসির মার্চ ও ডিসেম্বরের কয়েক দিনের কয়েকটি সংবাদ তুলে থরছি।
২৬ মার্চ ১৯৭১
পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান পূর্ব পাকিস্তানে তার সরকারের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ গ্রহণ করায় সেখানে ব্যাপক লড়াই শুরু হয়েছে বলে পূর্ব পাকিস্তান থেকে খবর পাওয়া গেছে। অন্যদিকে ভারত থেকে পাওয়া খবরে জানা গেছে, শেখ মুজিবুর রহমান প্রদেশটির স্বাধীনতা ঘোষণা করেছেন। পূর্বাঞ্চলের রাজধানী ঢাকায় অবস্থানরত মার্কিন কনসাল জেনারেল জানিয়েছেন, বিরোধীদের দমন করতে সেখানে কামানও ব্যবহার করা হচ্ছে। ভারত থেকে পাওয়া আগের আরেকটি প্রতিবেদনে বলা হয়েছে- সর্বত্র তীব্র লড়াই চলার খবর পূর্ব পাকিস্তানের একটি গোপন বেতার কেন্দ্র থেকে সম্প্রচার করা হয়েছে।
পূর্ববাংলার সেনা ইউনিটগুলো, এর মধ্যেই পুলিশ সশস্ত্র বেসামরিক নাগরিকদের সঙ্গে যোগ দিয়ে পশ্চিম পাকিস্তানি সেনা ইউনিটগুলোর বিরুদ্ধে লড়াই করে যাচ্ছে। পূর্ব পাকিস্তান থেকে সরাসরি কোনো সংবাদ পাওয়া যাচ্ছে না। প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান কঠোর ভাষায় শেখ মুজিবুর রহমানকে রাষ্ট্রদ্রোহের অভিযোগে অভিযুক্ত করেছেন এবং সংখ্যাগরিষ্ঠের দল আওয়ামী লীগকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছেন। তিনি তার নিজস্ব কর্মসূচি ঘোষণা করেছেন। কার্যত আওয়ামী লীগই পূর্ব পাকিস্তানের নিয়ন্ত্রণ হাতে নিয়েছিল।
১৫ ডিসেম্বর ১৯৭১
ভারতীয়রা বলছে, তারা পূর্ব পাকিস্তানের রাজধানী ঢাকায় ভারী অস্ত্রের গোলাবর্ষণ করে যাচ্ছে এবং ভারতীয় বাহিনী ও বাংলাদেশের গেরিলারা বহিঃপ্রতিরক্ষায় আক্রমণ করে তাদের মনোবল ভেঙে দিচ্ছে। সংবাদদাতাদের পাঠানো একটি সম্মিলিত বার্তায় জানা যাচ্ছে, রেডক্রস ও পাকিস্তানি কমান্ডার-ইন-চিফ জেনারেল নিয়াজির মধ্যে অস্ত্রবিরতি নিয়ে দরকষাকষি চলছে, তবে এখনো তা থেকে সুনির্দিষ্ট কিছু উঠে আসেনি।
বার্তায় বলা হয়েছে, ঢাকা ও ঢাকার আশপাশে বিমান আক্রমণ তীব্রতর করা হয়েছে, বিশেষ করে জেনারেল নিয়াজির সদর দপ্তর ও সামরিক লক্ষ্যবস্তুগুলো এই আক্রমণের প্রধান টার্গেট।
১৬ ডিসেম্বর ১৯৭১
পূর্ব পাকিস্তানে যুদ্ধ শেষ হয়ে আসছে। রেডিও পাকিস্তান জানিয়েছে, যুদ্ধবিরতি হয়েছে এবং ভারতীয় বাহিনী রাজধানী ঢাকায় প্রবেশ করেছে। পাকিস্তান বলেছে, স্থানীয় ভারতীয় ও পাকিস্তানি কমান্ডারদের মধ্যে চুক্তির মাধ্যমে যুদ্ধবিরতি করা হয়েছে। ভারতের প্রধানমন্ত্রী মিসেস গান্ধী সংসদে বলেছেন, দুই পক্ষের প্রতিনিধি ঢাকায় আত্মসমর্পণ চুক্তিতে স্বাক্ষর করেছেন।
পাকিস্তানের পক্ষে এই চুক্তি নিঃশর্ত আত্মসমর্পণ। তিনি বলেন, ভারত আশা করে, পূর্ব পাকিস্তানিদের নেতা শেখ মুজিবুর রহমান, যিনি পাকিস্তানে আটক রয়েছেন, নিজ দেশের মানুষের মধ্যে তার আসন গ্রহণ করবেন এবং বাংলাদেশকে শান্তির পথে এগিয়ে নিয়ে যাবেন।
মিসেস গান্ধী বলেন, ভারতীয় বাহিনী প্রয়োজনের অতিরিক্ত সময় সেখানে অবস্থান করবে না। তিনি আরো যোগ করেন, লাখ লাখ শরণার্থী ইতোমধ্যেই দেশের পথে পা বাড়িয়েছে।
ক্লেয়ার হোলিংওয়ার্থ
ডেইলি টেলিগ্রাফ

১৯১১ : জন্ম ১০ অক্টোবর, ইংল্যান্ডের লিস্টারের দক্ষিণ নাইটন
১৯৭১ : বাংলাদেশের অভ্যন্তরে ও রণাঙ্গনে ডেইলি টেলিগ্রাফ প্রতিনিধি
১৯৮২ : অর্ডার অব ব্রিটিশ এম্পায়ার খেতাব অর্জন
১৯৮৯ : তিয়ান আনমেন স্কোয়ার অভুত্থানের সময় ঘটনাস্থলে উপস্থিতি
১৯৯০ : আত্মজীবনী ফ্রন্টলাইন প্রকাশিত
২০১৭ : ১০ জানুয়ারি ১০৫ বছর বয়সে হংকং-এর রতনজি হাসপাতালে মৃত্যুবরণ
একাত্তরের দুঃসহ সংকটের দিনগুলোতে বাংলাদেশের মানুষের পাশে দাঁড়িয়েছিলেন ডেইলি টেলিগ্রাফ-এর ক্লেয়ার হোলিংওয়ার্থ।
ক্লেয়ার হোলিংওয়ার্থের একটি প্রতিবেদনই বলে দেবে তিনি কেমন করে সত্যের চিত্র তুলে ধরেছেন :
পূর্ববাংলায় সেনাবাহিনী ত্রাসের রাজত্ব চালাচ্ছে
ঢাকা থেকে পাঠানো ক্লেয়ার হোলিংওয়ার্থের প্রতিবেদনটি ২৯ জুন ১৯৭১ দ্য ডেইলি টেলিগ্রাফ-এ প্রকাশিত হয় :
ব্রিটিশ সংসদীয় প্রতিনিধি দল পূর্ববাংলা ঘুরে গতকাল কলকাতার উদ্দেশে ঢাকা ত্যাগ করেছে। দলনেতা মিডলসবারা পূর্ব থেকে নির্বাচিত শ্রমিক দলীয় এমপি আর্থার বটমলেকে হতাশ ও বিষণ্ন দেখাচ্ছিল। তার ঢাকা থেকে ১৫ মাইল উত্তরে বলিয়াদি যাওয়ার উদ্যোগ কয়েক ঘণ্টা অপেক্ষার পর ব্যর্থ হয়ে যায়। রবিবার ভোরে পাকিস্তান সেনাবাহিনী এলাকাটি ধ্বংস করে ফেলেছে।
ছোট শিল্পশহর টঙ্গী থেকে উত্তরে এই এলাকার ছয়টি গ্রাম কেন জ^ালিয়ে দেয়া হলো, কেন গুলি চালানো হলো এখনো তার কোনো ব্যাখ্যা দেয়া হয়নি। টুইকেনহাম থেকে নির্বাচিত রক্ষণশীল দলের এমপি টবি জেসেল ব্রিটিশ সংবাদমাধ্যমের কাছে মন্তব্য করেছেন, ‘এখানে যে সন্ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করা হয়েছে তা দেশের মানুষের অর্থনৈতিক জীবন পূর্বাবস্থায় ফিরিয়ে আনতে সহায়ক হবে না।’
গত চার দিনের প্রকৃত ঘটনা উদঘাটনে মিশনের অভিজ্ঞতার আলোকে তিনি বলেন, স্থানীয় মানুষদের নিরুদ্দিষ্ট হওয়া এবং গ্রাম তছনছ করে ফেলা বরং পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর প্রতি আতঙ্কই বাড়িয়ে দেবে।
তিনি বলেন, ‘জেনারেলদের খামখেয়ালিপূর্ণ ট্রিগার-হ্যাপি আচরণ এবং বিভিন্ন ইউনিটের স্বৈরাচারী কার্যক্রম অবশ্যই বন্ধ করতে হবে।’ তিনি আরো বলেন, ‘আমি বুকে হাত রেখে কাউকে বিশেষ করে তারা যদি হিন্দু হন কিংবা আওয়ামী লীগের সঙ্গে কোনোভাবে সম্পর্কিত হন, বলতে পাবর না- আপনারা পাকিস্তানে ফিরে যান।’
‘এখন পাকিস্তান সেনাবাহিনীর যে মানসিক প্রস্তুতি- ভারত থেকে যে কারো পাকিস্তানে ফিরে যাওয়া নিরাপদ হবে কিনা আমি সন্ধিহান।’
টবি জেসেল বলেন, জনগণের আস্থা ফিরিয়ে আনতে একটি পদক্ষেপ সামরিক গভর্নরের পদ থেকে জেনারেল টিক্কাকে সরিয়ে বাঙালিদের হৃদয় ও মন জয় করতে সক্ষম এমন কোনো সেনাকর্মকর্তাকে নিয়োগ দেয়া প্রয়োজন।
দুর্বিনীত রণাঙ্গন প্রতিনিধি
ক্লেয়ার হোলিংওয়ার্থের জন্ম ১০ অক্টোবর ১৯১১। ইংল্যান্ডের ডিস্টারের দক্ষিণ নাইটন নামের আধা-শহরে। তার বয়স যখন তিন বছর ১৯১৪ সালে প্রথম মহাযুদ্ধ শুরু হয়। ক্লেয়ারকে চলে যেতে হয় বাবার জুতো ও বুটের ফ্যাক্টরিতে। যুদ্ধ যে ইতিহাস ও জীবনের অংশ- শৈশব থেকেই ক্লেয়ারকে তা উপলব্ধি করতে হচ্ছে:
আমরা যে খামারবাড়ীতে থাকতাম, মনে আছে সেখানে আমাদের মাথার ওপর জার্মান বোমারু বিমান উড়ে গেছে এবং লাফবারাতে বোমা ফেলেছে। পরদিন সকালে আমার টাট্টুঘোড়া নিয়ে বোমার ক্ষয়ক্ষতি দেখতে চলে গেলাম। সেখানে এত কম ক্ষতি হয়েছে দেখে অবাক হয়ে গেলাম।
তার বাবা যদিও সৈনিক ছিলেন না, স্কুলে-পড়া মেয়েটিকে যুদ্ধক্ষেত্র দেখাতে নিয়ে গেছেন- নেসবি, বসওয়ার্থ, ক্রেসি, পয়টার্স ও এজিনকোর্ট। বাবার পীড়াপীড়িতে লেস্টার কলেজে গার্হস্থ্য বিজ্ঞান পড়লেন এবং অচিরেই গার্হস্থ্য সব বিষয়ে উৎসাহ হারালেন। এক যুবকের সঙ্গে প্রেম হলেও তিনি বুঝতে পারলেন এসব পানসে বিষয় তার জন্য নয়। শিগগিরই সম্পর্কটি ভেঙে যায়।
তারপরও ২৪ বছর বয়সে ভ্যান্দেলু রবিনসন নামের একজন সহকর্মীকে বিয়ে করেন। কিন্তু নিজের নামের সঙ্গে স্বামীর নাম জুড়ে দিতে রাজি হলেন না- সেকালের বিচারে এটাকেই গুরুত্বপূর্ণ বিদ্রোহ হিসেবে গণ্য করা যায়। শিগগিরই রবিনসনকে ফেলে পোল্যান্ড চলে যান এবং ২৭ বছর বয়সে হয়ে ওঠেন দ্য ডেইলি টেলিগ্রাফের মতো পত্রিকার রণাঙ্গন সংবাদদাতা।
ঘটনাবহুল তার জীবন। বয়স তখন ২৭ বছর, টেলিগ্রাফে চাকরিজীবনের এক সপ্তাহও পুরো হয়নি। তার অবস্থান পোল্যান্ড-জার্মান সীমান্তে ক্যাটোউইসে। সীমান্ত বন্ধ করে দেয়া হয়েছে, তবে পতাকাবাহী গাড়ি সীমান্ত অতিক্রম করে দুদিকেই যাওয়ার অনুমতি পাচ্ছে। পোল্যান্ড প্রান্তে ক্লেয়ারের কাছাকাছি পতাকাবাহী গাড়ি একটি- ব্রিটিশ কনসাল জেনারেলের। তিনি সেই গাড়িটাই ধার নিয়ে ছুটলেন জার্মানিতে।
তার পরিচিত একটি উপত্যকা ধরে ফেরার পথে রাস্তার পাশে ত্রিপলঘেরা একটি বিশাল এলাকায় হঠাৎ বাতাসের তোড়ে ত্রিপলের একটি অংশ উড়ে গেলে বিস্মিত হয়ে তিনি দেখলেন সারি সারি ট্যাঙ্কের বহর সব পোল্যান্ডমুখী।
হঠাৎ দেখা এই দৃশ্যপট তার হাতে তুলে দিল বিংশ শতাব্দীর সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ভয়াবহ খবর- ‘জার্মানি পোল্যান্ড আক্রমণ করছে।’ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হয়ে গেল।
বিচিত্র ও অসনাতন সাংবাদিক জীবনের সক্রিয় সত্তরটি বছর তার কেটেছে রণাঙ্গন ও সংকটপূর্ণ স্থানে- মহাযুদ্ধকালের পূর্ব ইউরোপ, উত্তর আফ্রিকা, রক্তাক্ত প্যালেস্টাইন, সাম্যবাদী চীন, আলজেরিয়া, এডেন, ভিয়েতনাম- তার জীবনের ঘাম ও রক্তবিন্দু মিশে আছে এসব জায়গার মানুষের হাহাকারের সঙ্গে।
ওয়ার্কোহোলিক ক্লেয়ার হয়ে ওঠেন রণাঙ্গনের ওয়ারহর্স। ‘আমি খুব সাহসী ছিলাম বলব না, তাই বলে আমি একেবারেই সরল ছিলাম তা-ও না। কিন্তু আমি মনে করেছি একটা কিছু দেখা, সাক্ষী হিসেবে থাকা এবং কিছু একটা করা জরুরি- আমি কমবেশি দুশ্চিন্তামুক্তই থেকেছি। রাস্তায় থাকতাম, গাড়িতে ঘুমাতাম, একটা বিস্কুট খেয়ে একটুখানি ওয়াইন মুখে দিয়ে আবার ছুটতাম- সেইসব দিনগুলোতে আমরা বলতাম যেখানে ইচ্ছে দুটো ‘ঞ’ সঙ্গে নিয়ে যাও- একটি টাইপরাইটার এবং একটি টুথব্রাশ।’-নিজের সম্পর্কে ক্লেয়ার হোলিংওয়ার্থ।
দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় তার পছন্দের ও শ্রদ্ধার দুজন জেনারেল ছিলেন- ওয়াভেল এবং অশিনলেক; কিন্তু মন্টগোমারির জন্য তার তেমন সময়ই ছিল না-অবশ্য মন্টগোমারিও বিশ্বাস করতেন নারী-সাংবাদিকদের রণাঙ্গন থেকে দূরে রাখা উচিত।
জার্মান-ঘেঁষা- এই অভিযোগ এনে টেলিগ্রাফ তখন ক্লেয়ারকে সরিয়ে দিলে তিনি তখন শিকাগো ডেইলি নিউজের হয়ে কাজ করছিলেন। মন্টগোমারি ত্রিপোলি বিজয়ের পর তাকে এবং অন্যান্য সাংবাদিকদের ব্যাগ গুছিয়ে বিদায় নেয়ার নির্দেশ দিলেন- তিনি মনে করতেন সাংবাদিকরা তাকে খাটো করে লিখছে, প্রাপ্য মর্যাদা দিচ্ছে না। ক্লেয়ার চলে গেলেন আলজিয়ার্সে আইজেনহাওয়ারের মার্কিন বাহিনীর কাছে, অন্যরা গেলেন কায়রো।
তিনি বললেন, আমি সবই করতে পারি, পুরুষ যা পারে আমিও তা পারি। পুরুষের টয়লেট ব্যবহার করতে পারি, ফ্লোরে ঘুমতে পারি।...তার মূল কর্মক্ষেত্র কায়রো থেকে চলে এলেন প্যালেস্টাইন, ইরাক এবং ইরান।
তেহরানে একুশ বছর বয়সি ইরানের শাহ রেজা পাহলভির প্রথম সাক্ষাৎকারটি গ্রহণ করেন। ইহুদি সন্ত্রাসীরা কিং ডেভিড হোটেল উড়িয়ে দেয়ার জন্য বোমাবর্ষণ করলে তিনি বেঁচে যান কিন্তু তার চোখের সামনে ৯১ জনের মৃতদেহ। এ কারণেই তিনি ইহুদি নেতা মেনাচিম বেজিনের সঙ্গে হ্যান্ডশেক করতে অস্বীকার করেন, এমনকি বেজিন প্রধানমন্ত্রী হওয়ার পরও না।
অবিবেচক মেয়ের ওপর মা ক্ষেপে তার উইল পরিবর্তন করেন- যে হোটেল উড়িয়ে দেয়া হতে পারে এমন জায়গায় যে মেয়ে ঘুমাবে এমন দায়িত্বহীন (!) মেয়েকে মা কেন টাকা দেবেন?
সুতরাং ক্লেয়ার মাতৃসূত্রে প্রাপ্য সম্পত্তি থেকে সেই ১৯৪৮ সালেই বঞ্চিত হলেন।
ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধের সময় ভারতীয় সেনাবাহিনীর জিপে তিনি রণাঙ্গনের দিকে যাওয়ার পথে একটি সেতুর ওপর পাকিস্তানি গোলা এসে পড়ল। ভারতীয় অফিসার বললেন, আরো একটা গোলা এসে পড়–ক, তারপর আমরা দ্রুত পার হয়ে যাব। আরো একটা গোলার জন্য প্রতীক্ষায় ক্লেয়ারের চোখের তারা তখন নাচছে। মহাযুদ্ধ শুরুর ব্রেকিং নিউজ যেমন তার, গত শতাব্দীর কলঙ্কজনক ভিয়েতনাম যুদ্ধ সমাপ্তির ও আমেরিকান সেনা প্রত্যাহারের গোপন সিদ্ধান্তের ব্রেকিং নিউজটিও তারই।
১৯৮০-র দশক থেকে প্রায় স্থায়ীভাবেই তিনি হংকংয়ে অবস্থান করছেন। এর মধ্যে হংকং বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়িয়েছেন, সেন্টার ফর এশিয়ান স্টাডিজে গবেষণা করেছেন এবং বয়স নব্বই ছাড়িয়ে ভেবেছেন, একটি স্টোরি করার কাজ পেলে এখনো ছুটবেন পৃথিবীর যে কোনো প্রান্তে, সবচেয়ে দুর্গম ও ভয়ংকর স্থানে।
২৯ আগস্ট ১৯৩৯ টেলিগ্রাফের শিরোনাম : ‘পোলিশ সীমান্তে ১০০০ ট্যাঙ্ক আক্রমণ, চালানোর জন্য ১০ ডিভিশন প্রস্তুত।’ এত সব বাঘা সাংবাদিক থাকতে সদ্য যোগ দেয়া ক্লেয়ারই হয়ে গেলেন রণাঙ্গনের সেলিব্রিটি।
ক্লেয়ার আরো একবার বিয়ে করেন। টেকেনি, সন্তান ধারণ না-করার ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে বললেন, রণক্ষেত্র ও কাজ তার কাছে এমনই গুরুত্বপূর্ণ যে সন্তান অনাদরে থাকবে, উপেক্ষিত হবে, এই আশঙ্কায় আর এগোননি।
মা সাংবাদিকের কাজ কেবল অপছন্দ করতেন তা নয়, এটাকে হীন একটি কাজ বলে মনে করতেন। এদিকে যুদ্ধের প্রকৃত স্বাদ নেয়ার জন্য তিনি পাইলট লাইসেন্স করলেন, বিমান থেকে প্যারাসুট জাম্প প্রশিক্ষণ নিলেন। পরের দিনগুলোতে তিনি ইকোনমিস্ট, অবজার্ভার এবং মানচেস্টায় গার্ডিয়ানের হয়েও কাজ করলেন। ১৯৬৩ সালে ডেইলি টেলিগ্রাফ তাকে রণাঙ্গন সংবাদদাতার বদলে প্রতিরক্ষা প্রতিনিধি করতে চাইলে, উঁচু পদ হলেও তিনি তা প্রত্যাখ্যান করলেন- তার চাই রণক্ষেত্র, মন্ত্রণালয়ের প্রতিরক্ষা নীতি তাকে আকৃষ্ট করবে না।
১৯৭৩ সালে টেলিগ্রাফ তাকে পাঠিয়ে দিল বেইজিংয়ে আবাসিক প্রতিনিধি হিসেবে। বেইজিং তখন লৌহ-পর্দার আড়ালে। কিন্তু তিনি সবার আগে সম্পর্ক স্থাপন করলেন চায়নিজ জেনারেশনের সঙ্গে। তার কাজ সহজ হয়ে গেল।
এ সময় পা অপারেশনের পর চেনতানাশকের ঘোর কাটতেই তিনি বললেন, কালই যদি আমার পা ভালো হয়ে যায়, কালই কোথাও না কোথাও যুদ্ধ লাগবে।
দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ দিয়েই তার শুরু। তিনি এরপর পৃথিবীর প্রায় সব যুদ্ধই সাহসের সঙ্গে প্রত্যক্ষ করেছেন। প্রতিবেদন পাঠিয়েছেন। অ্যাকশন জার্নালিজম তার রক্তে মিশে আছে। ১০ অক্টোবর ২০১১ হংকংস্থ বিদেশি সাংবাদিক সমিতি তার শততম জন্মদিনের উৎসব করে আর তিনি জানিয়ে দেন, এখনও রণক্ষেত্রে যেতে প্রস্তুত রয়েছেন। তিনি প্রায় তিন দশক ধরে হংকংয়ে বসবাস করছেন।
১৯৯০ সালে প্রকাশিত হয়েছে তার স্মৃতিকথা ‘ফ্রন্ট লাইন’। তার অন্যান্য প্রকাশনার মধ্যে রয়েছে ‘দেয়ার ইজ এ জার্মান রাইট বিহাইন্ড ইউ’, ‘দ্য আরাবস অ্যান্ড দ্য ওয়েস্ট’ এবং ‘মাও অ্যান্ড দ্য অন এগেইনস্ট হিম’।
বাংলাদেশের স্বাধীনতাযুদ্ধে একজন প্রকৃত বন্ধু ক্লেয়ার হোলিংওয়ার্থ। ১০ ফেব্রুয়ারি ১৯১৬, একশত পাঁচ বছর বয়সে তিনি হংকং-এ মৃত্যুবরণ করেছেন।
ক্লেয়ার হোলিংওয়ার্থের সাক্ষ্য : ভারত কত দূর
আজ পূর্ব পাকিস্তানের ভেতরেই ৮০ লাখ মানুষ বাস্তুচ্যুত-পুরুষ, নারী ও শিশু ক্ষুধার্ত এবং গৃহহারা, তারা নিজ দেশে শরণার্থী।
দলে দলে গ্রামবাসী এদিক-ওদিক ঘুরে মরছে, তারা ভারতে যাবে। কিন্তু প্রায়ই ভুল পথে পা বাড়াচ্ছে হতবুদ্ধি ও বিমূঢ় এই মানুষগুলো। কিন্তু তেমন কোনো সন্দেহ নেই যে দুর্দশাগ্রস্ত এই জনসমষ্টির একটি বড় অংশই শরণার্থী শিবিরের খাবার ও আশ্রয়ের আশায় সীমান্ত পাড়ি দেবে।
বাংলাদেশ লিবারেশন আর্মি- মুক্তি ফৌজের আক্রমণাত্মক কর্মকাণ্ডের জবাব দিতে পশ্চিম পাকিস্তানি সেনারা যখন গ্রামে আগুন লাগিয়ে দিল- এই মানুষগুলোর একটি বড় অংশ বন্দুকের গোলাগুলির শব্দ শুনে এবং পাশের গ্রাম আগুনে জ্বলতে দেখে অন্ধ আতঙ্কে বাড়ি ছেড়েছে।
নিরাপদ জলাভূমির দিকে ছুটে যাওয়ার সময় মহিলাদের কেউ কেউ সহজাতভাবে কিছু কৌটা, কড়াই বা চালের বস্তা তুলে নেয়। ভাগ্য ভালো হলে পুরুষদের কারো কারো পকেটে কিছু টাকাও থেকে যায়, যা দ্রুত ফুরিয়ে আসে। ভ্রাম্যমাণ এই মানুষগুলো সেনাবাহিনী চলাচল করে এমন সড়ক সতর্কভাবে এড়িয়ে চলে।
প্রকৃতপক্ষে জিপের শব্দ শোনামাত্র সমর্থ লোকজন নিকটতম নিচু জমিতে লাফিয়ে পড়ে। কখনো কখনো এসব চলমান মানুষ বিরান গ্রামে ঠাঁই নেয় কিন্তু তারা এতই আতঙ্কিত যে খাবারের জন্য স্থানীয় কর্তৃপক্ষের কাছে আবেদন জানাতেও পারে না। তারা বিশ্বাস করে, সমস্ত ক্ষমতা সেনাবাহিনীর এবং সাহায্যের জন্য কাউকে অনুরোধ করলে তা বরং কিছু যুবক ও যুবতীর গ্রেপ্তারের কারণ হয়ে দাঁড়াবে।
বন্যার কারণে নৌকার লাগাতার অভাব আর মুক্তিফৌজের ধ্বংসযজ্ঞের কারণে রেলওয়ে ও সড়কের অচলাবস্থার কারণে এই ঘরছাড়া মানুষ কোথায় আছে তাও শনাক্ত করা যায় না, ব্যতিক্রম কেবল সেখানে যেখানে খ্রিস্টান মিশনারি কিংবা ইউরোপীয় কর্মীরা কাজ করছে।
ভারতে পৌঁছানো পর্যন্ত এদের কয়জন মৃত্যুমুখে পতিত হয় তার হিসাব পাওয়া মুশকিল। তবে কোনো কোনো ডাক্তারের মতে, কমপক্ষে পাঁচ ভাগের এক ভাগ। যে দলটি আমি দেখেছি, তাদের অপুষ্টির আগাম নমুনা দেখা গেছে। এই বাস্তুচ্যুত মানুষগুলোর জরুরি প্রয়োজন কাপড়-চোপড়, ওষুধপথ্য, কিন্তু ভারতে পৌঁছার আগে কেমন করে এসবের ব্যবস্থা করা যায়, তা ধারণা করা সম্ভব নয়।
একাত্তরের শরণার্থী শিবির
যে মিশন এখনো পূর্ব পাকিস্তানে কাজ করছে তাদের কাছে সাহায্য-সামগ্রী পাঠিয়ে এবং জাতিসংঘের মাধ্যমে পাকিস্তানকে ত্রাণকর্মীদের খাদ্য বিতরণ ও ত্রাণ তৎপরতা চালানোর অনুমতির জন্য চাপ দিয়েই কেবল সেই মানুষগুলোর কাছে পৌঁছা যেতে পারে। এ মুহূর্তে পাকিস্তান সরকার কয়েকজন পর্যবেক্ষককে থাকার অনুমতি দিয়েছে যাতে তারা দেখতে পান ত্রাণের খাবার সঠিক মুখেই পৌঁছেছে। খাদ্য একটি রাজনৈতিক অস্ত্র এবং খাদ্য যতটা দুর্লভ হতে থাকবে, পাকিস্তান সেনাবাহিনীর হাতে তৈরি শান্তি কমিটির ‘ভালো মানুষ’ সদস্যরা তাদের রাজনৈতিক সমর্থকদের খাওয়াতে শুরু করবে।
‘খারাপ মানুষ’ যারা একতাবদ্ধ পাকিস্তানের জন্য বিক্ষোভ করেনি, তাদের নিশ্চয়ই বাংলাদেশের ব্যাপারে সহানুভূতি রয়েছে, যেসব জায়গায় সেনাবাহিনী কার্যকরী বেসামরিক শাসন প্রতিষ্ঠা করতে পেরেছে, তার বাইরে সর্বত্রই তাদের খারাপ আচরণই প্রাপ্য হবে।
নিকটবর্তী বাজারে প্রচুর চাল থাকার পরও শত সহস্র মানুষ নিজ বাড়িতেই ক্ষুধার যন্ত্রণায় ভুগতে শুরু করেছে, আর্থিক জীবন ভেঙে পড়ায় তাদের ক্রয়ক্ষমতাও নেই। পাট উৎপাদনকারীরা তাদের উৎপন্ন পাট বাজারে বেচতে পারেনি। গণযুদ্ধের কারণে উন্নয়ন প্রকল্প বন্ধ হয়ে যাওয়ায় মানুষ কর্মচ্যুত হয়েছে। আবার ত্রাণের পক্ষপাতহীন বিতরণ অত্যন্ত জরুরি, নতুন হাজার হাজার দুর্গত মানুষ তাদের পরিচিত আশ্রয়স্থল ছেড়ে ভারতের পথ ধরবে।
হাজার হাজার, সম্ভবত লাখ লাখ মানুষের জীবন বাঁচাতে ত্রাণ তৎপরতাই হচ্ছে একমাত্র পথ। শরতের চাল খাওয়া শেষ হলে দুর্ভিক্ষ এড়ানো যাবে না। যে পরিমাণ চাল এখন পাওয়া যাচ্ছে, প্রতি মাসে তার চেয়ে বিশ লাখ টন বেশি চাল ও অন্যান্য শস্য খাওয়া হচ্ছে।
এখন প্রধান সমস্যা হচ্ছে পরিবহনের- প্রধান প্রধান বন্দরগুলোর খাদ্যের মজুত গড়ে তোলা হচ্ছে, এসব খাদ্যসামগ্রী বিতরণের কোনো ট্রেন নেই, জাহাজ ও লরির সংখ্যাও অত্যন্ত কম। এখন যা জরুরি ভিত্তিতে দরকার তা হচ্ছে যন্ত্রচালিত নৌকা এবং ট্রাক, যার কর্তৃত্ব থাকবে রাজধানীর বাইরে স্বল্প পরিচিত রুটে খাদ্যশস্য পৌঁছে দেয়াতে।
এ মুহূর্তে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার পাকিস্তান সেনাবাহিনীর। খাদ্যশস্য বোঝাই লরি কোনো না কোনো ফেরিতে ঘণ্টার পর ঘণ্টা আটকে থাকবে। এটা বলা ন্যায্যই হবে যে মুক্তিফৌজের ধ্বংসাত্মক কর্মকাণ্ড যোগাযোগব্যবস্থা আরো বিচ্ছিন্ন করে বাঙালিদের ভোগান্তিকে বাড়িয়ে দিয়েছে।
এ বছরের শেষ দিকে যখন দুর্ভিক্ষ শুরু হবে তখন মানুষের জীবন বাঁচাতে জরুরি পদক্ষেপ হিসেবে এয়ার লিফট বা এয়ার ড্রপ- বিমান থেকে খাদ্য ফেলার নাটকীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা দরকার হবে। কিন্তু পাঁচ থেকে সাত কোটি মানুষকে বাঁচাতে এটা কোনো বাস্তবোচিত পদক্ষেপ নয়।
দুঃখের ব্যাপার হলেও এটা সত্য যে, অনেক পরিবার বিভক্ত হয়ে আছে- যে লোক তার দোকান ঢাকা বা চট্টগ্রামে খোলা রাখতে বাধ্য হচ্ছে তার স্ত্রী ও সন্তানদের পাঠিয়ে দিচ্ছে আত্মীয়দের কাছে- সেখানে যে বিপদ আরো বেশি হতে পারে তা বিবেচনায় না এনেই। বাস্তবিকই হিসাব করে দেখা গেছে শহুরে লোকসংখ্যা কমে অর্ধেকে নেমে এসেছে।

কিন্তু এটি সংখ্যার প্রশ্ন নয়। আমি বেশ মনে করতে পারছি ঢাকা থেকে ১০ মাইল দূরে বন্যাপ্লাবিত এলাকায় অর্ধনগ্ন মানুষের বিশাল একটি লাইন ছনের ঘরের সামনে অপেক্ষমাণ- কিছু কাপড় পাবে এবং ক্যাথলিক ধর্মযাজকের কাছ থেকে দৈনিক চালের একটি টিকেট নেবে।
আমি একজন মহিলার সঙ্গে কথা বলি, তার পাঁচটি ক্ষুধার্ত সন্তান। আমাকে বলল, যুদ্ধের প্রথম দিকেই তার স্বামী নিহত হয়েছে। তার বাসা ছনের, পাকিস্তানি সেনারা পুড়িয়ে দিয়েছে। আগুন গোটা ঘরকে ছেয়ে ফেলার আগে কেবল তার সন্তানদের বের করে আনার সময় পেয়েছে। সে জন্যই তার কাপড়চোপড় কিছুই নেই। তার এই গল্প হাজারবার পুনরাবৃত্তি করা যেতে পারে।
পাকিস্তান সরকারের কোনো সাহায্য-সহায়তা ছিল না, যদিও এখান থেকে এক মাইলের মধ্যে চালু রেললাইন ছিল, যদি এই ধর্মযাজক না থাকতেন, এই বিধবা ও তার পাঁচ সন্তান সম্ভবত মৃতই পড়ে থাকত। পূর্ব পাকিস্তান থেকে পালিয়ে যে ৩০ হাজার মানুষ বার্মা সীমান্ত পাড়ি দিয়েছে, তাদের জন্যও ত্রাণ প্রয়োজন। সেখানে কোনো বিদেশিকে ঢুকতে দেয়া হয় না। কিন্তু একজন বার্মিজ ডাক্তার আমাকে বলেছেন, তাদের দুর্গতিও ভয়াবহ।
নিকোলাস টোমালিন
দ্য সানডে টাইমস

‘আমরা বাকি যারা ঘটনাটা ঘটতে দেখছি, আমরা বুঝতে পারছি ব্যক্তি হিসেবে আমাদের কী করণীয় তা নির্ধারণ করা ক্রমেই অসম্ভব হয়ে পড়েছে।’ ভারতে শরণার্থীদের ক্রমেই বেড়ে যাওয়া দুর্গতি নিয়ে বিশেষ প্রতিবেদনটি রচনা করেছেন সানডে টাইমস-এর নিকোলাস টোমালিন।
সাংবাদিকও মুহ্যমান
গত ৩০ বছরে পৃথিবী যত দুর্যোগ মোকাবিলা করেছে, তার মধ্যে ভয়াবহতমটি হচ্ছে পাকিস্তান সংকট। নৈতিকতার প্রশ্নেও এটি সবচেয়ে সরল। পাকিস্তানি জেনারেল- সেই খলনায়করা, যারা গত ২৫ মার্চ নিজ দেশবাসীর ওপর সামরিক আক্রমণের আদেশ দিয়েছেন, হিটলার-পরবর্তী যেকোনো সামরিক আগ্রাসনে, স্পষ্টতই সবচেয়ে বড় অন্যায় কাজটি করেছেন।
এর শিকার ভারতে আগত ৯০ লাখ শরণার্থী, পূর্ব পাকিস্তানে রয়ে যাওয়া সাড়ে ছয় কোটি বাঙালি- আমরা যা ভাবি তারা তার চেয়েও বেশি নিষ্পাপ, তার চেয়েও বেশি যন্ত্রণাক্লিষ্ট এবং সংখ্যায়ও তার চেয়ে বেশি। যুদ্ধ, দুর্ভিক্ষ, সাইক্লোন, চরম অবিচার, মানুষের ও পৃথিবীজুড়ে সরকারগুলোর উদাসীনতা মিলিয়ে পরিস্থিতি এতটাই ভয়াবহ যে, তা ভিয়েতনাম, বায়াফ্রা কিংবা গত ১৫ বছরে সংঘটিত যেকোনো রক্তাক্ত আফ্রিকান দ্ব›দ্বকে ছাড়িয়ে গেছে। এই বিশাল অতিনাটকীয় ট্র্যাজেডিতে যা নেই তা হচ্ছে একজন নায়ক এবং একটি সমাধান।
সপ্তাহের পর সপ্তাহ গড়াচ্ছে এবং আরো বেশি সংখ্যায় মানুষ মরছে- কেউ বলছে, সপ্তাহে দুই থেকে তিন হাজার, আমাদের বাকি যারা ঘটনাটা ঘটতে দেখছি, আমরা বুঝতে পারছি, ব্যক্তি হিসেবে আমাদের কী করণীয় তা নির্ধারণ করা ক্রমেই অসম্ভব হয়ে পড়ছে। আমরা কেবলই অসহায়।
আমাদের কেউ কেউ দুস্থ সহায়তা তহবিলে চেক পাঠিয়ে, দূরবর্তী শহরে কনসার্টের আয়োজন করে, প্রতিবাদ সভা ডেকে, স্বাধীন বাংলাদেশের প্রচারণা চালিয়ে আমাদের বিবেকে সান্ত¡নার প্রলেপ লাগাতে পারি। কেউ কেউ ভারতে এসে ৯০ লাখের মধ্যে কয়েকশ’কে খাওয়াচ্ছেন ও শুশ্রƒষা দিচ্ছেন।
অক্সফামের মতো ত্রাণসহায়তা সংস্থা এই যন্ত্রণা লাঘব করতে পারে, চূড়ান্ত দুর্যোগকে পিছিয়ে দিতে পারে; কিন্তু এদের কারোই পর্যাপ্ত অর্থ, জনবল কিংবা ক্ষমতা নেই, যা দিয়ে প্রকৃত সমস্যার সমাধান করবে। কেবল সরকার- সবচেয়ে ক্ষমতাধর সরকারগুলো একত্রে কাজ করে এই সমাধান দিতে পারে। তাদের কঠোর ও দক্ষতাপূর্ণ রাজনৈতিক কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে, যাতে ইয়াহিয়া খান ও তার পাকিস্তান সরকার স্বীকার করতে বাধ্য হয় যে তাদের গৃহীত নীতিমালা অপরাধমূলক ও মূর্খতাপূর্ণ এবং অবশ্যই তাদের কর্মকাণ্ড বন্ধ করতে হবে।
তারপর ইয়াহিয়া খান তার উত্তরসূরিদের চাপ দিয়ে পূর্ব পাকিস্তান থেকে শেষ পর্যন্ত সেনা প্রত্যাহার করাবেন এবং যেসব শরণার্থী ফিরে আসতে চায় তাদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করাবেন। তারা অবশ্যই ইন্দিরা গান্ধী ও ভারতীয় সরকারকে প্রভাবিত করবেন যেন ফিরে যেতে অনাগ্রহী শরণার্থীদের ভারতে গ্রহণ করা হয় এবং সহায়তা প্রদান করা হয়। মানুষকে অনাহার, অসুখবিসুখ ও প্রতিকূল অবস্থায় মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা করার জন্য শত লাখ পাউন্ড অবশ্যই তাদেরই দিতে হবে।
যদি সবকিছু দ্রুত সম্পাদন করা সম্ভব হয়, একটি মহাপ্রলয় এড়ানো সম্ভব হবে। পূর্ব পাকিস্তান, মূলত গোটা বাংলাই তারপরও দুর্যোগকবলিত এলাকা হিসেবে রয়ে যাবে।
কলকাতার কাছাকাছি স্থাপিত কয়েকটি শরণার্থী শিবির দেখে আসার প্রায় এক সপ্তাহ পর আমিই মহাপ্রলয়ের এই ভাবনা নিয়ে লিখতে বসেছি। আমি শহরের কেন্দ্রস্থলে গ্র্যান্ড হোটেলের বিশাল সুইমিংপুলের পাশে বিছানো নরম ম্যাট্রেসে শুয়ে, বেশ কয়েক বোতল ঠাণ্ডা বিয়ার খেয়ে বাদাম চিবোতে চিবোতে কখনো বিরতি দিয়ে নোংরাভাবে ছাপা ‘আই লাভ ইউ’ কমিক পড়ছি, যেখানে একটি যুবক ও যুবতী পাহাড়ের পাদদেশে স্কি করছে। মেয়েটি বলছে, ‘স্টিভ, আমি তোমাকে ভালোবাসি, কিন্তু সে যখন আমার এই গোপন বিষয়টি জেনে যাবে তখন কী করবে? সে কি আমার অতীত ভুলে যেতে পারবে?’
আমি পুলে সাঁতার কাটি, অদ্ভুত তিতকুটে তরকারি খাই এবং বাঙালি লিফটবয়দের আচরণে বিরক্ত না হতে চেষ্টা করি- যারা বড় অঙ্কের টিপসের আশায় জৌলুশ দেখানো মহারাজাদের বেলায় যেমন করে, আমাকে নিয়ে সে ধরনের বাড়াবাড়ি করে।
শরণার্থীদের বেলায় যা ঘটছে তা দেখার পর আমার যে স্নায়বিক দৌর্বল্য সৃষ্টি হয়েছে তা কাটাতে আমার লম্বা সময় লেগে যাচ্ছে বলেই আমি এসব করছি। সংবাদপত্র জগতের আমার অন্য সহকর্মীদেরও একই অবস্থা। আমি এটা উল্লেখ করছি এ কারণে যে অন্য সব পরিস্থিতিতে তারা সবচেয়ে ভয়ংকর ঘটনাগুলো দেখেছে, দুঃসহ মানবিক যন্ত্রণার অভিজ্ঞতা লাভ করেছে এবং তারপরও নিজেদের ভেতর এর কোনো প্রভাব পড়তে দেয়নি।
আমি তাদের দেখেছি ভিয়েতনামে, বায়াফ্রা থেকে ফিরে আসতে এবং বাংলার সাইক্লোনে। তারা উদ্বিগ্ন হয়েছে, সমব্যথীও হয়েছে কিন্তু নিজেদের আবেগ সামলে নিতে পেরেছে। এবার আর সামলে নিতে পারছে না।
গলায় ক্যানসারের জন্য আমার যে সহকর্মীর অপারেশন হয়েছে, তাকেও এখন ফিরে আসতে হয়েছে প্রতিদিন ৭০টি সিগারেটে। এখানে জমায়েত সংবাদপত্রকর্মীরা নিজেদের রক্ষার জন্য মারাত্মক উন্নাসিকতার বর্ম পরিধান করে আছে।
একটা ছবিতে দেখা যাচ্ছে বিশীর্ণ একটি বাঙালি মেয়ে ভাঙা এক টুকরো আয়নায় নিজেকে দেখে মুগ্ধ হচ্ছে, এটা দেখে একজন ‘অক্সফামের পোস্টার হওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছে’ মন্তব্য করায়, অন্যরা সবাই খিলখিল করে হেসে ওঠে। একজন আলোকচিত্রী বলে, আজ একটা চমৎকার ছবি পেয়েছি, দুটো শিশু একত্রে কাদার মধ্যেও মরতে বসেছে।
অন্য জন বলল, আমারটা এর চেয়ে ভালো। আমি দুজনকে হাত ধরাধরি করিয়ে দিয়েছি।
কলকাতার সবাই একই রকম আবেগপ্রবণ। একজন স্থানীয় কূটনীতিক, যাকে দেখে মনে হয় পুনর্জন্ম পর্যন্ত একই রকম পরিশীলিত থাকবেন, তিনি আবেগের মধ্য দিয়ে যুদ্ধের কথা বলছেন। তিনি মনে করেন, এই নভেম্বরে ভারত এবং পাকিস্তানের মধ্যে কেবল একটিই থাকবে, যদি এই নভেম্বরে না হয়, আগামী নভেম্বরে। তিনি যুক্তি দেখিয়ে বলেন, ভারত অনুৎপাদনশীল এই ৯০ লাখ নতুন মানুষের অর্থনৈতিক ভার বহন করতে কোনোভাবেই সক্ষম হবে না।
আসামে এর মধ্যে দাঙ্গা শুরু হয়েছে। সমতলের যেসব বাঙালি পালিয়ে আসামের পাহাড়ে এসেছে, আসামের মানুষ তাদের পছন্দ করছে না। এমনকি কলকাতার আশপাশের ক্যাম্পেও অবিরাম কলহ ও মারামারি লেগেই আছে। ভারতীয় কৃষকরা শুরুতে তাদের এই বিপদাপন্ন ভাইদের স্বাগত জানিয়েছিল। কিন্তু এখন যখন দেখছে এই আগন্তুকেরা নামমাত্র মজুরিতে তাদের কাজ নিয়ে নিচ্ছে, তাদের মাঠ নষ্ট করে ফেলছে, তাদের জিনিসপত্র ও নারীদের চুরি করে নিয়ে যাচ্ছে, তখন শত্রæতা বাড়তে শুরু করে।
এই কূটনীতিবিদ যুক্তি দিয়ে বলছেন, অতএব, এ কারণেই ভারত শিগগিরই পূর্ব পাকিস্তান ভূখণ্ডে সামরিক আক্রমণ চালাতে বাধ্য হবে। তারপর এক সপ্তাহের মধ্যে (স্থানীয় বাঙালিদের সহায়তায়) ইয়াহিয়া খানের সেনাবাহিনী হটানোর বাজিতে যাবে। তারপর ভারত সব শরণার্থীকে আবার পূর্ব পাকিস্তানে ফেরত পাঠিয়ে দেবে। তারপর ঠিক করবে পূর্ব পাকিস্তানকে ভারতের একটি প্রদেশে পরিণত করা হবে কি না। এর সবই ঘটতে হবে নভেম্বরে মধ্যে। এই সময় তুষার সকল গিরিপথ বন্ধ করে রাখে, ফলে উত্তর দিক থেকে আক্রমণ করতে চীনকে বাধা দেবে।
এ ভদ্রলোক অনেক দিন ধরে ভারতে আছেন। তিনি বাঙালিদের ভালোবাসেন, এমনকি কলকাতাকেও ভালোবাসেন।
এই গ্রীষ্ম পর্যন্ত তিনি বিশ্বাস করতেন শক্তিশালী নতুন একটি কেন্দ্রীয় সরকার ক্ষমতা গ্রহণ করলে ভারতের উপর্যুপরি ভয়াবহ সংকট, দুর্ভিক্ষ ও যুদ্ধ শেষ হয়ে আসবে। তিনি ভেবেছেন, শেষ পর্যন্ত দেশটি শান্তিপূর্ণ একতাবদ্ধ ও সমৃদ্ধ হয়ে উঠবে। আর এখন এই অবস্থা!
তিনি বললেন, ‘আমি আপনাকে যতটা বলছি, তার চেয়ে বেশি বিষাদগ্রস্ত। বেরোনোর কোনো পথ দেখছি না, আমি কোনো সমাধান দেখছি না। মৃত্যু ও ধ্বংস চারদিকে- আর আমি তা-ই দেখতে পাচিছ।’
আমার বন্ধু ভারতীয় আর্মি জেনারেলের দুই চোখের ঠিক দুই ইঞ্চি নিচে পুটলি জমে আছে। রাতে কদাচিৎ তার ঘুম হয়। ‘আমি বুঝতে পারছি না তারা আক্রমণ করতে যাচ্ছে কি না, যদি করে কখন, কীভাবে। আমি এই পাকিস্তানি সেনাদের মনোভাব আর বুঝে উঠতে পারি না। তিনি বলেন, ‘সত্যিই আমার মনে হয়, তারা পাগল হয়ে গেছে, তারা দেখতে পাচ্ছে পূর্ব পাকিস্তানে তাদের পরিকল্পনা পুরোপুরি ভেস্তে গেছে- এখন মনে হচ্ছে এতে তাদের নির্বুদ্ধিতা আরো বেশি উৎসাহিত হচ্ছে। তাদের চোখে ট্র্যাজিক যোদ্ধার অন্ধত্ব। তাদের উদ্দেশ্য যত ভয়াবহ, অকার্যকর ও অন্যায়- ততই সেটা তাদের কাছে মহান বলে মনে হচ্ছে। তাদের কর্মকাণ্ডে মানুষ যতই নিশ্চিহ্ন হচ্ছে, তারা ততই তরবারি ঘোরাচ্ছে।’
‘সত্যি বলতে কী আমার মনে হচ্ছে ইসলামাবাদ সরকার শেষ চেহারাটি দেখিয়ে ছাড়বে এবং যুদ্ধে নামবে। যদি তা-ই করে তাহলে গোটা উপমহাদেশ তাদের সঙ্গে জড়িয়ে পড়বে- শরণার্থী ও আমাদের বাঙালিদের কথা বাদই যাক। তারপর চীন এসে যেতে পারে, তারপর রাশিয়া। তারপর আমেরিকা এবং তোমরা, তারপরই আমাদের সামনে তৃতীয় মহাযুদ্ধ।’
ততক্ষণে মনে হচ্ছে বিলাসী সুইমিং পুলটা আশ্রয় দেয়া বন্ধ করে দিয়েছে। টুপ করে আস্তে পানিতে পড়ার শব্দ জানিয়ে দিল শবভোজী কাকের অসতর্ক ঠোঁট থেকে একটা মৃত ইঁদুর পড়ে গেছে। পুলের ডাইভিং বোর্ড থেকে ঝাঁপিয়ে পড়ার আমোদকে তা ব্যাহত করল।
সুইমিং পুলের চারপাশে আমরা যারা স্নায়ুবৈকল্যগ্রস্ত ও উদ্বিগ্ন অবস্থায় রয়েছি তার কারণ সম্ভবত পৃথিবীর এ অংশটিতে বিরামহীন দুর্যোগের ঘনঘটা। দুর্যোগ এখানে কখনো বিরতি দেয় না। এর মানে এই নয় যে আমি বিজয় ও পুনর্বিজয়ের পৌনঃপুনিকতার ইতিহাসের কথা তুলছি- যোদ্ধাদের বিজয়ের ঢেউয়ের পর ঢেউ বাংলার উজ্জ্বল সমৃদ্ধ এলাকাকে পৃথিবীর দরিদ্রতম অংশে পরিণত করেছে, সেই সঙ্গে যোগ দিয়েছে প্রাকৃতিক দুর্যোগ।
যা সবচেয়ে বেশি ব্যথিত করে তা হচ্ছে সাম্প্রতিক সময়ের ইতিহাস। দুর্ভাগ্য সৃষ্টি করেছে দারিদ্র্য, যা সৃষ্টি করেছে আরো বড় দুর্ভাগ্য, যা এখন আর অধিক প্রাকৃতিক দুর্যোগ, শোষণ, অভ্যন্তরীণ দুর্নীতি, ধর্মীয় গোঁড়ামি ও রাজনৈতিক দাবানল ধারণ করতে অক্ষম। এ রকম নৈরাশ্যজনক ও বিভ্রান্তিকর স্থানে কর্মচঞ্চল বেনিয়াদের শোষণ কেমন করে বন্ধ করা যাবে? কেমন করে ইসলামের নীতি বিসর্জন দিয়ে জন্মবিস্ফোরণ কমাতে সঠিক জন্মশাসন চালু করা হবে?
লম্বা বাদামি বর্ণের আবেগহীন পশ্চিমের মানুষ আর ছোট আকৃতির শ্যামলা উত্তেজনাপূর্ণ মেধাবী মানুষের জাতিগত শত্রæতার মধ্যে এটা কতটা গ্রহণযোগ্য যে পূর্ব পাকিস্তান কার্যত পশ্চিম পাকিস্তানের একটি উপনিবেশে পরিণত হয়ে থাকবে। পাঞ্জাবি ও বিহারিরা মনে করত, বাঙালিরা বেচারা নোংরা বানরের চেয়ে একটু ভালো এবং নিয়ন্ত্রণের অযোগ্য। আর তাদের কথা ও উদ্ভূত পরিস্থিতি তাদের এই বিশ্বাসের যৌক্তিকতা তুলে ধরে।
বাঙালিরা পশ্চিমের সেনাশাসক, বেনিয়া ও মহাজনদের মনে করে সাম্রাজ্যবাদী ব্রিটিশদের চেয়েও খারাপ, তাদের চেয়ে কম দয়ালু, বাঙালির বিশেষ সংবেদনশীলতা ও আত্মপ্রকাশের মেধাকে বুঝতে তারা ইংরেজদের চেয়ে কম সক্ষম। অবাক হওয়ার কারণ নেই, শত্রæতা এমনই হিংস্র পর্যায়ে পৌঁছে যে মার্চের বিস্ফোরণের ঠিক আগে বাঙালি হিংস্র বিক্ষোভ চালিয়ে যায় এবং পশ্চিমের বিদেশিদের হত্যা করতে থাকে। যেহেতু এত বছর তারা এমন হীন নারকীয় জীবনযাপন করেছে এ ধরনের নৃশংসতা (উপমহাদেশে এই সহিংসতার ঐতিহ্য দীর্ঘদিনের) পুরোপুরি অনুধাবনযোগ্য। অবাক হওয়ার কিছু নেই, গত বছরের সাইক্লোনে ১০ লাখ মানুষ নিহত হওয়ার ও ডুবে মরার পরও তারা শেষ পর্যন্ত প্রায় সর্বসম্মতভাবে ইসলামাবাদের আধিপত্যের বিরুদ্ধে আওয়ামী লীগকে ভোট দেয়।
এ পরিস্থিতিতে জেনারেল ইয়াহিয়া খানের সিদ্ধান্ত যে সাধারণ সামরিক সমাধানই একমাত্র সম্ভাবনা, তা অপরাধমূলক এবং মূর্খতাপূর্ণ। তার জানা উচিত ছিল কোনো সামরিক সমাধান এ ধরনের শত্রæতার মোকাবিলা করতে পারে না, আর স্পষ্টতই এটা কেবল অন্যায় ও তার গৃহীত পদক্ষেপ বেআইনি নয়, তা ব্যর্থ হতেও বাধ্য।
মার্চের আক্রমণের পরের মাসগুলোতে যা কিছু ঘটেছে তার সবই ইয়াহিয়ার অনুমান করার কথা। দেশের শত্রæভাবাপন্নতা কমেনি, বরং বেড়েছে। বাঙালি গেরিলারা যোগাযোগ ব্যবস্থা ধ্বংস করে দিয়েছে। যেখানে তারা ব্যর্থ হয়েছে, সেনাবাহিনীর পালটা আক্রমণ তা সফল করে দিয়েছে। প্রাকৃতিকভাবে উর্বর এই এলাকার খাদ্য উৎপাদন বাধাগ্রস্ত হয়েছে। ধর্মীয় ও জাতিগত বিরোধে শত্রæতা ও হত্যা চলতে থাকে। পূর্ব পাকিস্তানের মুসলমানদের মধ্যে এক কোটি হিন্দু বসবাস করত। যখনই এটা স্পষ্ট হয়ে উঠল যে পাকিস্তানি সেনারা নির্বিচারে হিন্দুদের হত্যা করছে, তাদের প্রায় সবাই ভারতে পালিয়ে যায়। তাদের সঙ্গে চলে আসে মুসলিম বাঙালি জাতীয়তাবাদী নাগরিক, আওয়ামী লীগের সমর্থক এবং যারা কেবল যুদ্ধ এড়াতে চায়, সে ধরনের মানুষ। লড়াই ও নৈরাজ্য নিজ থেকেই বড় হতে শুরু করে।
সেনাবাহিনী ভারতীয় সীমান্ত থেকে গেরিলাদের দ্বারা আক্রান্ত হবে আর সেনাবাহিনী তার প্রতিশোধ নেবে স্থানীয় সাধারণ মানুষের ওপর। তারপর এই সেনাবাহিনী বাঙালিদের কবজায় আনার জন্য অনিয়মিত মুসলমান স্বেচ্ছাসেবক নিয়োগ দিতে শুরু করে। এরাই হচ্ছে রাজাকার। এরা দুর্র্বৃত্ত ও সুযোগসন্ধানী, এরাই এখন অধিকাংশ খুনখারাবি করছে। তাদের কারণেই বর্ষাকালের বর্ষণ উপেক্ষা করে এখনো শরণার্থীরা সীমান্ত পাড়ি দিয়ে ভারতে আসছে।
বৃষ্টি থেমে গেলে পরিস্থিতি বদলে যাবে। সেনাবাহিনী যেহেতু রাস্তাঘাট ও সীমান্ত নিয়ন্ত্রণে অধিকতর সক্ষম, দেশের অবস্থা স্থিতিশীল হয়ে উঠতে পারে। যেহেতু মানুষের গতিশীলতা বাড়বে, মানুষ মানুষকে হত্যা করার জন্য ছুটে আসবে, ফলে পরিস্থিতি আরো খারাপ হতে পারে। কোনো একটি ভারতীয় কর্তৃপক্ষ ভবিষ্যদ্বাণী করেছে শরণার্থীদের নতুন একটি বন্যা আসবে- সম্ভবত আরো ৪০ লাখ। অন্যরা ভবিষ্যদ্বাণী করেছে যে এখন ভারতে যেসব শরণার্থী অবস্থান করছে, তাদের সিকিভাগ থেকে অর্ধেক আবার পাকিস্তানে ফিরে যাবে।
যা-ই হোক, এই শরণার্থীরা ভারতের ত্রাণশিবিরে গাদাগাদি করে বাস করছে, তাদের খাদ্য অপর্যাপ্ত। কিছুই করার নেই তাদের, বেঁচে থাকার মতো জায়গাও নেই। যে পড়তে পারে কিংবা কেবল চোখে দেখতে পারে, পাকিস্তানের ক্ষুধার্ত শরণার্থীদের চেহারা তাদের কাছে পরিচিত হয়ে উঠেছে। খবরের কাগজ, টেলিভিশন ও বিজ্ঞাপনী বিলবোর্ড এই দৃশ্য আমাদের সবার ওপর চাপিয়ে দিয়েছে।
এ ধরনের বোমাবর্ষণের পর এদের বাস্তবে দেখা পাওয়া কোনোভাবে একটি এন্টিক্লাইমেক্স। ঘটনাক্রম কারও করুণাধারাকে বাধাগ্রস্ত করে। দীর্ঘ কাক্সিক্ষত ক্যাথিড্রাল কিংবা পুরনো দুর্গ যেমন সব সময়ই স্মৃতিজাগানিয়া ছবির মতো নয়, তেমনি কলকাতার কাছাকাছি কিছু শরণার্থী শিবিরে অবস্থা বিস্ময়করভাবে স্বাভাবিক।
কেউ কেউ বেশ আনন্দ-ফুর্তিতে আছে। কেউ কেউ বেশ মোটাসোটা। কারও করার মতো কাজ আছে। কেউ কেউ পূর্ব পাকিস্তানে নিজ গ্রামে যে অবস্থায় থাকত তার চেয়ে এখানে ভালো জীবনযাপন করছে। অধিকাংশই তা নয়, লাখ লাখ শরণার্থী তা নয়। সীমান্তের কাছে রাস্তায় হাঁটতে হাঁটতে দেখা যায় কেবল ক্যাম্প আর ক্যাম্প, হাজার হাজার তাঁবু রাস্তার দুই পাশে, গাছে, ইটের স্তূপে জনাকীর্ণ এই জমিনে যেখানে একটু জায়গা পাওয়া যায়, সেখানেই এই ক্যাম্প, কেবল তাদের সংখ্যা- যা এতই ভয়াবহ।
কিছু সময় গেলে মানুষের দুর্দশা নিয়ে বিশেষজ্ঞ হয়ে উঠলে স্পষ্টভাবে বোঝা যায় এই ভয়াবহতার কারণেই পরিস্থিতি দুর্বোধ্য হয়ে উঠেছে। আমি দুই-তিনটি শরণার্থী ক্যাম্পের চারপাশে গাড়ি চালিয়ে গিয়েছি এবং একদিন অপেক্ষাকৃত উন্নতমানের ব্যবস্থাপনার একটিতে ঘুমিয়েছি।
প্রথমে আমি ব্যাখ্যা করেছি হাসনাবাদ সীমান্ত পর্যন্ত চলে যাওয়া রাস্তার পাশে যে শরণার্থীরা আছে, তাদের অবস্থা ততটা খারাপ নয়। কলকাতার উপশহর সল্ট লেক সিটিতে ২ লাখ ৫০ হাজার শরণার্থী মোটামুটি ভালো অবস্থায় আছে। তাদের প্রয়োজনীয় খাবার ছিল। বিদেশি ত্রাণ সংস্থা তিন-চারটে হাসপাতাল স্থাপন করেছে। কলকাতার কাছাকাছি হওয়ার কারণে এক ধরনের পুলিশি ব্যবস্থাও ছিল। কিন্তু এখানেও শিশুদের সবচেয়ে খারাপ দেখাচ্ছিল।
শিশুরা কতটা ভুগছে তা বুঝতে কিছুটা পুষ্টিজ্ঞান থাকা প্রয়োজন। একটি শিশুকে যদি শত শত মাইল পাড়ি দিয়ে আসতে হয় এবং সেই শিশু যদি তারপরও স্থায়ীভাবে রোগগ্রস্ত অবস্থায় বেঁচে থাকে, তাহলে তার খাবার হবে অন্য সবার চেয়ে আলাদা এবং প্রোটিনসমৃদ্ধ। তার বিশেষ পরিমাণ খাবার দরকার। ভারতীয় কর্তৃপক্ষ এখন জনপ্রতি ৪০০ গ্রাম চাল, কিছু তরকারি, রান্নার তেল ও শস্যদানার রেশন দিয়ে থাকে। বিতরণের সমস্যার কারণে এই পরিমাণ ২০০ গ্রামে নেমে এসেছে এবং অনেক ক্ষেত্রে শিশুরা পায় এর অর্ধেক, দিনে কেবল ১০০ গ্রাম চাল। এর মানে এক মুঠোতে যতটুকু ধরে ততটুকু চাল।
বিদেশি ও ভারতীয় চিকিৎসা বিশেষজ্ঞদের মতে, যদি এই শিশুদের অতিরিক্ত প্রোটিন দেয়া না হয়, তাহলে এরা অবশ্যই মৃত্যুবরণ করবে। শিশুদের তিন-চতুর্থাংশ নয় মাসের মধ্যেই মারা যাবে। তার মানে ১০ লাখ শিশু।
অতএব, ধীরে ধীরে যথেষ্ট পরিশ্রম করে শিশুদের জন্য বিশেষ খাদ্যকেন্দ্র গড়ে তোলা হচ্ছে, যেখানে তারা দুধ পাবে, পাবে উচ্চ-প্রোটিনযুক্ত খাবার ‘বালাহার’। এখনো যেহেতু অধিকাংশ খাদ্যকেন্দ্রে হাতে হাতে শিশুখাবার দিয়ে দেয়া হয়, শিশুরা বাড়ি ফিরে আসে এবং পুরনো ঐতিহ্য অনুযায়ী এর অনেকটাই তাদের কাছ থেকে নিয়ে নেয়া হয় এবং বড়দের ভাগ করে দেয়া হয়। কাজেই এ লেখাটি যখন প্রকাশিত হবে সে সময় পর্যন্ত শিশুদের মৃত্যুর আশঙ্কা একই রকম থেকে যাচ্ছে।
হতে পারে ১০ লাখ শিশু হয়তো মরবে না। তারা কোনোভাবে টেনেটুনে বেঁচে থাকবে। কোনো আশা নেই, শিক্ষা বা কাজকর্ম নেই, তাদের ঘিরে আরো ৭০ লাখ বয়স্ক মানুষ, তাদেরও কিছু করার নেই, কোনো আশা নেই, কেবল বাংলাদেশি বিদ্রোহীদের অগ্নিগর্ভ বক্তব্য তাদের স্পর্শ করে না, নিজ দেশ পুনরায় আক্রমণ করে উদ্ধারের নিঃসঙ্গ বাসনা, পাকিস্তানি ট্যাঙ্ক গুঁড়িয়ে দেয়ার স্বপ্ন তাদের স্পর্শ করে না যে তারা টিকে থাকবে।

একাত্তরের শরণার্থী শিবির
এই সম্ভাবনা আশঙ্কামূলক ও বিপজ্জনক। এটা অবাক করা কোনো ব্যাপার নয় যে এখানে সবাই আয়ুবিকারগ্রস্ত, ভেঙে পড়া, বিষয় ও সমাধানহারা।
এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে শিবিরের চারপাশের মর্মস্পশী মুহূর্তগুলো। পানির ভেতর দিয়ে হেঁটে যাওয়া বৃদ্ধা, দুই কৌটা চাল, কাঁধ পর্যন্ত তলিয়ে গেছে পানির নিচে, চালের পাত্র মাথার উপর ধরে রাখা। অধিকাংশ সময় কোনো কোনো ক্যাম্পের অবশিষ্ট কিছু তাঁবুর গুচ্ছে বাঁশের সরু সাঁকোতে পৌঁছাতে হয়, গোটা পরিবারই কাদায় ঢাকা, নিজেদের মলমূত্র কখনো ভালো করে ধোয়া হয় না- পানি ভেঙে খাবার আনতে যেতে হয়, ওষুধ থেকে তারা পুরোপুরি বঞ্চিত।
দিয়ারা নামের একটি ক্যাম্প, যেখানে ৩০ হাজার মানুষের বসবাস। পরিচ্ছন্ন তাঁবুতে সবাই বেশ ভালোভাবেই বসতি স্থাপন করেছিল- রাতারাতি বন্যায় তলিয়ে গেছে। তাদের যা কিছু ছিল, সবই হারিয়ে গেল। আশ্রয় হারাল, তারপর জমায়েত হলো পার্শ্ববর্তী উঁচু জমিতে। তৃতীয় বা চতুর্থবারের মতো এই মানুষগুলো চেষ্টা চালাল নিজেদের জীবন আবার সংগঠিত করতে।
হাসনাবাদ রেলওয়ে স্টেশনে একটি অভ্যর্থনা কেন্দ্র; মরিয়া হয়ে-ওঠা মানুষের দুঃস্বপ্নে লোকারণ্য, খাবারের জন্য নাম তালিকাভুক্ত করতে তারা অপেক্ষা করছে। বয়োবৃদ্ধ পুরুষ ও নারী এতই ক্লান্ত যে নড়তেও পারছে না। তরুণদেরও চক্ষু বের হয়ে আসা, অপুষ্টির কারণে খুশকির মতো সাদা পরত তাদের গায়ের ত্বকে এবং সম্ভাব্য সব ধরনের রোগ- সম্ভবত সাধারণ ক্লান্তি থেকে উদ্ভূত। মৃত শিশুরাও রয়েছে, কুঁচকে ছোট হয়ে আসা তাদের মুখে অস্বাভাবিকভাবে প্রকটিত দাঁত। সমর্থ প্রাপ্তবয়স্কদেরও কিছু করার নেই, কেবল তাঁবুতে গুঁটিশুটি মেরে পড়ে থাকা, শেষ কয়েকটি টাকা খরচ করে স্থানীয় চাষিদের সঙ্গে ভালো খাবারের জন্য দরকষাকষি করা।
এই দৃশ্য সর্বত্র। যে কেউ এর অন্তহীন তালিকা তৈরি করতে পারবে। এ মুহূর্তে সবচেয়ে বেশি দরকার- বন্যার পানি যখন নেমে যাচ্ছে- এরপর কী হবে তা নিয়ে ভাবা এবং চেষ্টা করা। সবচেয়ে খারাপ যা ঘটতে পারে তা হচ্ছে শরণার্থী এবং স্থানচ্যুত ভারতীয় কৃষক, যারা নিজেরাও অভুক্ত, তাদের মধ্যে রাজনীতিক সংকট। এদিকে বাংলায় শীত এসে যাচ্ছে। এতে খুব বেশি কিছু এসে যায় না, এ দিকটা উষ্ণই, কিন্তু সিলেটের উত্তরে আসামে বরফ শীতল। দুই মাসের মধ্যে তুষারপাত হবে, হিমশীতল আবহাওয়া থাকবে আর অবিরাম ঠাণ্ডা।
বাঙালি শরণার্থীদের কোনো কাপড় নেই, কম্বল নেই, অল্প কিছু কেবল তাঁবু। এই মানুষগুলোর জন্য এ মুহূর্ত ৩০ লাখ কম্বল দরকার। এর সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে কাপড় ও তাঁবু।
এই ৯০ লাখ শরণার্থী রাজনৈতিক অবিচারের শিকার হয়েছে। তারপর সাইক্লোন, তারপর যুদ্ধ, তারপর বাস্তচ্যুতি, ক্ষুধা, রোগবালাই- খারাপ যা কিছু হতে পারে তার সবই তাদের ভুগতে হয়েছে। এখন তারা এমন এক দেশে, যাদের সামর্থ্য নেই তাদের দেখাশোনার; তারপর এসেছে বন্যা আর এখন তার মোকাবিলা করবে প্রচণ্ড শীত সম্ভাবনার।
আমি বলেছি, গত ৩০ বছরে পৃথিবী এ ধরনের দুর্যোগের ঘা খায়নি। আমি বলতে পারি এটি এখন এক ধরনের ভয়াবহ মহাপ্রলয়, যা কারও পক্ষে সঠিক ও যৌক্তিক কোনো শর্তে মোকাবিলা করা সম্ভব নয়।
কলকাতার সব সাংবাদিকেরা জানেন, অক্সফাম ও অন্য ত্রাণকর্মীরা জানেন, এটি আমাদের জন্য অত্যন্ত বড় একটি সমস্যা। এটি এখন আর সাধারণ সহানুভূতি বা সাধারণ চ্যারিটিতে সামলে নেয়ার বিষয় নয়। মোটের ওপর পৃথিবী চ্যারিটিতে সাড়া দিয়েছে যে মাসে, যখন কলেরা মহামারির সংবাদ প্রচারিত হয়, আমরা আমাদের হাতের অর্থ করুণার জোয়ারে ঢেলে দিয়েছি। কাজেই পৃথিবীর কার্যকরী করুণা আসলে ফুরিয়ে গেছে। কাজেই প্রকৃত দানশীলতা দেখাতে হবে কঠোর রাজনৈতিক সিদ্ধান্তের মাধ্যমে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করে। পাকিস্তান সরকারের কাছে এটা স্পষ্টভাবে প্রকাশ করতে হবে যে কেবল আন্তর্জাতিক আর্থিক ও সামরিক সহায়তায়ই তারা টিকে আছে।
পাকিস্তান যদি বর্তমান নীতিতেই চলতে থাকে তাহলে তারা পাকিস্তানকে পরিত্যাগ করলে পাকিস্তানের অবস্থা অনেক খারাপ হয়ে যাবে। রাজনৈতিক পদক্ষেপ সেনা কর্মকর্তাদের দিকে নির্দেশিত হবে, যারা এখনো ইয়াহিয়া খানকে সমর্থন দিয়ে যাচ্ছে।
তারা যদি তাকে বাদ দেয়ার ব্যাপারে সম্মত হতে পারে, পুরনো ভুলের দায় তার ঘাড়ে চাপিয়ে দিতে পারে, সমঝোতার নতুন নীতিমালা গ্রহণের একটি সুযোগ সৃষ্টি হয়। সেটিই প্রথম অত্যাবশ্যকীয় কাজ। তারপর কী ঘটবে তা খুব স্পষ্ট নয়। একটি স্বাধীন বাংলা দেশ সৃষ্টি হতে পারে। কিন্তু তাতেও অনেক সমস্যার সৃষ্টি হবে। পাকিস্তানের একটি নতুন সংবিধান হতে পারে, যাতে পূর্ব পাকিস্তান একটি ফেডারেল অংশ হিসেবে পশ্চিম পাকিস্তানের সঙ্গে যুক্ত থাকতে পারে। অথবা শেষ পর্যন্ত একটি নতুন জাতিগত রাষ্ট্রের অভ্যুদয় ঘটতে পারে, যার জনসংখ্যার অর্ধেক মুসলমান অর্ধেক হিন্দু। পাকিস্তান ও ভারত উভয় অংশ থেকে কেটে নিয়ে নতুন রাষ্ট্র। সবগুলো সম্ভাবনাই বিপজ্জনক। কিন্তু এখন যা ঘটতে দেয়া হচ্ছে, কোনোটাই এত বিপজ্জনক নয়।
মহাশক্তিগুলো রাজনৈতিক সদিচ্ছায় নিজেদের অনুপ্রাণিত করে এখনই পরিস্থিতি পাল্টে দিতে পারে এবং তা তাড়াতাড়ি করা উচিত। এত দিন মানুষ যা জেনেছে, এই দেশগুলোর উচিত হবে তার চেয়ে আরো অনেক বড় আকারে অর্থ, খাদ্য ও দ্রব্যসামগ্রী পাঠানো যেন শরণার্থীদের পূর্ব পাকিস্তানে পুনর্বাসিত করতে, ভারতে ভর্তুকি দিতে তা যথেষ্ট হয়।
যদি তারা থেকে যেতে চায়, এর মানে সম্ভবত জাতিসংঘের সংস্থার মাধ্যমে লাখ লাখ পাউন্ড। যদি তা না ঘটে গ্র্যান্ড হোটেলের সুইমিংপুলের চারপাশের শৌখিন হিসেবে আমাদের স্নায়ুবিকার, ভেঙে পড়া ও বিষণ্নতার ভাব চলতেই থাকবে। স্থানীয় কূটনীতিবিদ ও জেনারেলরা মহাপ্রলয়ের ভাষায় বলতেই থাকবেন, রাতে ঘুমোবেন না। লাখ লাখ শিশু মৃত্যুবরণ করবে। হাজার হাজার প্রাপ্তবয়স্কও একইভাবে মারা যাবেন। আর যে কোটি কোটি মানুষ ভারতীয় উপমহাদেশে বসবাস করে, তাদের দুর্যোগ এখনকার দুর্যোগকেও খাটো করে ফেলবে।
(ঈষৎ সংক্ষেপিত)
আত্মসমর্পণের আগে...
নিকোলাস টোমালিন, ঢাকা থেকে
ঢাকায় বৃহস্পতিবার আত্মসমর্পণের আগে পাকিস্তানি সেনাবাহিনী শহরের বুদ্ধিজীবী, বিজ্ঞানী, ব্যবসায়ীদের গ্রেপ্তার করেছে এবং তাদের মধ্যে পঞ্চাশেরও বেশি লোককে গুলি করে হত্যা করেছে। আকস্মিক সামরিক অভিযানের অংশ হিসেবে এবং নিবিড় পরিকল্পনার আওতায় বাঙালি এলিট নিধনের অংশ হিসেবে এই হত্যাকাণ্ড ঘটানো হয়েছে। এটা অবশ্যই কমান্ডিং অফিসার জেনারেল নিয়াজিসহ পাকিস্তান হাইকমান্ডের পূর্ণ জ্ঞাতসারে ঘটেছে।
এসব মৃতদেহের আবিষ্কার ঢাকা শহরে উত্তেজনা বাড়াতে পারে, পালটা হত্যাকাণ্ড ও দাঙ্গার জন্ম দিতে পারে, এমনকি মুক্তিবাহিনীর গেরিলা ও ভারতীয় সেনাবাহিনীর মধ্যেও সংঘর্ষের সৃষ্টি করতে পারে।
ঢাকার মূল শহরের পাশের রায়েরবাজারে কতগুলো বিচ্ছিন্ন গর্তে নিহত বুদ্ধিজীবীদের মৃতদেহ আবিষ্কৃত হয়। আমি নিজে ৩৫টি গলিত দেহ দেখেছি। আপাতদৃষ্টে মনে হয়, তারা চার-পাঁচ দিন আগে নিহত হয়েছেন। মৃতের সংখ্যা সম্ভবত আরো বেশি হবে। ঢাকায় অপহরণ করা এ ধরনের লোকের সংখ্যা অন্তত ১৫০ হতে পারে।
ইউপিআইয়ের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, নিহত ব্যক্তিদের মধ্যে ঢাকা মেডিকেল কলেজের প্রধান হৃদরোগ চিকিৎসক ফজলে রাব্বী ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের চেয়ারম্যান মুনীর চৌধুরী রয়েছেন। ঢাকার মধ্যবিত্ত এলাকা ধানমন্ডির বাইরে একটি ইটখোলাকে বধ্যভূমিতে পরিণত করা হয়েছে। যদিও কচুরিপানার নীল-সাদা ফুল কর্দমাক্ত জলাশয়ে শোভা পাচ্ছে।
স্থানটি লোকালয় থেকে বিচ্ছিন্ন। আজ ঢাকার শত শত মানুষ মাটির বাঁধ দিয়ে হেঁটে হেঁটে এখানে এসেছে, তাদের অনেকেই খুঁজে বেড়াচ্ছে নিরুদ্দিষ্ট স্বজনদের।
বিশিষ্টজনদের অপহরণ করে তুলে নেওয়ার ঘটনাটি ঘটেছে মঙ্গলবার সকালেই। পাঞ্জাবি সেনাদের কয়েকটি স্কোয়াড নির্দিষ্ট ঠিকানায় হাজির হয়ে নির্ধারিত পুরুষ ও নারীকে সশস্ত্র প্রহরায় উঠিয়ে নিয়ে এসেছে। তাদের সম্ভবত রায়েরবাজার ইটখোলায় এনে মাটির বাঁধের পাশে লাইন ধরে দাঁড় করিয়ে গুলি করেছে, যাতে তারা হুমড়ি খেয়ে নিচের জলাশয়ে পড়ে যান।
দেহগুলো এখনো সেখানে শায়িত, কাদা ও বালুতে মাখা, গলতে শুরু করেছে। ঢাকার কুকুরগুলো নাটকীয়ভাবে একটি দেহের কঙ্কাল তুলে এনে বাঁধের ওপর ফেলে রেখেছে। এই কাদার মধ্যেই বাঙালি জনতা অদ্ভুতভাবে শক্ত হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। দেখে মনে হচ্ছে না এখানে তারা ক্ষুব্ধ। কিন্তু অন্যত্র তারা ক্ষিপ্ত। এখানে তারা ঘুরে বেড়াচ্ছে, বিড়বিড় করে কথা বলছে, যেন তারা একটি গির্জা দেখতে আসা পর্যটক।
একটি জলাশয়ের পাশে সবচেয়ে বেশিসংখ্যক মানুষ, সেখানেই পাওয়া গেছে সবচেয়ে বেশি মৃতদেহের স্তূপ। একজন মুসলমান ব্যক্তি উলের মাফলারে মুখটা ঢেকে চিৎকার করে বিলাপ করছেন। মুয়াজ্জিনের তারস্বরে। আমরা তার নাম জিজ্ঞেস করলাম। বললেন, তিনি আবদুল মালেক, ঢাকার একজন ব্যবসায়ী। সামনের জলাশয়ে তিনি তার তিন ভাইকে শনাক্ত করতে পেরেছেন- বদরুজ্জামান, শাহজাহান ও মুল্লুক জাহান। তারা পাশাপাশি পড়ে আছেন। তারাও ঢাকার ব্যবসায়ী। তাদের ব্যবসা পারিবারিক। তার আর কোনো ভাই নেই।
আবদুল মালেক বলেন, পাকিস্তানি সেনাবাহিনী মঙ্গলবার ভোর ৭টায় এসে হাজির হয়। ঘটনাচক্রে আমি আগেই বেরিয়ে গিয়েছিলাম। তখন আমার সঙ্গী যুবকটিও কাঁদতে শুরু করেন। তার নাম নাজিউর রহমান, ঢাকার ছাত্র। তিনিই আমাকে এই ইটখোলায় নিয়ে এসেছেন। তিনি তার ভগ্নিপতিকে খুঁজছেন।
ড. আমিনুদ্দিন বেঙ্গল রিসার্স ল্যাবরেটরির প্রধান, অক্সফোর্ডের পিএইচডি। পাকিস্তানি সেনারা যখন তাকে তুলে নেয়, সেই মঙ্গলবার ভোর ৭টায় তাকে শেষবারের মতো দেখা যায়। নাজিউর রহমান বললেন, ‘আমি দুঃখিত, আমাকেও যেতে হচ্ছে, খুঁজে দেখি।’ ততক্ষণে তিনিও উলের মাফলার দিয়ে নাক-মুখ পেঁচিয়ে নিয়েছেন।
গতকাল আমি কেবল তিন ঘণ্টা ঢাকায় ছিলাম, ততক্ষণে ইটভাটার এই খবর তেমন ছড়ায়নি। জনতা উত্তেজিত, তবে আচরণে অদ্ভুত কোমলতা। ভারতীয় সেনাদের হাত নেড়ে অভিবাদন জানাচ্ছে, গাড়িতে এই প্রান্ত থেকে অন্য প্রাপ্ত পর্যন্ত যাচ্ছে, আবার ফিরে আসছে।
সেদিনও অনেক গোলাগুলি হয়েছে, বিশেষ করে, রাতের বেলায়। ইন্টারকন্টিনেন্টাল হোটেলে অবস্থানরত সাংবাদিকেরা জানিয়েছেন, পরিস্থিতি তখনো বিস্ফোরণোন্মুখ। বাঙালিরা অভিযোগ করছে, বিহারি এই বিদেশিরা বহু বছর আগে মুসলমান হিসেবে ঘাঁটি গেড়ে বসেছে, তারা বাঙালি হত্যাকাণ্ডে পাকিস্তানি সেনাসদস্যদের সাহায্য করেছে। আট মাস আগে আমি যখন যশোরে ছিলাম, এ কারণেই সেখানে বেসামরিক বিহারিদের হত্যা করা হয়। ঢাকায় বুদ্ধিজীবীদের হত্যাকাণ্ড যশোরের হত্যাকাণ্ডের চেয়ে শতগুণ বেশি ভয়াবহ একটি ব্যাপার। কাজেই এক ধরনের প্রতিশোধ গ্রহণের ব্যাপার অবশ্যম্ভাবী হয়ে উঠবে।
ইতোমধ্যে ভারতীয় সেনাবাহিনীর প্রহরায় সেনানিবাসে বন্দি পাকিস্তানি সেনারা এখনো সশস্ত্র, যদি প্রয়োজন পড়ে! ঢাকা যখন জেনে যাবে পাকিস্তানি সেনারা কত পরিকল্পিতভাবে এই হত্যাকাণ্ড চালিয়েছে, তখন দেখা দেবে সত্যিকারের সংকট। যা-ই ঘটুক, পরাজিত পাকিস্তানি সেনাদের জন্য সহানুভূতিপ্রবণ হওয়া বাঙালিদের জন্য ক্রমেই কঠিন হয়ে পড়ছে এ রকম একটি সুশৃঙ্খল সেনাবাহিনী এভাবে খেলাচ্ছলে অপ্রয়োজনে, উন্মত্তের মতো খুন করতে পারে, তা অবিশ্বাস্য।
যদি পাইকারি হত্যাকাণ্ডকে সংবাদপত্র গণহত্যা আখ্যায়িত করে, তা অবশ্যই ভয়ংকর; কিন্তু পরিকল্পিতভাবে বাছাই করে জাতির সবচেয়ে যোগ্য, বুদ্ধিমান ও গুরুত্বপূর্ণ পুরুষ ও নারী হত্যার মাধ্যমে যদি জাতির ভবিষ্যৎ ধ্বংস করে দেয়া হয়, সেই ‘এলিটোসাইড’- এলিট হত্যা যে আরো বেশি ভয়ংকর।
গত মঙ্গলবারের অনেক আগেই পাকিস্তান শেষ হয়ে গেছে। যেসব কর্মকর্তা এই পরিকল্পনা করেছেন, তারাও তা অবশ্যই জানেন। কাজেই হত্যাকাণ্ডের উদ্দেশ্য ছিল পাকিস্তানের সঙ্গে বাংলাদেশকেও ধসিয়ে দেয়া। বহুদিন ধরেই অনুমান করা হচ্ছিল, পাঞ্জাব মরুভূমির রুক্ষ সেনারা বাঙালিদের প্রতি হিংস্র বর্ণবাদী ঘৃণা লালন করে আসছে। এখন দেখা যাচ্ছে, তারা বুদ্ধিভিত্তিক ঈর্ষাও লালন করছে, যার প্রকাশ ঘটেছে এই ব্যাপক হত্যাকাণ্ডে।
দ্য সানডে টাইমস, ১৯ ডিসেম্বর ১৯৭১ (ঈষৎ সংক্ষেপিত)
সায়মন ড্রিং ডেইলি টেলিগ্রাফ

২৫ মার্চ ১৯৭১-এর ভয়াল ও নির্মম দৃশ্য যারা প্রত্যক্ষ করেছেন সেই বিদেশি সাংবাদিকরা যখন হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টালে কার্যত বন্দি এবং ঢাকা থেকে বহিষ্কৃত হওয়ার অপেক্ষায় তখন পাকিস্তানি মেজর সিদ্দিক সালিক এসে জানালেন তাদের জীবনের নিরাপত্তার কথা বিবেচনা করেই তাদের সরিয়ে দেয়া হচ্ছে। লন্ডনের ডেইলি টেলিগ্রাফের ২৬ বছর বয়সি সংবাদদাতা সায়মন ড্রিং মেজরকে জিজ্ঞেস করলেন, না গেলে কী হবে? মেজরের উত্তর, বিদ্রোহী বাঙালিরা হত্যা করবে। যখন হোটেলের লবিতে সাংবাদিকদের জড়ো করা হলো সায়মন তখন থেকে পালিয়ে যাওয়ার কৌশল খুঁজছেন।
বিদেশি সাংবাদিকদের যখন গাড়িতে তোলা হচ্ছে তিনি তখন হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টালের ছাদে এয়ার কন্ডিশনার প্লান্টের নিচে লুকিয়ে। মাঝেমধ্যে ওপর থেকে উঁকি দিয়ে দেখছেন সাংবাদিকদের গাড়ি ছেড়ে গেল কিনা।
গাড়িগুলো ছেড়ে যাওয়ার পরও আশঙ্কামুক্ত হলেন না। যখন গুনতিতে কম পড়বে কিংবা পত্রিকার নাম ধরে হাজিরা নেবে তার অনুপস্থিতির খবরটি ফাঁস হয়ে যাবে, তাকে ধরে নিতে সেনাবাহিনী আবার হাজির হবে।
গাড়ি ছাড়ার দেড় ঘণ্টা পর তিনি সিঁড়ি বেয়ে নেমে এলেন। রিসেপশনের বাঙালিরা তাকে দেখে বিষ্মিত। তিনি সরজমিন দেখে রিপোর্ট করবেন এবং তখনই বেরিয়ে পড়তে চাচ্ছেন। তারাই তাকে জানায়, আরো একজন বিদেশি সাংবাদিক সেনাবাহিনীকে ফাঁকি দিয়ে রয়ে গেছেন। সেই বিদেশি হচ্ছেন অ্যাসোসিয়েটেড প্রেসের ফটোগ্রাফার মিশেল লরেন্ট, (১৯৭২-এ পুলিৎজার বিজয়ী, ১৯৭৫-এর এপ্রিলে ভিয়েতনাম যুদ্ধের শেষ প্রান্তে সায়গনে নিহত)।
দুজন একসঙ্গে বেরোলেন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, পুরানো ঢাকার হিন্দু অধ্যুষিত এলাকা ঘুরে ছবি তোলার সময় টহলরত সেনাবাহিনীর চোখে পড়ে যান। তারপর অবস্থান পরিবর্তন করে কোনোভাবে বেঁচে গিয়ে যখন হোটেলে ফিরে আসেন জানতে পারেন সেনাবাহিনী অনুসন্ধান করতে এসেছিল।
রাতেও তারা দুবার আসে। কিন্তু নিরাপদ আশ্রয়ে থাকায় ধরা পড়েননি। তারপর আরো ঝুঁকি নিয়ে ছবি তুলে ও নোটখাতা ভর্তি বিবরণী লিখে ঢাকা ছাড়লেন; উদোম তল্লাশির পরও ধরা পড়লেন না, করাচি পৌঁছালেন যে কোনো সময় গ্রেপ্তার ও মৃত্যুর আশঙ্কা নিয়ে; সেখান থেকে ব্যাংকক পৌঁছে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললেন।
২৯ ও ৩০ মার্চ রক্তাক্ত ঢাকা নিয়ে তার বেশ কটি টেলিগ্রাফ প্রতিবেদন পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর হত্যাযজ্ঞ তুলে ধরে পৃথিবীকে জানিয়ে দিল।
ভিয়েতনাম যুদ্ধ কভার করার সময় সায়গনে থাকা অবস্থায় টেলিগ্রাফ হেডকোয়ার্টার্স থেকে নির্দেশ পেয়ে সায়মন ড্রিং ৬ জানুয়ারি ১৯৭১ ঢাকা আসেন।
৯ মাস পর আবার ফিরে আসেন এবং বাংলাদেশের স্বাধীনতা লাভ প্রত্যক্ষ করেন। ঢাকা ক্যান্টনমেন্টে যান এবং মেজর সিদ্দিককে বলেন, মার্চে যদি ধরা পড়তেন তাহলে কী হতো?
মেজর তেমন ভণিতা না করেই বললেন, সম্ভবত হত্যা করা হতো।
৭ মার্চ রেসকোর্সে বঙ্গবন্ধুর ঐতিহাসিক ভাষণ যারা খুব কাছ থেকে শুনেছেন, তিনি তাদের অন্যতম। ১০ জানুয়ারি বঙ্গবন্ধু যখন স্বদেশে ফিরলেন, সায়মন ড্রিং সেদিনও ঢাকায়, তার মনে হলো আন্দোলনের শুরু থেকে শেষ পরিণতি পর্যন্ত একটি বৃত্ত সম্পন্ন করেছেন।
সায়মন জন ড্রিং ১১ জানুয়ারি ১৯৪৫ দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের শেষ বছরে ইংল্যান্ডের নরফোক কাউন্টির বাজার শহর ফাকেনহামে জন্মগ্রহণ করেন। উডব্রিজ বোর্ডিং স্কুলে পড়তেন, কিন্তু মধ্যরাতে ডেবেন নদীতে সাঁতার কাটার অপরাধে স্কুল থেকে বহিষ্কৃত হন, তারপর কিংস লিন টেকনিক্যাল কলেজে।
১৭ বছর বয়সে বিশ্বভ্রমণে বাড়ি ছাড়লেন। ইউরোপ, মধ্যপ্রাচ্য, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া এবং ভারত ঘুরে ১৯৬৩ সালে ১৮ বছর বয়সে ব্যাংকক পোস্ট পত্রিকায় প্রæফ রিডারের চাকরি নিলেন, তারপর ফিচার রাইটার; ১৯৬৪ সালে ১৯ বছর বয়সে ডেইলি মেইল এবং নিউইয়র্ক টাইমসের ফ্রিল্যান্স কন্ট্রিবিউটর। ১৯৬৪-এর শেষে নিয়োগ পেলেন রয়টারের সর্বকনিষ্ঠ স্টাফ করেসপন্ডেন্ট, তার দায়িত্ব ভিয়েতনাম যুদ্ধ কভার করা।
১৯৭০, ১৯৮০ এবং ১৯৯০-এর দশকে তিনি রয়টার্স, ডেইলি টেলিগ্রাফ, সানডে টাইমস, নিউজউইক, বিবিসি রেডিও এবং বিবিসি টিভির হয়ে কাজ করেন। ক্রিস ল্যাঙ্গ ও স্যার বব গোল্ডফ-এর সঙ্গে প্রতিষ্ঠা করেন স্পোর্ট এইড, আফ্রিকার দুর্ভিক্ষপীড়িত মানুষের জন্য এর মাধ্যমে ৩৬ মিলিয়ন ডলার উত্তোলন করেন। বিবিসি টেলিভিশনে তার ২৯০০০ কিলোমিটার জিপ ও ল্যান্ড রোভার ভ্রমণের অভিজ্ঞতা নিয়ে উপস্থাপনা করেছেন ‘অন দ্য রোড এগেইন’।
১৯৯৭ সালে বাংলাদেশে টেলিভিশন নিউজ নেটওয়ার্ক সৃষ্টি ও একুশে টেলিভিশনে ব্যবস্থাপনা পরিচালকের দায়িত্ব পালন করেন। তার আগ্রহেই টেলিভিশন সাংবাদিকতার একটি নতুন পর্ব এখানে শুরু হয়। একাত্তরের বাংলাদেশ প্রতিবেদন তাকে করেছে ইউকে রিপোর্টার অব দ্য ইয়ার। বলিষ্ঠ সাংবাদিকতার জন্য আরও অনেক পুরস্কার তিনি লাভ করেছেন। ১৬ জুলাই ২০২১ একটি অপারেশন-উত্তর হার্ট অ্যাটাকে ৭৬ বছর বয়সে তার মৃত্যু হয়।
রণাঙ্গনে একাধিকবার আহত হয়েছেন। উগান্ডায় ইদি আমিনের আমলে তার মৃত্যুদণ্ড হতে পারত। তিনি পালিয়ে বেড়িয়েছেন। বাংলাদেশবান্ধব সায়মন ড্রিংকে বাংলাদেশ আনুষ্ঠানিকভাবে সম্মানিত করেছে।
ট্যাঙ্ক পাকিস্তানে বিদ্রোহ গুঁড়িয়ে দিয়েছে
ঢাকার প্রত্যক্ষদর্শী সায়মন ড্রিং-এর ব্যাংকক থেকে পাঠানো প্রতিবেদন :
[৩০ মার্চ ১৯৭১ ডেইলি টেলিগ্রাফে প্রকাশিত সায়মন ড্রিং-এর প্রতিবেদনটি ভাষান্তরিত করা হলো]
‘আল্লাহ এবং অখণ্ড পাকিস্তানের নামে।’
ঢাকা এখন বিধ্বস্ত ও আতঙ্কিত শহর। পাকিস্তানি সেনাবানিহীর টানা ২৪ ঘণ্টা শীতল মস্তিষ্কের নির্বিচার গোলাবর্ষণে ৭০০০ মানুষের হত্যাকাণ্ড ও বিশাল এলাকা গুঁড়িয়ে দেয়ার পর নির্মমভাবে পূর্ব পাকিস্তানের স্বাধীনতার লড়াই স্তব্ধ করা হয়েছে।
পাকিস্তানের সামরিক সরকারের প্রধান প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খানের দাবি, পরিস্থিতি এখন শান্ত, তা সত্ত্বেও হাজার হাজার মানুষ গ্রামের দিকে পালিয়ে যাচ্ছে, শহরের রাস্তাগুলো প্রায় পরিত্যক্ত এবং প্রদেশের অন্যান্য অংশে এখন হত্যাকাণ্ড অব্যাহত রয়েছে। তবে এতে কোনো সন্দেহ নেই ট্যাঙ্কের সমর্থনপুষ্ট সেনাবাহিনীই এখন প্রধান শহর প্রধান লোকালয় নিয়ন্ত্রণ করছে এবং প্রতিরোধ যৎসামান্য এবং এখন পর্যন্ত সে প্রতিরোধ অকার্যকর। তার পরও নামমাত্র প্ররোচনাতেই জনতার ওপর গুলিবর্ষণ করা হচ্ছে এবং কোনো বাছবিচার না করে ভবনগুলো ধ্বংস করা হয়েছে।
পাকিস্তানের পূর্বাংশের ৭ কোটি ৩০ লাখ বাঙালির ওপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার জন্য সেনাবাহিনীকে প্রতিদিনই আরো বেশি প্রতিশ্রæতিবদ্ধ বলে মনে হচ্ছে। কত নিরীহ মানুষের মৃত্যু হয়েছে ও ধ্বংসযজ্ঞে আসলে কত ক্ষতি হয়েছে তা নির্ধারণ করা অসম্ভব। চট্টগ্রাম, কুমিল্লা ও যশোর থেকে যে মৃত্যুর প্রতিবেদন পাওয়া যাচ্ছে তাতে ঢাকাসহ পূর্বাঞ্চলের মৃতের সংখ্যা ১৫০০০ বলে অনুমান করা হচ্ছে।
সামরিক অভিযানের ভয়াবহতা সঠিকভাবে আঁচ করতে হলে জানা দরকার হলের ছাত্ররা তাদের বিছানায় গুলিবিদ্ধ হয়ে নিহত, বাজারে দোকানের পেছনে দোকানিরা খুন হয়েছে, নারী ও শিশু তাদের ঘরে পুড়ে অঙ্গার হয়েছে, হিন্দু পাকিস্তানিদের বাড়ি থেকে বের করে নিয়ে লাইন ধরে হত্যা করা হয়েছে, বাজার ও দোকানপাট আগুনে পুড়িয়ে দেয়া হয়েছে, আর এখন রাজধানীর প্রতিটি ভবনের ওপর পাকিস্তানের পতাকা উড়ছে।
পাকিস্তানি সৈন্যের মৃত্যুর কোনো খতিয়ান পাওয়া যায়নি। তবে কমপক্ষে একজন নিহত ও দুজন আহত হয়েছে। অন্তত এ সময়ের জন্য হলেও বাঙালিদের অভ্যুত্থান সত্যিই শেষ হয়ে গেছে বলে মনে হচ্ছে। সেনাবাহিনীর হাতে শেখ মুজিবুর রহমানকে গ্রেপ্তার হতে দেখা গেছে। আওয়ামী লীগের জ্যেষ্ঠ নেতারাও আটক হয়েছেন।
জ্যাক এন্ডারসন
সংবাদ বিশ্লেষক

জন্ম ক্যালিফার্নিয়ার লংবিচ, ১৯ অক্টোবর ১৯২২। ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধ ও বাংলাদেশের স্বাধীনতা নিয়ে হোয়াইট হাউস ও স্টেট ডিপার্টমেন্টের ভেতরের খবর প্র্রকাশ করে তিনি চাঞ্চল্য সৃষ্টি করেছিলেন। ইউনাইটেড ফিচার সিন্ডিকেটের কলামিস্ট হিসেবে তিনি এ চাঞ্চল্য সৃষ্টি করা সংবাদের জন্য সাংবাদিকতায় ১৯৭২ সালের পুলিৎজার পুরস্কার পান। তিনি এবিসি টেলিভিশনের ‘গুড মর্নিং আমেরিকা’ অনুষ্ঠানে নয় বছর সংবাদ বিশ্লেষণ করেছেন। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় আমেরিকান সৈন্যবাহিনীর সদস্য হিসেবে চীনে মোতায়েন ছিলেন এবং জাপানের বিরুদ্ধে প্র্রত্যক্ষ যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছেন। তিনি তার সময়ের সবচেয়ে প্র্রভাবশালী মার্কিন কলামিস্ট হিসেবে সমাদৃত ছিলেন, বিশ্বব্যাপী প্র্রায় এক হাজার ইংরেজি পত্রিকায় তার সিন্ডিকেটেড কলাম প্র্রকাশিত হতো।
১৯৭১-এর ডিসেম্বরের প্র্রতিবেদন জ্যাক এন্ডারসনকে এনে দিয়েছে সাংবাদিকতার জন্য পুলিৎজার পুরস্কার। ইউনাইটেড ফিচার সিন্ডিকেটের প্র্রতিবেদক ও কলাম লেখক জ্যাক এন্ডারসনের যে প্র্রতিবেদনগুলো বিবেচনায় আনা হয়েছে, সেগুলো মূলত ১৯৭১-এর ডিসেম্বর যুদ্ধ নিয়ে, যার পরিণতি বাংলাদেশের স্বাধীনতা। জ্যাক নর্থম্যান এন্ডারসন (১৯ অক্টোবর ১৯২২-৭ ডিসেম্বর ২০০৫) অনুসন্ধানী-প্র্রতিবেদকদের গুরু। অনেক ঘটনার ব্রেকিং নিউজ তার হাতেই তৈরি হয়েছে। প্রেসিডেন্ট নিক্সন ও সিআইএ প্রধান তাকে খুব অপছন্দ করতেন। তিনি ছয়টি ফিকশন সাতটি নন-ফিকশন গ্রন্থেরও প্র্রণেতা। এক পর্যায়ে তার প্র্রতিবেদন ও কলাম প্র্রায় একহাজার সংবাদপত্রে ছাপা হতো। প্রেসিডেন্ট নিক্সন এবং ওয়াটারগেট বার্গলার গর্ডন লিভি তাকে খুন করতে চেয়েছেন। জ্যাক এন্ডারসনের সাড়া জাগানো ডিসেম্বর প্র্রতিবেদনের কয়েকটি অনূদিত হলো।
১৩ ডিসেম্বর ১৯৭১
বঙ্গোপসাগরে যুক্তরাষ্ট্র ও সোভিয়েত রণতরী
বঙ্গোপসাগরে সোভিয়েত ও যুক্তরাষ্ট্রের নৌশক্তির মুখোমুখি হওয়ার পরিণতি হবে ভয়ংকর। ভারতকে নিরস্ত্র করার জন্য প্রেসিডেন্ট নিক্সন নৌ-টাস্কফোর্সকে ঝামেলার দিকে ঠেলে দিয়েছেন।
বিমানবাহী জলযান এন্টারপ্র্রাইজ বঙ্গোপসাগরের দিকে এগোচ্ছে, সঙ্গে আছে উভচর যান ত্রিপোলি, গাইডেড মিসাইল ফ্রিগেট কিং, গাইডেড মিসাইল ডেস্ট্রয়ার তিনটি-পার্সন, ডেকাটুর এবং টার্টার স্যাম।
একই সঙ্গে স্পষ্টতই ভারতকে সাহায্য করার জন্য বঙ্গোপসাগরের দিকে সোভিয়েত যুদ্ধজাহাজকে এগিয়ে আসতে দেখা যাচ্ছে। গোয়েন্দা প্র্রতিবেদন থেকে আরো অমঙ্গলজনক খবর পাওয়া গেছে-ভারতীয় নৌবাহিনীর জাহাজে সোভিয়েত টেকনিশিয়ান রয়েছে, সে জাহাজ পাকিস্তানি বন্দর এবং সংলগ্ন স্থাপনার ওপর আক্রমণ চালিয়েছে।
যুক্তরাষ্ট্র ও ব্রিটেনসহ অন্যান্য দেশের বাণিজ্যিক জাহাজও আক্রান্ত হয়েছে, সমুদ্রতল থেকে উৎক্ষিপ্ত রকেটও শনাক্ত হয়েছে। সোভিয়েত সাবমেরিন থেকে রকেট নিক্ষেপ করা হয়েছে কিনা তা জানতে যুক্তরাষ্ট্র আশু সাহায্য চেয়েছে।
এদিকে হোয়াইট হাউসের অভ্যন্তরে পাকিস্তানের ব্যাপারে প্রেসিডেন্ট নিক্সনের পক্ষপাত লুকোবার আর কোনো চেষ্টা করা হচ্ছে না।
পাকিস্তানের ‘ডিনামিক’ প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খানের সঙ্গে তিনি ঘনিষ্ঠ ব্যক্তিগত সম্পর্ক গড়ে তুলেছেন।
ওয়াশিংটন স্পেশাল অ্যাকশন গ্রুপ নামে পরিচিত তার সংকটকালীন সহায়তা দলকে সরাসরি হস্তক্ষেপের মাধ্যমে পাকিস্তানকে সাহায্য করার পথ বের করতে তিনি বলেছেন। প্র্রেসিডেন্টের নীতিনির্ধারক হেনরি কিসিঞ্জার ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধ শুরু হওয়ার পর থেকেই হোয়াইট হাউসের গল্পকথার গোপন ‘সিচুয়েশন রুমে’ প্র্রায় প্র্রতিদিনই সভা করছেন।
১৫ ডিসেম্বর
যুক্তরাষ্ট্রের কারণে ভারত সোভিয়েত কব্জায় চলে যাচ্ছে
আমরা আরও প্র্রমাণ পেয়েছি দৃশ্যত পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খানের সঙ্গে প্রেসিডেন্ট নিক্সনের ব্যক্তিগত সম্পর্কের কারণেই ভারতকে সোভিয়েত বলয়ের অধীনে চলে যেতে বাধ্য করছে।
জনসংখ্যার দিক দিয়ে ভারত কেবল পৃথিবীর দ্বিতীয় বৃহত্তম দেশই নয় এ দেশের গণতান্ত্রিক সরকার স্বাভাবিক কারণেই দেশটিকে যুক্তরাষ্ট্রের মিত্রে পরিণত করছিল, কিন্তু নিক্সন যা করছেন তাতে দক্ষিণ-পশ্চিম এশিয়ায় ঢুকে পড়ার যে রুশ-স্বপ্ন তা বাস্তবায়িত হতে চলেছে।
স্বাধীন বাংলাদেশ একটি আন্তর্জাতিক ভিক্ষার ঝুড়িতে পরিণত হবে, এটা হেনরি কিসিঞ্জারের কথা নয়, এটা বলেছেন অ্যাম্বাসেডর-এট-লার্জ অ্যালেক্সিস জনসন
পেছনমঞ্চে যা কিছু ঘটছে নিক্সন প্র্রশাসন তার ওপর সেন্সরশিপ পর্দা টাঙিয়ে দিয়েছে। কিন্তু যেহেতু যুক্তরাষ্ট্রে সেন্সরশিপ সহ্য করা হবে না হোয়াইট হাউস গোপনীয়তার লেবেল সেটে বিব্রতকর অনেক কিছু সরিয়ে ফেলেছে। কিন্তু আমরা সেন্সরশিপ ভেঙে ফেলেছি, নিক্সনের দ্বৈত চেহারা আমরা তুলে ধরতে পারি।
নিক্সনের ব্যক্তিগত নীতিপ্র্রণেতা হেনরি কিসিঞ্জার গত সপ্তাহের একটি প্র্রস্তুতিমূলক বৈঠকে সাংবাদিকদের আশ্বস্ত করেছেন যে, নিক্সন প্র্রশাসন ভারতের বিরুদ্ধাচারী নয়। প্র্রশাসন ভারত-বিরোধী বলে কোথাও কোথাও মন্তব্য করা হয়েছে যা মোটেও যথার্থ নয়।
হোয়াইট হাউস সিচুয়েশন রুমের কঠিন প্র্রহরাধীন দরজার অন্তরালে অবশ্য কিসিঞ্জারের ভিন্ন চেহারা আর ভিন্ন সুর। ৩ ডিসেম্বর যেসব ঊর্ধ্বতন পরিকল্পনাকারী বৈঠকে যোগ দিয়েছেন তিনি তাদের কর্মকৌশল নির্ধারণ করতে বলেছেন ‘প্র্রতি আধঘণ্টা পরপর প্রেসিডেন্ট একবার করে আমাকে এক হাত নিচ্ছেন যে আমরা ভারতের ব্যাপারে যথেষ্ট কঠোর ভূমিকা পালন করছি না।’ 
পিটার কান
দ্য ওয়াল স্ট্রিট জার্নাল

পিটার আর কান একজন প্রথিতযশা আমেরিকান সাংবাদিক, সম্পাদক ও ব্যবসায়ী। সাংবাদিকতার জন্য ১৯৭২ সালের পুলিৎজার পুরস্কার বিজয়ী। তার জন্ম ১৯৪২ সালে আমেরিকার নিউ জার্সির প্রিন্সটনে, একটি ইহুদি পরিবারে। তিনি হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র, সাংবাদিকতায় স্নাতক।
১৯৬৩ সালে ওয়াল স্ট্রিট জার্নালের সানফ্রান্সিসকো ব্যুরোতে যোগ দেন। ১৯৬৭ থেকে ১৯৭৫ পর্যন্ত তিনি ওয়াল স্ট্রিট জার্নালের হংকং অফিসে দায়িত্ব পালন করেন। তিনি একই সঙ্গে ভিয়েতনামে পত্রিকার রেসিডেন্ট রিপোর্টারও ছিলেন। এশিয়ার অন্যান্য প্রধান ঘটনার অনেক প্রতিবেদন তার তৈরি।
১৯৭১ সালে তিনি ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধ কাভার করার জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত ছিলেন। সে সময় তিনি ঢাকায় অবস্থান করেন এবং যুদ্ধের কারণে রিপোর্ট পাঠাতে না পারায় ঢাকা ডায়েরি লেখেন, যা পরে প্রকাশিত হয় এবং পিটার কানকে এনে দেয় পুলিৎজার পুরস্কার। ১৯৭৬ সালে তিনি দ্য ওয়াল স্ট্রিট জার্নাল এশিয়ার সম্পাদক ও প্রকাশক নিযুক্ত হন এবং ১৯৮৮ থেকেই তিনি মূল ওয়াল স্ট্রিট জার্নালের প্রকাশক।
১৯৯২ থেকে ২০০৬ পর্যন্ত তিনি বিখ্যাত ডাউজোন্স অ্যান্ড কোম্পানির প্রধান নির্বাহী ও চেয়ারম্যান হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকতাও করেন। ডাউজোন্স অ্যান্ড কোম্পানির প্রসারের কৃতিত্ব যেমন তাকে দেয়া হয়, আর্থিক ধসের জন্যও পিটার কানকে দায়ী মনে করা হয়।
পিটার কানের এপ্রিল ১৯৭১
একাত্তরের বাংলাদেশ নিয়ে ওয়াল স্ট্রিট জার্নালে প্রকাশিত ঢাকা ডায়েরি পিটার কানকে এনে দিয়েছে ১৯৭২ সালের পুলিৎজার পুরস্কার। তার জন্ম ১৯৪২ সালে আমেরিকার নিউ জার্সি অঙ্গরাজ্যের প্রিন্সটন শহরে একটি ইহুদি পরিবারে। হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সাংবাদিকতায় স্নাতক ডিগ্রি নিয়ে তিনি ওয়াল স্ট্রিট জার্নাল পত্রিকায় সানফ্রান্সিসকো ব্যুরোতে যোগ দেন। ১৯৭১-এ তিনি ওয়াল স্ট্রিটের উপমহাদেশের প্রতিনিধি ছিলেন। বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রাম এবং বাংলাদেশের অভ্যুদ্বয়ের তিনি অন্যতম সাক্ষী। ১৯৬৭ সালে পিটার কান ভিয়েতনাম যুদ্ধের প্রতিবেদন দেয়ার জন্য সেখানে প্রথম রেসিডেন্ট রিপোর্টার নিয়োজিত হন। পরবর্তীকালে তিনি ওয়াল স্ট্রিট জার্নাল এশিয়ার সম্পাদক; ১২ বছর এ দায়িত্ব পালনের পর যুক্তরাষ্ট্রে ফিরে যান জার্নালের প্রকাশক এবং ডাউ জোন্স ইন্ডাস্ট্রিয়াল এভারেজের চেয়ারম্যান হন।
তার স্ত্রী ক্যারেন এলিয়ট হাউস (জন্ম ১৯৪৭) একই পত্রিকার সাংবাদিক ছিলেন, মধ্যপ্রাচ্য নিয়ে সাংবাদিকতায় তিনিও ১৯৮৪ সালের পুলিৎজার পেয়েছেন।
২১ এপ্রিল ওয়াল স্ট্রিট জার্নালে প্রকাশিত তার প্রতিবেদন ‘পূর্ব পাকিস্তানিরা আমৃত্যু লড়াই করতে তারা প্রতিশ্রæত’ ভাষান্তর করে উপস্থাপন করা হচ্ছে :
স্বাধীনতা পথ দীর্ঘ
এ কথার মানে এই নয় যে বাংলাদেশ সৃষ্টির স্বপ্ন শেষ হয়ে গেছে। গত চার সপ্তাহ বিপ্লবের যে স্বতঃস্ফূর্ত বিস্ফোরণ ঘটছে কেবল তার মাধ্যমে স্বাধীনতা অর্জন করা যাবে না। স্বাধীনতা অর্জন কয়েক সপ্তাহে হয় না, বছরের পর বছর লেগে যাবে, বক্তৃতা নয়, অনেক বেশি লড়াই লাগবে- গেরিলা কৌশলের লড়াই, প্রচলিত যুদ্ধ নয় আর সম্ভবত সে জন্য লাগবে জঙ্গি বামপন্থি, আদর্শবাদী মধ্যপন্থি নয়।
অনেক বেশি নির্ভর করবে ভারতের ওপর- তারা অস্ত্র সহায়তা এবং দীর্ঘমেয়াদি একটি যুদ্ধের জন্য সীমান্ত আশ্রয় দেবে কিনা তার ওপর নির্ভর করবে।
যাই ঘটুক পশ্চিম পাকিস্তানকে গভীর সমস্যার মোকাবিলা করতে হচ্ছে। প্রধানত বিশাল গ্রামাঞ্চল এবং বর্ষা মৌসুম এসে যাচ্ছে। এ সময় দখল বজায় রাখার জন্য সেনা মোতায়েন কেমন করে করবে তা তাদের দুশ্চিন্তার বিষয়। তিক্ততার বিজয় দিয়ে উপনিবেশ তারা কেমন করে চালাবে, ছিন্নভিন্ন হয়ে যাওয়া পূর্ব পাকিস্তানের অর্থনীতি, কেমন করে জোড়া লাগবে, কেমন করে পশ্চিম পাকিস্তানের সীমিত সম্পদ দিয়ে এই উপনিবেশ টিকিয়ে রাখবে? বাঙালিদের প্রতিরোধের আন্দোলনে ভারত যদি আরো নিবিড়ভাবে জড়িয়ে পড়ার সিদ্ধান্ত নেয় তাহলে তারা কেমন করে সামাল দেবে?
যদি পশ্চিম পাকিস্তানেও সংখ্যালঘু জাতিগোষ্ঠীর আন্দোলন ও অস্থিরতা পরিস্থিতিকে আরো জটিল করে ফেলে এবং প্রতিদ্ব›দ্বী জেনারেল ও বিরোধী দলগুলো যদি তাদের সঙ্গে যোগ দেয় এই সংকট মোকাবিলা করা পশ্চিম পাকিস্তানের পক্ষে কঠিন হয়ে পড়বে।
আমরা মরতে প্রস্তুত
একজন রাজনীতিবিদ শপথ নেয়া আন্তরিক বক্তৃতায় বললেন, বাইরের পৃথিবী বাংলাদেশের কাজে আসতে ব্যর্থ হয়েছে, অন্যজন জিজ্ঞেস করলেন আর্মি ঠেকাতে পরিকল্পনা কী? জবাব এলো প্রয়োজনে আমরা মরব, অন্যরা মাথা নাড়ল। কিন্তু পরের দিনই পাকিস্তানি সৈন্যরা বিনা বাধায় চুয়াডাঙ্গা শহরের ভেতর ঢুকে পড়ল।
বাংলাদেশের পক্ষ থেকে তাদের সহায়তায় আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের এগিয়ে না আসার কথা শোনানো হচ্ছে। তাদের এই চাওয়া সরল বলে মনে হতে পারে, তবে বাস্তববাদী মানুষও পৃথিবীর নিষ্পৃহতায় হতাশ হয়েছে।
পাকিস্তানের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ আক্রান্ত হওয়ার পরই স্বাধীনতার লড়াই শুরু করেছে। হত্যাকাণ্ড বন্ধ করতে পাকিস্তানকে চিঠি দিয়ে রাশিয়া বাংলাদেশকে কিছুটা মৌখিক সমর্থন জুগিয়েছে। আর যুদ্ধের প্রস্তাবক চীন পাকিস্তানকে বড় গলায় সমর্থন দিয়ে যাচ্ছে। পাকিস্তানের প্রতিবেশী এবং শত্রæ ভারতই একমাত্র দেশ যে বাংলাদেশকে মৌখিক সমর্থন দিচ্ছে, সীমান্তে আনুষ্ঠানিকভাবে সীমিত সহায়তা পাঠাচ্ছে বাংলাদেশের মানুষ ও বাহিনীকে সাময়িকভাবে হলেও আশ্রয় দিয়েছে। ভারত কূটনৈতিক প্রক্রিয়ায় সহায়তা এবং সংঘটিত সামরিক সহায়তায় এগিয়ে আসছে।
এখন পর্যন্ত ভারত ও পাকিস্তান দুই পক্ষই পরস্পরের বিরুদ্ধে তিক্ত অভিযোগ আনলেও সত্যিকারের মুখোমুখি হওয়া এড়িয়ে যেতে চাচ্ছে বলেই মনে হয়। কিন্তু তারা যদি এই সতর্কতা বজায় না রাখে তাহলে পূর্ব পাকিস্তানের নৈরাজ্য উপমহাদেশকে গিলে খাবে।
ভারতীয় সীমান্ত থেকে অল্প ভেতরে গত শনিবার (১৭ এপ্রিল ১৯৭১) মুজিবনগরের আমবাগানে বাংলাদেশের অস্থায়ী সরকার সংবাদ মাধ্যমের সামনে উপস্থাপন করা হয়েছে, স্বাধীনতার ঘোষণা পাঠ করা হয়েছে, বক্তারা দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ ভাষণ দিয়েছেন। এই গৌরব দ্রুত কমে আসতে শুরু করেছে, উৎসবের পরের দিনই কয়েক ডজন অধিবাসী ছাড়া গোটা গ্রামই জনশূন্য হয়ে গেছে। সেই আমবাগানের নিচে সন্ধ্যা আগের মতো স্থির হয়ে আছে, কেবল কিছু মুরগি এবং একটি রাজহাঁস ঘুরে বেড়াচ্ছে।
গৌরবের স্মৃতি রয়ে গেছে। সীমান্তের ভারতীয় দিকে বাংলাদেশি কর্মকর্তা আগের দিনের গৌরবের স্বপ্ন নিয়ে মজে আছে- সাতজন মন্ত্রী, সাতাশজন সাক্ষী, সুন্দর ভাষণ, চমৎকার উৎসব।
জন উডরাফ
দ্য বাল্টিমোর সান

বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে যোদ্ধাদের অস্ত্র ও গোলাবারুদের ঘাটতি থাকলেও এ অভাব পূরণ করে দিয়েছে জাগ্রত বিশ্ববিবেক এবং বিদেশি সব গণমাধ্যম। এশিয়া, ইউরোপ, উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকায় বিভিন্ন দেশের জাতীয় পত্রিকাগুলোর স্থানে স্থানীয় ও আঞ্চলিক পত্রিকাগুলোকে পাল্লা দিয়ে পূর্ব পাকিস্তানে জনগণের দেয়া ম্যান্ডেটের কথা বলেছে, সামরিক বাহিনীর নির্যাতনের কথা বলেছে এবং বাংলাদেশের স্বাধীনতা যে অবশ্যম্ভাবী সে কথাও জোর দিয়ে বলেছে। এমনি একটি আঞ্চলিক পত্রিকা যুক্তরাষ্ট্রের ম্যারিল্যান্ড অঙ্গরাজ্যের দ্য বাল্টিমোর সান। জন উডরাফের মতো সত্যনিষ্ঠ একজন সাংবাদিকের কারণেই বাল্টিমোর সানের পাতায় গুরুত্বেও সঙ্গে ছাপা হয়েছে একাত্তরের বাংলাদেশ কাহিনী। ঢাকা থেকে বহিষ্কৃত বিদেশি সাংবাদিকদের অন্যতম জন ই উডরাফ।
ঢাকা থেকে বহিষ্কৃত বিদেশি সাংবাদিকদের অন্যতম জন ই উডরাফ। এই মেধাবী মানুষটির জন্ম যুক্তরাষ্ট্রের মিশিগানের গ্রিনভিল উপশহরে, উইলিয়ামস কলেজ থেকে ইতিহাসে স্নাতক হয়ে সঙ্গে সঙ্গেই সপ্তাহে ৭৫ ডলার বেতনে ম্যাসাচুসেটস-এ উইলিয়ামসন নিউজে চাকরি নেন। ১৯৬৫ সালে বাল্টিমোর সান-এ যোগ দেন, অনুসন্ধিৎসা ও লেখার শক্তিতে শিগগিরই অনেককে ডিঙ্গিয়ে ১৯৬৯ সালে ভিয়েতনাম যুদ্ধ কাভার করার দায়িত্ব নিয়ে ইন্দোচিনে আসেন, ১৯৭০ সালে তাকে হংকংয়ের ব্যুরো চিফ করা হয়, ১৯৭১-এর মার্চে তিনি ঢাকায়।
১৯৭৫-এ সদর দপ্তরে ফিরে যান, প্রথমে ডেপুটি এডিটর, পরে উইকঅ্যান্ড এডিটর ও স্পেশাল প্রোজেক্ট ডিরেক্টও হন। ১৯৮২ থেকে ১৯৮৭ কাটান বেইজিংয়ে এবং চীনের আর্থরাজনৈতিক পরিবর্তন নিয়ে দুটো গ্রন্থ রচনা করেন। ১৯৯৫ সালে মাত্র ৫৭ বছর বয়সে মূত্রাশয়ের ক্যান্সারে তিনি মুত্যুবরণ করেন।
১৮৩৭ সালের ১৭ মে বাল্টিমোর সান পত্রিকাটির প্রথম প্রকাশ। তখন ট্যাবলয়েড আকৃতির পত্রিকাটি প্রকাশিত হয় ২১ লাইট স্ট্রিট থেকে, মূল্য ১ পেনি। ১৯০৪ সালের গ্রেট বাল্টিমোর ২১ লাইট স্ট্রিটের পাঁচ তলা লৌহ খিলানের ভবনটি ভস্মীভূত হয় দ্য গ্রেট ফায়ারে। বহু ঠিকানা বদলে ১৯৫০ সালে পত্রিকাটির অফিস স্থাপিত হয় নিজস্ব জমিতে বাল্টিমোর শহরের ৫০১ নর্থ ক্যালভার্ট স্ট্রিটে। পত্রিকাটির প্রচার সংখ্যা দুই লাখ দশ হাজার আর রোববারে সাড়ে তিন লাখ।
আঞ্চলিক পত্রিকা হলেও দ্য বাল্টিমোর সান ঐতিহ্য ও কৌলীন্যে বিখ্যাত লেখক ও সাংবাদিকদের আকৃষ্ট করেছে। লেখক তালিকায় রয়েছেন, রাসেল বেকার, রিচার্ড ক্র্যামার, জন ক্যারোল, এডমন্ড ডাফি, থোমাস ফ্ল্যানারি, জেরাল্ড জনসন, ফ্র্যাঙ্ক কেন্ট, লরা লিপম্যান, থোমাস ও’নেইল, ডেভিড সিমন, মার্ক ওয়াটসন প্রমুখ।
১৯৭১-এর বাংলাদেশকে এই পত্রিকাটি মানবিক ছোঁয়া দিয়ে পৃথিবীর সামনে তুলে ধরেছে। ২৫ মার্চের পাকিস্তানি আগ্রাসনের কথা সবার আগে যে দু-একটি বিদেশি পত্রিকা বিস্তারিতভাবে প্রকাশ করতে পেরেছে বাল্টিমোর সান তার অন্যতম।
প্রতারণার পরিকল্পনা
ক্ষমতা হস্তান্তর দেরি করিয়ে দেবার জন্যই যে আলোচনা এমন সিরিয়াস মন্তব্য এটাই প্রথম নয়। ক্ষমতাসীনদের সঙ্গে নিবিড় যোগাযোগ রয়েছে এমন একজন সফরকারী সেনা অভিযানের এক সপ্তাহ আগে করাচি থেকে ঢাকা এসে এমন কথা বললেন যে, সাংবাদিকরা অবাক হয়ে গেলেন।
তিনি বললেন, অত্যন্ত বিশ্বস্ত হিসেবে পরিচিত দুজন সেনাবাহিনীর জেনারেল তাকে বলেছেন- আলোচনার নামে বাঙালি নেতাদের মধ্যে সাফল্যের বিশ্বাস সৃষ্টি করা হবে, তারপর একসময় বিনা সতর্কীকরণে সেনা আক্রমণ চালানো হবে।
এ নিয়ে সে সময় আমাদের কেউ কিছু লিখেনি কারণ এই কথার পক্ষে নির্ভরযোগ্য সমর্থন আমরা পাইনি। নির্বাচিত বেসামরিক প্রতিনিধিদের ক্ষমতা হস্তান্তরে ইয়াহিয়ার যে ঘোষিত সদিচ্ছা তিনি তার ব্যত্যয় ঘটাবেন এ ধারণা পোষণ করতে কেউ তৈরি ছিলেন না। সেনাবাহিনীর একেবারে সুনির্দিষ্ট ইচ্ছে কি তা জোর দিয়ে বলা যাচ্ছে না, কিন্তু গত বৃহস্পতিবারের (২৫ মার্চ) ঘটনা যারা সরাসরি দেখেনওনি তারাও আস্থার সঙ্গে বলতে পারেন পুরো ব্যাপারটাই আগে থেকে পরিকল্পিত।
শহরের বাইরে সেনাবাহিনী ও বেসামরিক জনগণের সংঘর্ষের কারণে শনিবার (২৭ মার্চ) শেখ মুজিব যে সাধারণ ধর্মঘটের ডাক দিয়েছেন বৃহস্পতিবার রাতে তা সংবাদিকদের পড়ে শোনানো হয়েছে।
প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া তার অস্ত্রে সুরক্ষিত ভবন ত্যাগ করেছেন। তার এবং ভুট্টোর উপদেষ্টাদের বৈঠকের পর তার হাতে ব্যাগ গোছাবারও সময় ছিল না। এ সময় একজন বাঙালি সাংবাদিক বললেন, তিনি প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়াকে চলে যেতে দেখেছেন।
সন্ধ্যা ৭টা নাগাদ সৈন্যরা হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টালের লিফটে একবার উপরে উঠছেন, নিচে নামছে- এগারো তলায় উঠছে। ভুট্টোর জায়গাটাকে একটি দুর্গ বানিয়ে ফেলেছেন- লবিতে বসানো আধ ডজন অটোমেটিক রাইফেল- মিনিটে দুজন করে উপরে উঠছেন।
প্রায় একঘণ্টা ধরে এই চর্চা অব্যাহত থাকল। সৈন্যদের একটি বড় দল লোহার পাত লাগানো কালো কার্ডবোর্ডের স্যুটকেস নামিয়ে নিয়ে এলো, কুড়িজন বা কাছাকাছি সংখ্যক সৈন্যের হেফাজতে তা দিয়ে দিল। সৈন্যদল রওনা হলো প্রেসিডেন্ট হাউসের দিকে, যেখানে কিছুসংখ্যক গার্ড এখনো প্রহরারত।
কালো স্যুটকেসে কি ছিল জানা যায়নি।
উৎফুল্ল জনতা রাস্তায় নেমে এসেছে
৭ ডিসেম্বর, যশোর, পূর্ব পকিস্তান
উৎফুল্ল জনতা বাংলাদেশ স্লোগান দিয়ে বিজয়ী ভারতীয় বাহিনীকে অভিনন্দন জানাতে দলে দলে রাস্তায় নেমে এসেছে।
লাল-সবুজ-সোনালি বাংলাদেশ পতাকা, যা এতদিন লুকিয়ে রেখেছিল, তা ওড়াতে ওড়াতে তারা বাড়ি থেকে আবির্ভূত হয়েছে; পাকিস্তানি সেনারা বাড়ি আসবে এই আতঙ্কে যেসব নারী ধান ড়্গেেতর গভীরে লুকিয়েছিল, তারাও ফিরে এসেছে।
একটি আচমকা ধাক্কাতেই সেখানকার পাকিস্তানি বাহিনীকে টুকরো টুকরো করে ভেঙে দিলে তাদের পালিয়ে যেতে হয়। ট্যাংক ও সাঁজোয়া গাড়ি সশব্দে অধিকাংশ তালাবন্ধ, শাটার নামানো দোকানের সামনে দিয়ে চলে যায়।
পাগড়িবাঁধা শিখ এবং বাদামি মুখমণ্ডলের গোর্খা রাইফেলধারীরা জনতার সঙ্গে মিশে গিয়ে সানন্দে তাদের নেতৃত্ব দিয়ে তাদের স্লোগান ‘জয় বাংলা’ দিতে থাকে।
যশোরে যারা বেঁচে আছেন, শেষ পর্যন্ত একটি স্বাধীন বাংলাদেশ পাওয়া ছিল তাদের লালিত স্বপ্নের চেয়েও বেশি।
রাস্তায়ও মুক্তিবাহিনী, জাতীয়তাবাদী গেরিলা, যারা আট মাস ধরে প্রেসিডেন্ট এ এম ইয়াহিয়া খানের সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে নাশকতামূলক কাজ এবং অ্যামবুশ করে তাদের বিরুদ্ধে লড়ে গেছে।
তাদের কাঁধে ঝুলছে ভারতের সরবরাহ করা আধুনিক স্বয়ংক্রিয় রাইফেল; তাদের গোপন ক্যাম্পে জঙ্গলে কিংবা কলার বনে রয়েছে মর্টার এবং লাইট মেশিনগান।
যশোর যুদ্ধে তাদের ভূমিকা কম থাকলেও তাদের হাঁটার ভঙ্গি ছিল সদম্ভ- তারা বিজয়ের এ দিনটিকে উপভোগ করছে।
ভারতীয় মেজর জেনারেল দলবীর সিং, যার বাহিনী যুদ্ধ করে এই শহর জয় করেছে তিনি বললেন, যদি পাকিস্তানি বাহিনী মাথা খাটিয়ে যুদ্ধে নামত, তাহলে আমাদের এক মাস ধরে যুদ্ধ করতে হতো।
ভারতীয় নবম ডিভিশনের কমান্ডার জেনারেল সিং বলেন, একটি ট্যাংক ঠেকানো পরিখা এবং ছোট ম্যাজিনট লাইন (প্রতিরোধক ব্যবস্থা) থাকলেও তার বাহিনী প্রায় বাধাহীনভাবেই শহরে ঢুকতে পেরেছে।
কলকাতায় সেনাবাহিনীর মুখপাত্র যশোর জয়ের যে বিবৃতি দিয়েছেন, তার সঙ্গে জেনারেল সিংয়ের কথার মিল খুঁজে পাওয়া যায় না। মুখপাত্র বলেছেন, যশোরে পাকিস্তানি বাহিনীর সঙ্গে তাদের তীব্র লড়াই হয়েছে।
যেটুকু লড়াই হয়েছে, তার সবটাই শহরের বাইরে। জেনারেল সিং বলেছেন, পাকিস্তানি সৈন্যরা এপ্রিল থেকে লড়াই করে আসছে, তবুও তারা যথেষ্ট অসংঘটিত।
কোনো কোনো বাড়ির ওপর শেলের আঘাত লেগেছে। এছাড়া যশোরের অতি সামান্যই ক্ষতি হয়েছে।
‘আমি তাদের কজনকে এক জায়গায় পেয়ে গেছি, বাকিদেরও পালানোর কোনো সুযোগ নেই’- জেনারেল দলবীর সিং বললেন, ‘আমি তাদের কাউকে হত্যা করতে চাই না, কেবল ধরতে চাই। আমি ভদ্র প্রকৃতির মানুষ।’ (বাল্টিমোরের ‘দ্য সান’-এ প্রকাশিত)
ডেভিড লোশাক
ডেইলি টেলিগ্রাফ

৫ এপ্রিল ২০২১ একাত্তরের বাংলাদেশবান্ধব ব্রিটিশ সাংবাদিক ডেভিড লোশাক ৮৭ বছর বয়সে প্রয়াত হলেন। বাংলাদেশের কোনো পত্রিকায় এই সংবাদটি আমি দেখিনি।
একাত্তরের আনসাঙ্গ ফ্রেন্ড ডেভিড লোশাক।
টেলিগ্রাফের ৩৭ বছর বয়স্ক বিদেশ প্রতিনিধি ডেভিড জীবনের ঝুঁকি নিয়ে অবিরাম বৃষ্টি ও মর্টারের গোলাবর্ষণের মধ্যে বিপজ্জনক পাহাড়ি পথে সিলেট প্রবেশ করলেন। মুক্তিযোদ্ধাদের হাতে অস্ত্র থাকুক বা নাই থাকুক, তিনি বিশ্বকে জানিয়ে দিলেন তাদের বিজয় ঠেকানো সম্ভব নয়, সমগ্র জনগোষ্ঠী তাদের সমর্থক। ডিসেম্বরে লিখলেন, পৃথিবীর বোধোদয় কেন হচ্ছে না, বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দিতে আর দেরি কেন?
‘পাকিস্তান ক্রাইসিস’ গ্রন্থের লেখক ডেভিড লোশাকের দুটি একাত্তরের প্রতিবেদন- একটি সিলেট থেকে, একটি লাহোর থেকে উপস্থাপন করে প্রয়াত যুদ্ধদিনের বন্ধুকে শ্রদ্ধা জানানো হচ্ছে :
একাত্তরে সিলেট ও লাহোর থেকে ডেভিড লোশাক
পূর্ব পাকিস্তানের রাজধানী শহর থেকে অনেক দূরে বিচ্ছিন্ন শহর সিলেটের নিয়ন্ত্রণ বাংলাদেশের মুক্তিবাহিনীর কাছ থেকে ছিনিয়ে নিতে পাকিস্তান কেন্দ্রীয় সরকারের সেনাবাহিনীকে গতকাল একটি জটিল পরিস্থিতির মোকাবিলা করতে হয়েছে। আগামী দুসপ্তাহের মধ্যে বর্ষাকাল এসে যাচ্ছে, এর মধ্যেই পাকিস্তানি বাহিনী সব ধরনের প্রতিরোধ থেকে মুক্ত হতে চাচ্ছিল- এতে তারা জোর প্রতিরোধের সম্মুখীন হয়েছে এবং দুই পক্ষেই অনেক হতাহত হয়েছে।
গত রাতে ৩১ পাঞ্জাব রেজিমেন্টের পশ্চিম পাকিস্তানি সৈন্যরা কর্তৃত্ব স্থাপন করতে পারলেও দ্বিতীয় দিনের মতো অবিরাম মর্টার বর্ষণ দেখে আমি স্পষ্ট বুঝতে পেরেছি যুদ্ধ শেষ হতে এখনো অনেক বাকি। পূর্ব পাকিস্তানের মুক্তিবাহিনীর সদস্যরা প্রশিক্ষণ পায়নি, স্বাধীনতার সেনাবাহিনী হিসেবে তেমন সংগঠিত হয়ে উঠেনি, কিন্তু মরণ কামড় দিয়ে তারা লড়াই করেছে। শহর এখন ধ্বংসস্তূপ, চারদিকে গোলার খোসা।
তারা পাঞ্জাব ইউনিটের ৮০০ সৈন্যের মধ্যে ২০০ জনকেই হত্যা করতে পেরেছে। তারা নিজেরাও অনেক ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে, কিন্তু হাজার হাজার বাঙালি তাদের লড়াই অব্যাহত রেখেছে এবং দ্রুত মৃত যোদ্ধার স্থলাভিষিক্ত হতে একজন যোদ্ধা এসে যাচ্ছে। তাদের অবস্থা অত্যন্ত খারাপ হবার পরও আমি তাদের উঁচু মনোবল দেখেছি। কোনো সন্দেহ নেই যুদ্ধ করে মরার জন্য তারা সত্যিই প্রস্তুত।
ম্যালকম ব্রাউন
নিউইয়র্ক টাইমস

ম্যালকম ব্রাউন একাত্তরের বাংলাদেশ-বান্ধব সাংবাদিকদের একজন। তিনি আমেরিকান সাংবাদিক লেখক ও ফটোগ্রাফার। তবে তার ব্যাপক পরিচিতি ও খ্যাতি এনে দেয় ১৯৬৩ সালে তোলা বৌদ্ধ পুরোহিত থিক কোয়াঙ দুক-এর আত্মহননের ছবি। এ ছবি ১৯৬৩ সালে তাকে এনে দেয় পুলিৎজার পুরষ্কার।
তার জন্ম নিউইয়র্ক সিটিতে ১৭ এপ্রিল ১৯১৩। মা ছিলেন যুদ্ধবিরোধী সক্রিয় কর্মী, বাবা রোমান ক্যাথলিক, স্থপতি ছিলেন।
প্রথম থেকে দ্বাদশ শ্রেণি পর্যন্ত তিনি মানহাটানের ফ্রেন্ডস সেমিনারিতে পড়াশোনা করেন। তারপর পেনসিলভানিয়ার সোয়ার্থমোর কলেজে রসায়ন শাস্ত্র পাঠ করেন।
কোরীয় যুদ্ধের সময় তাকে বাধ্যতামূলক সেনাবাহিনীতে যোগ দিতে হয়; তাকে স্টার্স অ্যান্ড স্ট্রাইপস পত্রিকার প্রশান্ত মহাসাগরীয় সংস্করণে কাজের দায়িত্ব দেওয়া হয়। দু’বছর পর তিনি টাইমস হেরাল্ড রেকর্ড-এ যোগ দেন। তারপর এপি (অ্যাসোসিয়েটেড প্রেস)-তে যোগ দিয়ে ১৯৫৯ থেকে ১৯৬১ পর্যন্ত বাল্টিমোর কার্যালয়ে দায়িত্ব পালন করেন। পরের বছর তিনি ইন্দো-চীনের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। তখনই আত্মহননের ছবিটি তোলেন।
১৯৬৫-তে এপি ছেড়ে এবিসি টেলিভিশনে যোগ দেন, ফ্লিল্যান্স সাংবাদিক হিসেবে বিভিন্ন পত্রিকায় কাজ করেন। তারপর কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের ফেলোশিপ নিয়ে আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগে পড়াশোনা করে ১৯৬৮ সালে আবার সাংবাদিকতায় ফিরে আসেন, নিউইয়র্ক টাইমসের দক্ষিণ আমেরিকার সংবাদদাতার দায়িত্ব পালন করেন।
কর্মজীবনের শুরুতে তিনি ছিলেন কেমিস্ট, ১৯৭৭ সালে তিনি বিজ্ঞান বিষয়ে লিখতে শুরু করেন এবং ডিসকভার পত্রিকায় জ্যেষ্ঠ সম্পাদক হন। ১৯৮৫-তে টাইমসে যোগ দিয়ে ১৯৯১-র উপসাগরীয় যুদ্ধেও সংবাদদাতা হন।

১৯৯৩ সালে প্রকাশিত হয় তার আত্মজীবনীমূলক গ্রন্থ মাডি বুটস অ্যান্ড রেড সকস। এর আগে ১৯৬৫ সালে প্রকাশ করেন দ্য নিউ ফেইস অব দ্য ওয়ার। পার্কিনসন’স ডিজিজ ও অন্যান্য স্বাস্থ্য সংকটে ২৭ আগস্ট ২০১২ ম্যালকম ব্রাউন মারা যান।
ম্যালকন ব্রাউন তার পুলিৎজার বিজয়ী ছবির প্রেক্ষাপট ও ছবি তোলা নিয়ে বলেন; সেন্ট্রাল ভিয়েতনামে সবকিছু সবকিছু যখন ক্রমে কুৎসিত হয়ে আসছে আমি সেখানে গিয়ে পৌঁছলাম। সেখানকার বৌদ্ধদের নিয়ে আমার আগ্রহ আগের চেযে বেড়ে গেল কারণ আমার মনে হয়েছে যা-ই ঘটুক আগামীতে তারাই হবে প্রধান চরিত্র। এর মধ্যে মঙ্কদের কাছ থেকে শুনলাম, যুদ্ধাবস্থার প্রতিবাদ করতে তারা একটা বড় কিছু করতে যাচ্ছেন- সম্ভবত নিজের ভুঁড়িতে ছুুুুুুুুুুুুুুুুুুুুুুুুুুুুুরি ঢুকিয়ে আত্মহনন করবেন।
মঙ্করা বিভিন্ন পত্রিকার বিদেশ সংবাদদাতাদের ফোন করে জানাতে শুরু করলেন যে তারা একটা ভয়ংকর কিছু করতে যাচ্ছেন। তবে সেই মর্মান্তিক দিনটিতে পশ্চিমের সাংবাদিকদের মধ্যে একমাত্র আমিই ছিলাম। আমি জানতাম এই বৌদ্ধ পুরোহিত- মঙ্করা কোনো ধাপ্পা দিচ্ছেন না। তাদের প্রতিবাদটি সহিংসই হবে। অন্য কোনো সংস্কৃতির ব্যাপার হলে দেখা যেত তারা বোমা বা এমন কিছু দিয়ে একটা ঘটনা ঘটিয়ে দিয়েছে।
আমি যখন প্যাগোডায় গিয়ে হাজির হই ততক্ষেণে প্রস্ততি বেশ এগিয়ে গেছে। মঙ্ক এবং নালরা একটা শোকগীত গাইতে শুরু করেছেন যা সাধারণত শেষকৃত্যের অনুষ্ঠানে গাওয়া হয়। তাদের নেতার নির্দেশে তারা খালি পায়ে রাস্তায় নামেন এবং সায়গন সেন্ট্রাল পার্কের দিকে এগোতে থাকেন। আমরা যখন সেখানে পৌঁছলাম সায়গনের দুটো প্রধান রাস্তার সংযোগ স্থলে মঙ্করা একটা বৃত্তের মতো ঘিরে ফেলল।
একটি গাড়ি এসে থামল, দুজন তরুণ মঙ্ক গাড়ি থেকে নামলেন। তরুণদের দিকে ঝুঁকে আরো একজন বয়স্ক মঙ্ক গাড়ি থেকে নেমে এলেন। তিনি চৌরাস্তার ঠিক মধ্যখানের দিকে এগোলেন। তরুণদের সঙ্গে প্ল্যাস্টিকের একটি জ্যারিকেম। পরে বোঝা গেল এতে গ্যাসোলিন বোঝাই ছিল। তিনি তার আসনে বসে পড়া মাত্রই তারা তার সারা শরীরে জেরিকেন থেকে তরল তেল ঢেলে দিয়ে একটি দেশলাই ধরিয়ে তার কোলে ছুড়ে মারল, সঙ্গে সঙ্গে আগুনের লেলিহান শিখা তাকে ঘিরে ফেলল।
এই ভয়ংকর দৃশ্য সবাই দেখল। আমি যতটা ভয়ংকর হবে ভেবেছি, কোনোভাবেই তার চেয়ে কম কিছু নয়।
তিনি ঠিক কখন মারা গেলেন বলা সম্ভব নয়। তিনি কখনো যন্ত্রণায় চিৎকার করে উঠেননি। যতক্ষণ না আগুন তার মুখ কালচে করে ফেলল, ততক্ষণ পর্যন্ত তিনি শান্তই ছিলেন। এক সময় উপস্থিত মঙ্করা সিদ্ধান্ত নিলেন যে তার মৃত্যু ঘটেছে। তারা কাঠ কেটে বানানো একটি কফিন নিয়ে এলেন।

একমাত্র বিদেশ ফটোগ্রাফার ছিলাম আমি। ভিয়েতনামি ক’জন ছিলেন কিন্তু তাদের কারো ছবি দেশের বাইরে কোথাও যায়নি।
ম্যালকম ব্রাউনের হাতে ছিল সস্তা দামের একটি জাপনি পেট্রি ক্যামেরা। এই ক্যামেরার সঙ্গে তার পরিচিত ভালোই ছিল। পুরো ঘটনাটি তুলে রাখার জন্য তিনি দ্রুত ছবি তুলছিলেন, তিনি দশটি রিল ভর্তি করেন।
সিডনি শনবার্গ
নিউইয়র্ক টাইমস

২৫ মার্চ ১৯৭১ পাকিস্তান সেনাবাহিনী ঢাকায় যে নারকীয় হত্যাযজ্ঞ চালিয়েছে, বিশ্ববাসীর কাছে সে খবর যারা পৌঁছে দিয়েছেন, তাদের অন্যতম নিউইয়র্ক টাইমস প্রতিনিধি সিডনি শনবার্গ।
২৭ মার্চ সকালে যে ৩৫ জন সাংবাদিক ও চিত্রগ্রাহককে বলপূর্বক হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টাল থেকে উঠিয়ে তাদের দেহ ও লাগেজ তল্লাশি করে ফিল্ম ও নোটবই ছিনিয়ে নিয়ে পূর্ব পাকিস্তান থেকে প্রায় তাৎক্ষণিকভাবে বের করে দেয়া হয়, সিডনি শনবার্গ তাদের একজন।
২৮ মার্চ নিউইয়র্ক টাইমস তার দুটি বড় প্রতিবেদন প্রকাশ করে:
১. বিদ্রোহ দমাতে সৈন্যরা কামান দাগাচ্ছে
২. পূর্ব পাকিন্তানে কামানের বিরুদ্ধে লাঠি ও বল্লম
১৯৭১-এ বাংলাদেশ ভূখণ্ড ও সীমান্তের ওপারে কী ঘটেছে, তার বিশ্বস্ত সাক্ষী সিডনি শনবার্গ।
বাংলাদেশের সেই যুদ্ধদিনের বন্ধু পুলিৎজার বিজয়ী সিডনি শনবার্গ ৯ জুলাই ২০১৬ হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে ৮২ বছর বয়সে নিউইয়র্কে মৃত্যুবরণ করেন।
সিডনি শনবার্গের নেয়া ইন্দিরা গান্ধীর সাক্ষাৎকার
ইন্দিরা গান্ধী (১৯ নভেম্বর ১৯১৭-৩১ অক্টোবর ১৯৮৪)
ভারতের প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী দ্য নিউইয়র্ক টাইমস প্রতিনিধি সিডনি এইচ শনবার্গকে একটি সাক্ষাৎকার দিয়েছিলেন। সাক্ষাৎকারভিত্তিক এ প্রতিবেদনটি ১৯ অক্টোবর ১৯৭১ প্রকাশ হয়:
প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী তখন ঘোষণা করেছেন, ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যবর্তী সীমান্তে সামরিক পরিস্থিতি ‘অত্যন্ত গুরুতর’।
১ ঘণ্টার একটি সাক্ষাৎকারে প্রধানমন্ত্রী বলেন, ‘আক্রমণের প্ররোচনা কিংবা বৈরিতার সূচনা আমরা অবশ্যই করব না। কিন্তু আমাদের স্বার্থ রক্ষার জন্য তো আমাদের জাগ্রত থাকতে হবে এবং আমাদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে হবে।’
তিনি বলেন, ‘দুর্ভাগ্যবশত পাকিস্তানের খতিয়ান কেবল ঘৃণার ও বেপরোয়া আচরণের। সেখানকার সামরিক শাসন নিজ দেশের ওপরও একটি যুদ্ধ চাপিয়ে দিয়েছে। এরপর তারা কী করবে আমাদের জানা নেই।’ সরকারি সচিবালয়ে যখন প্রধানমন্ত্রীর সাক্ষাৎকার নেয়া হচ্ছিল, পূর্ব পাকিস্তানের বাঙালি বিদ্রোহীদের ভারত সামরিক সহায়তা দিচ্ছে কিনা জিজ্ঞেস করা হলে তাকে বিরক্ত মনে হয়।
আবার ভারত তাদের সাহায্য করছে না, সুনির্দিষ্টভাবে এমন কিছুও তিনি বলেননি। বরং তিনি বলেছেন, ‘সম্ভবত তাদের সাহায্য করার মতো অনেকেই আছে, অধিকাংশই তাদের নিজেদের লোক, পৃথিবীজুড়ে। তাদের সামনে অনেক পথ খোলা।’ তিনি তার কথার ব্যাখ্যা দেননি।
সাক্ষাৎকারের শেষ দিকে তিনি বলেন, ‘তাদের অস্ত্র থাকুক বা না-ই থাকুক, কেউই তাদের সংগ্রামকে দমিয়ে রাখতে পারবে না।’
ইন্দিরা গান্ধী বলেন, ‘পাকিস্তান যে হুমকি দিচ্ছে, আমরা মনে করি, তা পুরোপুরি উপেক্ষা করা যায় না।’ বিশেষ করে তিনি পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট আগা মোহাম্মদ ইয়াহিয়া খানের গত সপ্তাহের ভাষণের উল্লেখ করে বলেন, ‘ভারতের উগ্র সামরিক প্রস্তুতি’কে তিনি দোষারোপ করেন এবং এ হুমকি মোকাবিলা করার জন্য তার দেশের ১২ কোটি মুসলমান মুজাহিদের প্রতি আহ্বান জানান, যাদের হৃদয় মহানবীর ভালোবাসায় উদ্বেলিত।’
৫৩ বছর বয়সি প্রধানমন্ত্রী ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে কোনো শান্তি আলোচনার সম্ভাবনা দৃঢ়ভাবে নাকচ করে দেন। তিনি বলেন, পাকিস্তানকে সবার আগে নির্বাচিত গণপ্রতিনিধিদের সঙ্গে সমঝোতা করে পূর্ব পাকিস্তান সংকটের সমাধান করতে হবে।
প্রায় সাত মাস ধরে প্রায় পুরোটাই পশ্চিম পাকিস্তানি সৈন্য নিয়ে গঠিত পাকিস্তান সেনাবাহিনী আওয়ামী লীগ নেতৃত্বাধীন পূর্ব পাকিস্তানিদের আন্দোলন নস্যাৎ করে দেয়ার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। গত ২৫ মার্চ সেনাবাহিনী যখন আক্রমণ চালায়, গত ডিসেম্বরের সাধারণ নির্বাচনে সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জনকারী এ দলটিকে সেনাশাসকরা নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছে।
সামরিক নির্যাতন লাখ লাখ পূর্ব পাকিস্তানিকে শরণার্থী বানিয়ে ভারতে পাঠিয়েছে। শরণার্থীরা ভারতের ওপর যে অর্থনৈতিক ও সামাজিক চাপ সৃষ্টি করেছে, তাতে ভেঙে পড়ার মতো অবস্থা তিনি অনুভব করছেন কিনা জিজ্ঞেস করা হয়; এর চেয়ে বেশি হলেই শরণার্থীর এ গণআগমন ঠেকাতে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে সামরিক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে কিনা জিজ্ঞেস করা হয়।
ইন্দিরা গান্ধী বলেন, ‘আমরা এ রকম একটি অবস্থায় আগেই পৌঁছেছি। কিন্তু তার মানে ভেঙে পড়া নয়। আমরা অবশ্যই দ্রুত সমাধান চাই, আমরা এমন কিছু করতে চাই না, যা আরো বেশি সমস্যার সৃষ্টি করবে। আপনারা জানেন, আমরা চূড়ান্ত সংযমের পরিচয় দিচ্ছি, এ রকম ভয়ংকর প্ররোচনার মুখে আমি গভীরভাবে ভেবে দেখেছি, আর কোনো দেশ এ ধৈর্য ও সংযমের পরিচয় দিতে পারবে বলে আমি মনে করি না।
গত কয়েক সপ্তাহে উভয় দেশই পূর্ব ও পশ্চিম সীমান্তে সামরিক শক্তি আরো জোরদার করেছে এবং সীমান্তের উভয় পারের গণমাধ্যম আরেকটি ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধ আসন্ন বলে মনে করছে। কাশ্মির নিয়ে ১৯৬৫ সালে শেষ ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধ হয়।
ইন্দিরা গান্ধী যদিও পরিস্থিতি গুরুতর বলে মনে করছেন, রোববার থেকে তিন সপ্তাহের জন্য তার আসন্ন বিদেশ সফর পরিবর্তনের কোনো আভাস দেননি। এ সময় তিনি লন্ডন ও ওয়াশিংটনসহ ছয়টি পাশ্চাত্য দেশের রাজধানী সফর করবেন।
পূর্ব পাকিস্তান সংকটে যুক্তরাষ্ট্রের নীতির সমালোচনা করে তিনি বলেন, ‘আমেরিকানরা ভালো করে চোখ মেলে সমস্যাটিকে দেখছে না।’
‘বাংলাদেশের সামরিক শাসনকে ঠেক দিয়ে রেখে কোনোভাবেই পাকিস্তানকে শক্তিশালী করা হচ্ছে না।’
ইন্দিরা গান্ধী পাকিস্তানে নিক্সন প্রশাসন কর্তৃক অস্ত্র সরবরাহ অব্যাহত রাখার এবং প্রকাশ্যে পাকিস্তান সরকারকে সমালোচনার অনীহার কথা উল্লেখ করেন। তিনি বলেন, ‘আমেরিকা ও আমেরিকার জনগণের সঙ্গে আমাদের অত্যন্ত অন্তরঙ্গ সম্পর্ক, কিন্তু ভারতীয় জনগণের মতে, সম্পর্ক হ্রাস পাওয়ার একটি কারণ যুক্তরাষ্ট্রের ভারত ও পাকিস্তানের ভারসাম্য রক্ষা করার চেষ্টা।’
পাকিস্তানের জন্য আমেরিকার অস্ত্র প্রসঙ্গে তিনি বলেন, ‘এখন অস্ত্রের পরিমাণ কত আমার জানা নেই, কিন্তু আমেরিকা আগে বিপুল পরিমাণ অস্ত্র সরবরাহ করেছে। আর এসব কেবল আমাদের বিরুদ্ধে ব্যবহার করা হয়েছে, কমিউনিজম বা অন্য যা কিছু তারা বলেছে, কোনোটার বিরুদ্ধেই নয়। এ বিষয়ে যুক্তরাষ্ট্রের চেয়ে সোভিয়েত ইউনিয়নের আমাদের সঙ্গে বোঝাপড়া বরং অনেক বেশি।
প্রধানমন্ত্রী আমেরিকা ও রাশিয়ার সঙ্গে ভারতের সম্পর্ক নিয়ে এ পর্যায়ে বিস্তারিত বললেন:
‘দেখুন, সোভিয়েত ইউনিয়নের ব্যাপারে যুক্তরাষ্ট্রের দৃষ্টিভঙ্গি আমাদের কাছে অদ্ভুত মনে হয়। আমরা আমেরিকাকে যেভাবে সমর্থন করি, সোভিয়েত ইউনিয়নকে তার চেয়ে বেশি কিছু করি না; এটাকে ধনাত্মক মনে করুন কিংবা ঋণাত্মক, দুই দেশের জন্যই আমাদের সমর্থন সমান।’
‘সোভিয়েত ইউনিয়ন কিছু মৌলিক বিষয়ে আমাদের সাহায্য করছে, যার জন্য আমরা এক সময় লড়াই করেছি। আর এ কারণে আমরা জাতিসংঘে সোভিয়েত ইউনিয়নকে সমর্থন দিই। আপনি মার্কিন সাহায্যের ব্যাপারে কিছু বলেছেন। আমরা যুক্তরাষ্ট্রের কাছে কৃতজ্ঞ, তারা বহুভাবে আমাদের সাহায্য করেছে। কিন্তু এক সময় যখন আমরা সরকারি খাতকে শক্তিশালী করতে তাদের সাহায্য চাইলাম, পেলাম না, কিন্তু সোভিয়েত ইউনিয়ন করেছে।’
তিনি আরো যোগ করেন, ‘ব্যক্তিগতভাবে রুশ কিংবা অন্যদের তুলনায় আমেরিকানদের সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক বেশি জমে। ভাষা তার একটি বড় কারণ। ব্যক্তিগতভাবে আমি আমেরিকার প্রযুক্তিগত ও বৈজ্ঞানিক অগ্রগতির প্রশংসা করি।