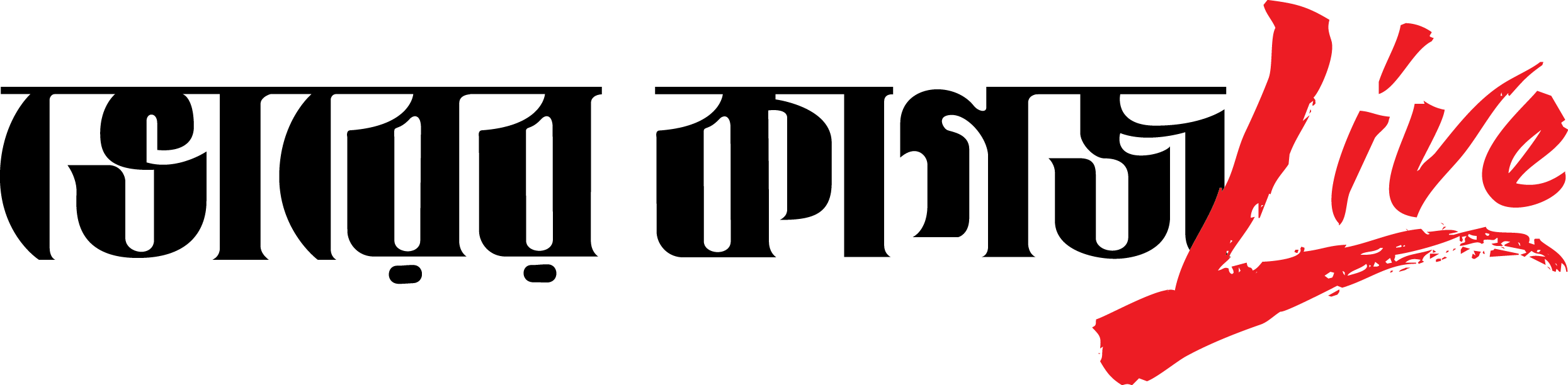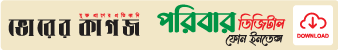অর্থনীতি
ক্রমে গভীর হচ্ছে সংকট, শঙ্কা বাড়ছে ব্যবসায়ীদের
মরিয়ম সেঁজুতি
প্রকাশ: ০২ অক্টোবর ২০২৫, ০৫:১৪ পিএম

বাংলাদেশের ব্যবসায়ীদের শঙ্কা বাড়ছে। ছবি: জেমিনি ও ভোরের কাগজ
বাংলাদেশ দক্ষিণ এশিয়ার অর্থনৈতিক অগ্রগতির এক উজ্জ্বল উদাহরণ হিসেবে দীর্ঘদিন ধরে প্রশংসিত হয়ে আসছে। তৈরি পোশাক খাত, প্রবাসী আয়, দারিদ্র্য হ্রাস, মানবসম্পদ উন্নয়ন ও অবকাঠামো খাতে সাফল্যের মাধ্যমে বিশ্ব দরবারে নিজের অবস্থান সুদৃঢ় করেছে। তবে গত জুলাইয়ে প্রকাশিত দুটি গুরুত্বপূর্ণ প্রতিবেদনের তথ্য বলছে, অর্থনীতির ভেতরে জমতে থাকা গভীর সংকট উপেক্ষা করার সুযোগ নেই। বিশ্বব্যাংকের ‘গ্লোবাল ফিনডেক্স ২০২৫’ এবং জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের (এনবিআর) সর্বশেষ হিসাব বলছে বাংলাদেশের আর্থিক অন্তর্ভুক্তি ও রাজস্ব আহরণে ধস নেমেছে। যা দেশের সামগ্রিক অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা ও টেকসই উন্নয়নের জন্য এক বড় চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়িয়েছে।
দেশের ব্যবসায় বিনিয়োগ নিয়ে ব্যবসায়ী-উদ্যোক্তাদের দুশ্চিন্তা কমছেই না। নানান প্রতিকূলতার মধ্য দিয়ে যাচ্ছে ব্যবসাবাণিজ্য। গ্যাসসংকটে ব্যাহত হচ্ছে শিল্পে উৎপাদন। ব্যাংক সুদহার বেড়ে হয়েছে ১৬ শতাংশ। মূলধনি যন্ত্রপাতির এলসি খুলতে গিয়ে মুখোমুখি হতে হচ্ছে নানান জটিলতার, সেই সঙ্গে রয়েছে ডলারসংকট। কর্মতৎপরতা কমে যাওয়ায় শিল্পকারখানা বন্ধ হয়ে বেকার হচ্ছে হাজার হাজার শ্রমিক। এ ছাড়া শ্রম আইন সংস্কার নিয়েও ব্যবসায়ীদের মাঝে রয়েছে উদ্বেগ। সাহস পাচ্ছেন না নতুন বিনিয়োগে, পুরোনো বিনিয়োগও হুমকিতে। রাজনৈতিক অনিশ্চয়তাসহ অভ্যন্তরীণ নানান সংকটের বৃত্তে ঘুরপাক খাচ্ছে ব্যবসা-বিনিয়োগ। এতে দেশের বেসরকারি খাতের প্রতিযোগিতা-সক্ষমতা রীতিমতো চ্যালেঞ্জের মুখে পড়ছে।
সম্প্রতি যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্র দপ্তরের ২০২৫ সালের বৈশ্বিক বিনিয়োগ পরিবেশ প্রতিবেদন বাংলাদেশে বিনিয়োগে বাধার পাঁচটি কারণ চিহ্নিত করেছে। এগুলো হচ্ছে অপর্যাপ্ত অবকাঠামো, সীমিত অর্থায়ন, আমলাতান্ত্রিক বিলম্ব, বিদেশি সংস্থাগুলোর জন্য অন্যায্য করের বোঝা ও দুর্নীতি। প্রতিবেদনে বাংলাদেশ অংশে উল্লেখ করা হয়েছে, গত এক দশকে বাংলাদেশে বিনিয়োগের সীমাবদ্ধতা কমাতে ধীরে ধীরে অগ্রগতি অর্জন করা হয়েছে। যেমন বিদ্যুৎ পরিষেবা আরো ভালোভাবে নিশ্চিত করার প্রচেষ্টা রয়েছে। তবে বিদেশি বিনিয়োগ এখনো বাধাগ্রস্ত হচ্ছে। প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়, নোবেলজয়ী ড. মুহাম্মদ ইউনূসকে প্রধান উপদেষ্টার দায়িত্ব দিয়ে অন্তর্বর্তী সরকার প্রশাসন সংস্কারের কাজ শুরু করে, কিন্তু দৈনন্দিন নিয়ন্ত্রক দৃশ্যপটের বেশির ভাগই অপরিবর্তিত রয়েছে।
অপরদিকে, গত মঙ্গলবার প্রকাশিত এশীয় উন্নয়ন ব্যাংকের (এডিবি) এশিয়ান ডেভেলপমেন্ট আউটলুক (এডিও) প্রতিবেদনেও প্রায় একই উদ্বেগ তুলে ধরা হয়েছে। প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, বাংলাদেশের অর্থনীতিতে এক বছর ধরে গতি মন্থরতা চলেছে, এরপর ২০২৫-২৬ অর্থবছরে এসে অর্থনৈতিক পুনরুদ্ধারে নতুন মার্কিন শুল্ক, ভ‚-রাজনৈতিক উত্তেজনা, উচ্চ নির্বাচনকালীন ব্যয়, সংকটগ্রস্ত দুর্বল ব্যাংকগুলোকে দেয়া তারল্য সহায়তা এবং ব্যাংকখাতের অব্যাহত দুর্বলতার কারণে ঝুঁকির মুখে পড়তে পারে। একইসঙ্গে এডিবি বাংলাদেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির পূর্বাভাস কিছুটা কমালেও প্রবৃদ্ধি ৫ শতাংশ হবে বলে ধারণা করছে, যা গত এপ্রিলের ৫ দশমিক ১ শতাংশ অনুমানের চেয়ে সামান্য কম। এরপরও এটি গত তিন বছরের মধ্যে দ্রুততম প্রবৃদ্ধি হবে। এর আগে ২০২৪-২৫ অর্থবছরে বাংলাদেশের জন্য মাত্র ৪ শতাংশ প্রবৃদ্ধির প্রাক্কলন করেছিল এডিবি।
এডিবি সতর্ক করে বলেছে, যুক্তরাষ্ট্রের নতুন শুল্ক এবং সম্ভাব্য ভ‚-রাজনৈতিক উত্তেজনা রপ্তানির প্রবৃদ্ধিকে বাধাগ্রস্ত করতে পারে। একই সঙ্গে ব্যবস্থাপিত ভাসমান বিনিময় হার নীতির দুর্বল বাস্তবায়ন বহিঃখাতের ভারসাম্যহীনতা আরো বাড়াতে পারে। বাংলাদেশে এডিবির কান্ট্রি ডিরেক্টর হো ইউং জং বলেন, ভবিষ্যৎ প্রবৃদ্ধি নির্ভর করবে ব্যবসার পরিবেশ উন্নয়নের মাধ্যমে প্রতিযোগিতা বাড়ানো ও বিনিয়োগ আকৃষ্ট করা এবং নিরবচ্ছিন্ন জ্বালানি সরবরাহ নিশ্চিত করার ওপর। দেশের অর্থনীতিবিদরা বলছেন, অর্থনৈতিক চ্যালেঞ্জ মোকাবিলার জন্য ব্যাংক খাত ঠিক করতে হবে, বিদ্যুৎ সরবরাহ নির্বিঘ্নে করতে হবে, বন্দর আধুনিকায়ন করতে হবে। শ্রমিকদের দক্ষতা বাড়াতে হবে, প্রশাসনকে দুর্নীতিমুক্ত করতে হবে, রপ্তানি বৈচিত্র্যকরণ করতে হবে। কিন্তু এগুলো ঘটবে কিনা, সেটা বলা এখন মুশকিল। এসব কিছুর জন্য রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা অপরিহার্য হয়ে পড়েছে।
শিল্পকারখানার উদ্যোক্তারা বলেছেন, নানান সমস্যায় দেশে নতুন করে বিনিয়োগের আগ্রহ নেই। ব্যাংকে সুদের হার বেড়েছে, নিরবচ্ছিন্ন গ্যাস সরবরাহ নেই, আইনশৃঙ্খলার সমস্যা তো রয়েই গেছে। এ ছাড়া কাস্টমসে নানান হয়রানির মুখোমুখি হতে হয় ব্যবসায়ীদের। এ বিষয়ে বাংলাদেশ নিটওয়্যার ম্যানুফ্যাকচারার্স অ্যান্ড এক্সপোর্টার্স অ্যাসোসিয়েশনের (বিকেএমইএ) সভাপতি মোহাম্মদ হাতেম বলেন, এ মুহূর্তে ব্যবসাবাণিজ্যে সবচেয়ে বেশি সমস্যার মধ্যে পড়ছি ব্যাংকিং নিয়ে। ব্যাংক সবচেয়ে বেশি সমস্যা তৈরি করছে। আমাদের আমদানি-রপ্তানি বাণিজ্য বিলম্বিত হচ্ছে। এর পরের সমস্যা কাস্টমস নিয়ে। তারপর গ্যাস-বিদুৎ, আইনশৃঙ্খলা। মোটা দাগে এ চার সমস্যার মুখোমুখি হচ্ছি। এ ছাড়া বাংলাদেশ ব্যাংকের পলিসি বিনিয়োগসহায়ক হতে হবে। এখনো বিনিয়োগসহায়ক পরিবেশের অভাব আছে। শ্রম আইন সংশোধন নিয়ে যা হচ্ছে তাতে বিদেশি বিনিয়োগ আসবে না এটা নিশ্চিত। আমাদের দেশের ব্যবসায়ীদের জন্য অপশন কম। বিদেশে বিনিয়োগের অনেক অপশন আছে। বিনিয়োগ যা করার করেছি নতুন করে আর বিনিয়োগ করার চিন্তাভাবনা নেই।
বাংলাদেশ গার্মেন্ট অ্যাকসেসরিজ অ্যান্ড প্যাকেজিং ম্যানুফ্যাকচারার্স অ্যান্ড এক্সপোর্টার্স অ্যাসোসিয়েশনের (বিজিএপিএমইএ) মো. শাহরিয়ার বলেন, পুরোনো বিনিয়োগকারীরা এখন নানান সমস্যায় আছেন। মূলধনি মেশিন আমদানিতে এলসি মিলছে না। নতুন বিনিয়োগে ঋণসহায়তা পাওয়া যায় না। ঝুট নিয়ে সমস্যা এখন আবার বড় আকার ধারণ করেছে। ব্যবসাবাণিজ্যে স্থিতিশীলতার বড় অভাব রয়েছে। ব্যবসায়ীরা এখন অভিভাবকহীন ও নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছেন।
বিনিয়োগ যে তলানিতে গিয়ে ঠেকেছে তা বেসরকারি খাতে ঋণের প্রবাহ দেখলেই অনুমান করা যায়। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর (বিবিএস) তথ্য অনুযায়ী, ১১ সেপ্টেম্বর বৃহস্পতিবার শ্রমশক্তি জরিপ ২০২৪-এর চূড়ান্ত প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো (বিবিএস)। তথ্য অনুযায়ী, বাংলাদেশের বেকারসংখ্যা ২৬ লাখ ২৪ হাজার। বিভাগওয়ারি হিসাবে সবচেয়ে বেশি বেকার ঢাকা বিভাগে। এ বিভাগে ৬ লাখ ৮৭ হাজার বেকার আছে। এরপরের দুটি স্থানে আছে যথাক্রমে চট্টগ্রাম ও রাজশাহী বিভাগ। ঢাকা বিভাগের পর চট্টগ্রাম বিভাগে ৫ লাখ ৮৪ হাজার, রাজশাহীতে ৩ লাখ ৫৭ হাজার, খুলনায় ৩ লাখ ৩১ হাজার, সিলেটে ২ লাখ ১৬ হাজার, রংপুরে ২ লাখ ৬ হাজার, বরিশালে ১ লাখ ৩৯ হাজার এবং ময়মনসিংহ বিভাগে ১ লাখ ৪ হাজার বেকার আছে।
বিশ্বব্যাংক ঢাকা কার্যালয়ের সাবেক প্রধান অর্থনীতিবিদ ড. জাহিদ হোসেন বলেন, অর্থনৈতিক চ্যালেঞ্জ মোকাবিলার জন্য ব্যাংকখাত ঠিক করতে হবে। গ্যাসের সমস্যার সমাধান করতে হবে। বিদ্যুৎ সরবরাহ নির্বিঘ্ন করতে হবে। বন্দর আধুনিকায়ন করতে হবে। শ্রমিকদের দক্ষতা বাড়াতে হবে। প্রশাসনকে দুর্নীতিমুক্ত করতে হবে। রপ্তানি বৈচিত্র্য আনতে হবে। কিন্তু এগুলো ঘটবে কিনা বা কীভাবে ঘটবে সেটা বলা এখন মুশকিল হয়ে গেছে। অর্থনৈতিক চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা নিয়ে ড. জাহিদ হোসেন বলেন, অর্থনৈতিক চ্যালেঞ্জ মোকাবিলার পূর্বশর্ত হলো রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা। সেটার তো কোনো আশা-ভরসার জায়গা এখন দেখা যাচ্ছে না। এ ধরনের অবস্থা থেকে এগুলো মোকাবিলা করা খুব কঠিন। অর্থনৈতিক অবস্থা যাতে আরো খারাপ না হয় সেটা নিশ্চিত করতে হবে। তাহলে রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা একসময় ফিরে আসবে এ আশা করা যায়। অনিশ্চয়তা সব দেশেই থাকে। কিন্তু আমাদের এখানে তো রাজপথই অস্থিতিশীল। স্বাভাবিক চলাফেরা বা ব্যবসা-বাণিজ্য করা যাবে কিনা, সেটা তো বলা কঠিন আজ যা আছে কাল থাকবে কিনা। তিনি আরো বলেন, এই ধরনের অবস্থায় অর্থনীতির তো হাঁটুভাঙা অবস্থা আরকি। আপনি যে একটু দাঁড়াবেন, ওই দাঁড়াবার আগেই আরেকটা বাড়ি খাচ্ছে। ভাঙা হাঁটু নিয়ে কতদূর যাবেন বা কত দ্রুত যাবেন, সেটা তো সম্ভব নয়। বিনিয়োগের যে স্থবিরতা এটা তো কাটবে না, যদি আপনার পূর্বশর্ত পূরণ না হয়। আর তার পরে যে বিনিয়োগ শুরু হবে, সেটাও তো বলা যায় না। কারণ আপনার তো সংস্কারও লাগবে। কিন্তু অর্থনৈতিক সংস্কার তো এগোতে পারছে না।
সার্বিক অর্থনীতি নিয়ে অর্থনীতিবিদ ড. জায়েদ বখত বলেন, এমন তো না যে আমাদের শিল্প-কারখানা নষ্ট হয়ে গেছে বা বন্যায় আমাদের তীব্র ক্ষতি হয়েছে। এমন কিছু তো নয়। এটা জাস্ট সাময়িক কিছু সমস্যা তৈরি হয়েছে। রেমিট্যান্স আসছে, রপ্তানির প্রবৃদ্ধিও একেবারে খারাপ নয়। সে জন্য আশা করা যায়, আগামীতে এগুলো ঠিক হয়ে যাবে। জায়েদ বখত বলেন, আমাদের অর্থনীতির মৌলিক ভিত্তিগুলো ঠিক আছে। এগুলো (বিনিয়োগ মন্দা, বেকারত্ব বেড়ে যাওয়া, কর্মসংস্থান না হওয়া, প্রবৃদ্ধি কমে যাওয়া) সাময়িক, রাজনৈতিক ও অন্য পরিস্থিতির কারণে হচ্ছে। একটা স্থিতিশীলতা এসে গেলে ঠিক হয়ে যাবে। বিনিয়োগ না হওয়ার কারণ হিসেবে এ অর্থনীতিবিদ বলেন, ধরুন আপনার কাছে ১০ কোটি টাকা আছে, আপনি কি বিনিয়োগ করবেন? করবেন না, আপনি মনে করবেন দেশের অবস্থা আরো একটু স্থিতিশীল হোক, তারপর করবো। সুতরাং দেশের ব্যবসায়ীরা একটু ‘ওয়েট অ্যান্ড সি’ নীতিতে আছেন, বিদেশিরাও সেই একই কাজ করবে। সুতরাং, সবাই একটু ধীরে ধীরে এগোবে। তিনি আরো বলেন, আমাদের যে উৎপাদন সক্ষমতা আছে, সেটা যখন কাজে লাগাতে পারবো, তখন নতুন বিনিয়োগ আসবে এবং প্রতিষ্ঠান তার পূর্ণ সক্ষমতায় চললে বেকারত্বও কমে আসবে।
মুদ্রাস্ফীতি কমলেও ঝুঁকি রয়ে গেছে :
এডিবির প্রতিবেদন বলছে, ২০২৫-২৬ অর্থবছরে গড় মুদ্রাস্ফীতি চার বছরের মধ্যে সর্বনিন্ম ৮ শতাংশে নামবে, যার এর আগের বছরের প্রায় ১০ শতাংশের থেকে কম। তবে এ উন্নতি আংশিক স্বস্তিই দিতে পারবে। তবে এ ঋণদাতা প্রতিষ্ঠান সতর্ক করেছে, সাম্প্রতিক সময়ের কঠোর মুদ্রানীতি সত্ত্বেও, উচ্চ নির্বাচনকালীন ব্যয় এবং দুর্বল ব্যাংকগুলোকে তারল্য সহায়তা মূল্যস্ফীতি ও বৈদেশিক মুদ্রা বাজারে চাপ বাড়াতে পারে এবং গভর্ন্যান্সের সংস্কার দুর্বল করতে পারে। প্রতিবেদন আরো বলা হয়, ২০২৬ সালের ফেব্রুয়ারিতে নির্ধারিত জাতীয় নির্বাচন এবং আর্থিক খাতে চলমান সংস্কারের কারণে স্বচ্ছতা, দক্ষতা ও স্থিতিশীলতা বৃদ্ধির মধ্য দিয়ে বিনিয়োগকারীর আস্থা বাড়তে পারে।
যুক্তরাষ্ট্রে রপ্তানিতে ২০ শতাংশ শুল্ক :
প্রতিবেদন অনুযায়ী, নতুন শুল্ক কার্যকর হলে যুক্তরাষ্ট্রে বাংলাদেশের রপ্তানি পণ্যের গড় শুল্কহার ১৫ শতাংশ থেকে বেড়ে ৩৫ শতাংশে পৌঁছাবে। পোশাক খাতে শুল্ক ১৬ দশমিক ৮ শতাংশ থেকে বেড়ে দাঁড়াবে ৩৬ দশমিক ৮ শতাংশে, আর কিছু পণ্যে যেমন কৃত্রিম ফাইবার সোয়েটার শুল্ক হবে ৫২ শতাংশ। এর প্রভাব পড়বে বিশেষ করে, পোশাকখাতে কর্মসংস্থান হওয়া বিপুলসংখ্যক নারী শ্রমিকের ওপর। যদিও এ শুল্ক ভারত বা চীনের ওপর আরোপিত শুল্কের চেয়ে তুলনামূলক কম, তবুও এগুলো যুক্তরাষ্ট্রে বাংলাদেশের পণ্যের চাহিদা ক্ষতিগ্রস্ত করতে পারে বলে এডিবি উল্লেখ করেছে। উন্নয়ন সহযোগী সংস্থাটির প্রতিবেদনে আরো বলা হয়েছে, বাংলাদেশের রপ্তানিকারকদের ইউরোপীয় ইউনিয়ন বাজারেও বাড়তি প্রতিযোগিতার মুখোমুখি হতে হবে, যেখানে হয় দাম কমাতে হবে, নয়তো বাজার হারানোর ঝুঁকি নিতে হবে।
এ ঝুঁকি সামাল দিতে এডিবি সুপারিশ করেছে, বাংলাদেশকে রপ্তানি বাজার বৈচিত্র্যময় করতে হবে, নতুন বাণিজ্য চুক্তির পথ খুঁজতে হবে এবং প্রতিযোগিতা সক্ষমতা বাড়াতে পদক্ষেপ নিতে হবে।
এশিয়া-প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলের প্রবৃদ্ধি শ্লথ হওয়ার পূর্বাভাস :
এডিবি বলছে, নতুন বৈশ্বিক বাণিজ্য পরিবেশ যা মার্কিন শুল্ক ও সাম্প্রতিক সময়ের বিভিন্ন বাণিজ্য চুক্তির মাধ্যমে গঠিত হচ্ছে তার প্রভাবে উন্নয়নশীল এশিয়া ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলের প্রবৃদ্ধি ধীর হবে। ২০২৫ সালে অঞ্চলের প্রবৃদ্ধি হবে ৪ দশমিক ৮ শতাংশ এবং ২০২৬ সালে ৪ দশমিক ৫ শতাংশ, যা গত এপ্রিলে দেয়া ৪ দশমিক ৯ শতাংশ ও ৪ দশমিক ৭ শতাংশ পূর্বাভাসের চেয়ে কম। মার্কিন শুল্ক বৃদ্ধির পাশাপাশি অনিশ্চিত বাণিজ্য পরিবেশ এ অঞ্চলের প্রবৃদ্ধির ওপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলবে বলে প্রতিবেদনে বলা হয়েছে।
অত্র অঞ্চলে মূল্যস্ফীতি চলতি বছরে খাদ্য ও জ্বালানির কম দামের কারণে ১ দশমিক ৭ শতাংশে নেমে আসবে, তবে আগামী বছর খাদ্যদ্রব্যের দাম স্বাভাবিক হলে তা সামান্য বেড়ে ২ দশমিক ১ শতাংশে পৌঁছাতে পারে। এডিবি আরো সতর্ক করেছে, বাণিজ্য ঝুঁকি এ অঞ্চলের প্রবৃদ্ধির প্রধান হুমকি। যুক্তরাষ্ট্র-চীনের বিদ্যমান উত্তেজনা, সেমিকন্ডাক্টর ও ওষুধে খাতভিত্তিক শুল্ক এবং ভবিষ্যৎ শুল্ক বৃদ্ধি এশিয়া ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলের দেশগুলোর অর্থনীতিকে প্রভাবিত করতে পারে।